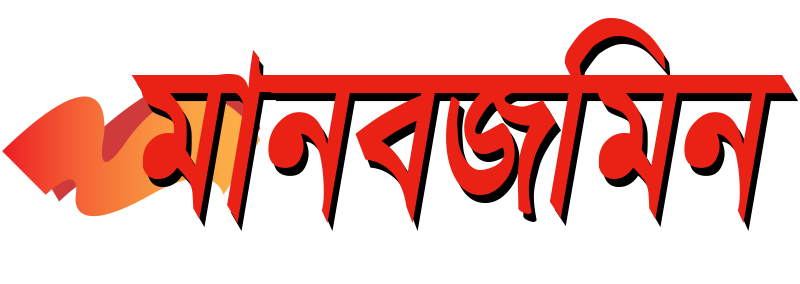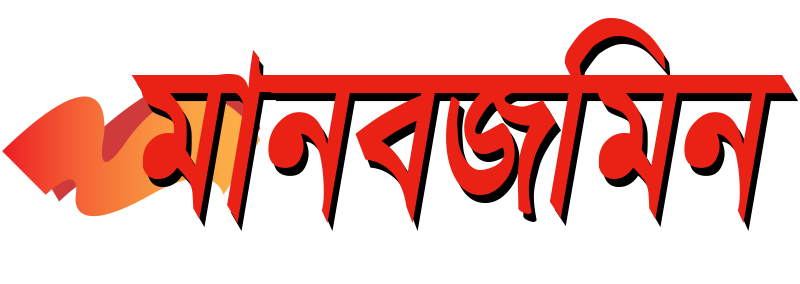ঈদ আনন্দ ২০১৮
ভ্রমণ
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে দু’পা ফেলিয়া
সাখাওয়াত হোসেন
৩০ জুন ২০১৮, শনিবার, ৫:২৩ পূর্বাহ্ন

প্রায়শঃই আমাদের আড্ডা গ্রুপের বিদেশ ভ্রমণের ভূত চেপে বসে। বছরে একবার বেশ দূরে আর কয়েকবার কাছাকাছি কোথাও। আর সেই কাছাকাছিটা বাড়ির একেবারে নিকট পশ্চিমবাংলা। বিশেষ করে কলকাতাঞ্চল। ঢাকার বাইরে বিশ্বের যে দু’টি শহর আমার কাছে বেশ আপন মনে হয় সে দু’টি হলো কলকাতা আর লন্ডন। তবে বহুবিধ কারণে লন্ডনকে এগিয়ে রাখছি। এই দুই শহর আপন মনে হওয়ার কারণ ভাষা আর খাবার। লন্ডনে ইংরেজি এবং বাংলা দুটোই স্বচ্ছন্দ্যে ব্যবহারযোগ্য আর কলকাতায় তো কথাই নেই। এক সময়ের ভারতের রাজধানী তবে ঢাকার মতো ঐতিহ্যবাহী নয়। যাই হোক বহুবিধ কারণে কলকাতায় কয়েকবার যাতায়াত। অন্যদিকে সুহৃদ হাবিবুর রহমান খানের কারণে যেখানেই যাই না কেন ছোটখাটো আড্ডার মানুষ জুটে যায়। সে কারণে জমে উঠে আন্তঃদেশীয় আড্ডা।
কয়েকদিন আগে আমাদের সকালের আড্ডায় বসে মনে হলো অনেকদিন দেশের বাইরে যাওয়া হয় না। আমাদের আড্ডার সংগঠক হাবিবুর রহমান খান আর দেরি করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন। কোথায় যাব? আর কোথায় ঢাকা-কলকাতা। আমি বললাম কলকাতায় আর কত যাব? হাবিব বললেন, তা হলে কলকাতা থেকে বাইরে কোথাও যাই। জায়গা নির্ধারণ করার দায়িত্ব আপনার (মানে আমার)। তা কি আর বলতে এ কাজটা আমার জন্যে অবধারিত। সঙ্গে সঙ্গে বললাম চলুন এবার ঐতিহাসিক স্বাধীন বাংলার রাজধানী গৌড় আর পাণ্ডুয়া দেখে আসি। প্রশ্ন সেগুলো কোথায়? বললাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জের অপর পাড়ে বর্ধমানের মালদা জেলায়। এরপরেই দলভারি হতে থাকল। মোট সাতজন প্রস্তুত হলেন প্রস্তাবিত গৌড় দর্শনে। তখনও বেশির ভাগেরই গৌড় সম্বন্ধে তেমন ধারণা ছিল না।
প্রথমে ভেবেছিলাম কলকাতা হতে ট্রেনে ‘মালদা’ গিয়ে স্থানীয় কোনো মাইক্রোবাস ভাড়ায় নেবো। তবে কলকাতা হতে খবর নিয়ে হাবিব জানলেন যে সড়ক পথে যাওয়াটাই উত্তম কারণ ট্রেনের সময় এবং বিড়ম্বনা হতে পরিত্রাণ পাবার সহজ উপায় সড়ক পথ। সড়ক পথে যাওয়ার এবং মালদাতে থাকার হোটেল বুকিং সব ব্যবস্থাই সম্পন্ন হলো। এ ব্যবস্থা হাবিবের মাধ্যমেই হয়েছিল। টিমে হাবিব আর আমার পরিকল্পনায় যোগ দিলেন ডা. নাসরুল্লাহ, ড. তানভীর আহমেদ খান, হাবিবের দুই বন্ধু শমসের এবং শাহাবুদ্দিন এবং সর্বশেষে যোগ দিলেন আমাদের ভ্রমণ গ্রুপের অন্যতম সদস্য জাকারিয়া। এদের সবার পরিচয় আমার একাধিক ভ্রমণ কাহিনীতে রয়েছে তাই নতুন করে পরিচয় দিলাম না। এ সফরের উদ্যোক্তা হাবিবুর রহমান খানের মন পারিবারিক কারণে খারাপ থাকলেও মেজাজ বেশ ফুরফুরে ছিল। কারণ এর মধ্যেই জানতে পেরেছেন যে তার প্রযোজিত ছায়াছবি ‘শঙ্খচিল’-এ অভিনয়ের জন্যে নায়িকা কুসুম সিকদার এবং শিশু শিল্পী হিসেবে তার ছেলের ঘরের নাতনী সাঁজবাতি শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্যে রাষ্ট্রীয় পুরষ্কার পেতে যাচ্ছে। ছবিটি গৌতম ঘোষ পরিচালিত যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছিল। আমার ভ্রমণ সঙ্গীদের আদি দলটি গঠিত হয়েছিল ২০১২ সালে জর্ডান সফরের মধ্যদিয়ে (জর্ডান নদীর তীরে দ্রষ্টব্য)। দলটি মাঝে-মধ্যে কলেবরে কমলে বা বাড়লেও সফর পাগল হাবিবুর রহমান বাদ পড়েন না।
যাই হোক আমাদের সফর শুরু হলো। আমরা আগেই সীদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে একবার মৈত্রী ট্রেনে ঢাকা-কলকাতা যাব। এর অন্যতম কারণ যে এদিকের কাস্টমস পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ঢাকায় আর কলকাতাতে কাস্টমস ইমিগ্রেশন সবই সম্পন্ন হয়। যথারীতি নিয়মমাফিক অগ্রিম টিকিট কেনা হলো। আমার সঙ্গে কনিষ্ঠপুত্র সাফাকও তৈরি হলো। তবে সে কলকাতার বাইরে যেতে পারবে না তার কিছু কাজের চাপে। আমরা ঢাকার ক্যান্টনম্যান্ট স্টেশন হতে কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে ট্রেনে চাপলাম। পুরো ট্রেন এসি আর চেয়ার কোচ। সব মিলে প্রায় ৪৫০ জন যাত্রী। সম্পূর্ণটাই ভর্তি।
ঢাকায় কাস্টমস ইমিগ্রেশন শেষ করতেও বেশ সময় নেয় কারণ স্টেশনটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও ছোট। তথধিক ছোট স্টেশনের দালানটি। কাজেই হুড়োহুড়ি আর গাদাগাদি হয়েই থাকে। এর আগে ২০১১ সালে প্রথম ট্রেন চেপে কলকাতা গিয়েছিলাম। প্রচুর সময় লেগেছিল দর্শনা আর ভারতের গেদেতে কাস্টমস সম্পন্ন করতে। সব যাত্রীদের দুবার করে মালপত্র নিয়ে নামতে হয়েছিল (বাংলা-বিহার প্রান্তরে দ্রষ্টব্য)। অন্তত সে বিড়ম্বনা লাঘব হয়েছে এবার। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল। সবাই বাসা থেকে হালকা নাস্তা করে আসার কথা ছিল তবে তেমনটা হয়েছে বলে মনে হয় না কারণ ভোর ৬টায় স্টেশনে আসতে হয়েছে। কাজেই প্রথমে নাস্তার অর্ডার নিতে এল ক্যাটারিংয়ের ওয়েটার। তার পেছনে টিটি এবং এসি কোচের সুপারভাইজার। সুপারভাইজার আমাকে দেখে অভিবাদন দিয়ে বললেন, স্যার খেয়াল করিনি যে আপনি ট্রেনে। ২০১১ সালে আপনি ট্রেনে চড়েছিলেন সে সময়ে আমরা আপনাকে আমাদের হাল শুনিয়েছিলাম। তাঁর কথা শেষ না হতেই ট্রেন এক্সামিনার যোগ দিলেন। তিনিও জানালেন যে ওই সময় থেকেই তিনি এই ট্রেনে ডিউটি করে আসছেন। তখনও যে অবস্থায় ছিল এখনও তাদের সেই অবস্থানই রয়েছে।
ওই সময়ে তারা বলেছিলেন যে তাদের প্রতিপক্ষ ভারতীয় রেলওয়ে স্টাফদের বাংলাদেশে অবস্থানের জন্যে ডলারের হিসাবে ভাতা দেয়া হয়। দিন প্রতি ৭২ ইউএস ডলার। অথচ বাংলাদেশী রেলওয়ে কর্মচারী যারা কলকাতায় রাত কাটান। তাদের জন্য আজ পর্যন্ত কোনো আলাদা ভাতা নির্ধারণ করা হয়নি বা বৈদেশিক মুদ্রাতে পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। তাদের নিজেদের পয়সাতেই ভারতে অবস্থানকালে থাকা-খাওয়া মিটাতে হয়। আমার মনে পরে যে ওই সময় আমি রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এ বিষয়টি জানিয়েছিলাম। আজ প্রায় ৭ বছর পর একই অনুযোগ শুনতে পেয়ে দুঃখই পেলাম। এত দিনে আমাদের দেশ মধ্যম আয়ের পথে রয়েছে বলে যখন সরকার উৎসব উদযাপন করছে তখনও তাদের এই নিম্ন বেতনভূক কর্মচারীদের সামান্য ভাতার ব্যবস্থাও করতে পারছে না বা করছে না। আমি বললাম যে যদি সম্ভব হয় তবে এ বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো আর না হলে নূন্যতম আমি যা করতে পারি তা হল আমার কোনো লেখনীতে তুলে ধরব। তাদের একথা আমার মনে রয়েছে তবে এখন পর্যন্ত তেমন কাউকে বলতে পারিনি।
কিছুক্ষণ পর নাস্তা এবং আরও পরে দুপুরের খাবারও সরবরাহ করলো তারা। বিল খুব বেশি নাহলেও খাবারের মান খুব ভাল ছিল তা বলা যাবে না। এদিক থেকে ভারতের রেল কর্তৃপক্ষ বেশ এগিয়ে। লম্বা সফরে বেশ কয়েকবার উচ্চক্লাসের যাত্রীদের খাবার ও নাস্তা সরবরাহ করে যার ন্যূনতম দাম টিকিটের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। যারা দূরপাল্লায় ভারতীয় ট্রেনে সফর করেছেন তাদের অভিজ্ঞতা বেশ সুখকর। এতদিনে আমরা আমাদের ট্রেন সার্ভিসে এমন কিছু চালু করতে পারিনি। যেহেতু পথে যাত্রীদের ট্রেন ছাড়বার বিধান নেই সেহেতু আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থাও নেই।
যাই হোক ট্রেনের সফর বেশভালই ছিল তবে যারা বিমান যাতায়াতে অভ্যস্থ তাদের জন্যে সময়টা একটু বেশি। কলকাতা স্টেশনে পৌঁছুতে স্থানীয় সময় প্রায় চারটা বেজে গেল। প্রথমদিকে থাকায় তাড়াতাড়ি বের হতে পেরেছিলাম তবে ট্যাক্সি পেতে সময় লেগেছিল। কলকাতায় হাবিবের কথিত এবং কমন মামু শার্শার জনাব মান্নান আমাদের সঙ্গে সড়ক পথে গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। সঙ্গে আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় জয়ন্ত শর্মা এবং কলকাতার আড্ডার আরেক সদস্য অলক মুখার্জি। কলকাতা মানেই আমাদের সঙ্গে এই দুজন। এ দু’জন হাবিবের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে আমাদের সকলের সঙ্গেই যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। যাদের বাদ দিয়ে আমাদের কলকাতার কোনো সফর পূর্ণ হওয়ার নয়। মাঝে-মধ্যে দু’জনই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে ঢাকাতেও আসা-যাওয়া করে। জয়ন্ত শর্মার মাধ্যমেই এবারের সফরের ব্যবস্থা করেছেন হাবিবুর রহমান। জাকারিয়া দেরি করাতে ট্রেনের টিকিট পায়নি তাই সন্ধ্যায় বিমানে পৌঁছবার কথা। আমাদের নিবাস হবে সল্ট লেকের একটি গেস্ট হাউস। যেখানে আমরা আগেও ছিলাম।
পাঠকদের কাছে এই দুই ব্যক্তির পরিচয় না দিলেই নয়। জয়ন্ত শর্মা এক সময় ছোটখাট ব্যবসা করতেন। তিনি এক সময়ের নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা। বয়স প্রায় ৭৪ বছর। এখন তেমন কিছু করেন না তবে জয়ন্ত মানেই আমাদের কলকাতার গাইড। অতি উৎসাহের সঙ্গে প্রায় সারাদিন আমাদের সঙ্গে কাটান আর যখন যা প্রয়োজন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে সে কাজগুলো করেন। বাজার করার অপরিহার্য গাইড জয়ন্ত শর্মা। লম্বা একহারা গড়ন কিন্তু দারুণ উদ্যোমী একজন মানুষ। এমনই অবস্থা যে জয়ন্ত ছাড়া কলকাতায় আমরা প্রকৃতপক্ষে বিকল। জয়ন্ত শর্মা একজন পারিবারিক সদস্যই হয়ে গিয়েছেন। কলকাতার বাইরে এ সফরেও জয়ন্ত আমাদের গাইড।
হাবিবের সঙ্গে জয়ন্ত শর্মার পরিচয় প্রায় ৩৮ বছর গড়িয়েছে। সেই হতেই এক ধরনের হরিহর আত্মা। অলক মুখার্জির সঙ্গেও প্রায় ৩০ বছরের পরিচয় চলচ্চিত্র নির্মাণের সূত্রে। অলক এক সময় ব্যাংকে চাকরি করতেন বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। দারুণ আড্ডাপ্রিয় মানুষ। এমন আরও কয়েকজন যাদের সঙ্গে আমরা এখন সবাই পরিচিত। আগেই বলেছি কলকাতায় কাটিয়ে আমরা মালদার পথে রওয়ানা হবো। তবে রাস্তায় একরাত থাকব বহরমপুরে। এর কারণ আমাদের সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন মুর্শিদাবাদ দেখেননি। আমি অবশ্য দুবার মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম কাজেই আমার উৎসাহ তেমন না থাকলেও আমাদের অন্যতম সদস্য ড. নাসরুল্লাহ মুর্শিদাবাদ বেড়াতে আগ্রহী। তবে তার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখলাম জাফরগঞ্জে মীর জাফরের এবং তার বংশের কবরগুলো দেখার। তার মতে মীর জাফরের কারণেই ইংরেজ শাসন এবং উপমহাদেশের আধুনিক হবার দ্বার উন্মোচন। জানি না তার এ ধারণার সঙ্গে কতজন একাত্ম হবেন। তবে এগুলো ইতিহাসের ‘যদি।’ যদি সিরাজ পরাজিত না হতেন তবে বাংলা কি স্বাধীন থাকতো বা আধুনিক রাষ্ট্র হতো। এসবের উত্তর কোনো পণ্ডিতের পক্ষেই দেয়া সম্ভব বলে মনে হয় না।
কলকাতায় দুদিন ছবি দেখা আর আড্ডা দেয়া ছাড়া আমাদের তেমন কিছুই করার ছিল না। জাকারিয়া সেদিন রাতে পৌঁছে ছিল তবে ঠিকানা বিভ্রাটে আমাদের খুঁজে না পেয়ে তার বন্ধুর বাড়িতেই রাত কাটিয়েছিল। কলকাতায় থাকাকালীন দ্বিতীয় দিনেই হাবিব পারিবারিক কারণে ঢাকায় ফিরে এল। এরপর সম্পূর্ণ সময় আমরা হাবিবের অনুপস্থিতি দারুণভাবে উপলব্ধি করেছি। আমাদের আড্ডা আর ভ্রমণের মধ্যমনি বরাবরই হাবিব। সাফাকও দ্বিতীয় দিনে ঢাকায় চলে এল। আর আমরা সকাল ৮টার দিকে বহরমপুর হয়ে মুর্শিদাবাদ এবং মালদার পথে রওয়ানা হলাম। কলকাতা হতে মালদা সরাসরি গেলে ৩০০ কি. মি.-এর বেশি যেহেতু আমরা বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ হয়ে যাব তাই দূরত্ব এবং সময় দুটোই বেশি লাগবে। তবে বহরমপুর মধ্যহ্নভোজের সময়েই পৌঁছব বলে আশা রাখি। সকালেই জাকারিয়া এসে যোগ দিলেন। কিছুক্ষণ পর জয়ন্ত গাড়ি নিয়ে হাজির। একটি মাইক্রোবাস। আটজন যাত্রী মালামাল সব নিয়ে রওয়ানা হলাম। মাইক্রোটি আহামরি কিছু নয়। লিকলিকে লম্বাটে ড্রাইভার। বয়সে তরুণ। প্রায় সড়কই তার চেনা। তবে আশপাশে চেনার কথা নয়। ড্রাইভারের নাম রাজু দেবনাথ মনে হলো জয়ন্তর পাড়ার বা পূর্ব পরিচিত। ছেলেটির মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। একেবারে ভাবলেশহীন মনে হলো। ড্রাইভার বাসটি চালায় মাত্র পরিষ্কার করা বা ধোয়ামোছা বোধ হয় বহুদিন করা হয়নি।
আমরা কলকাতা ছেড়েছি প্রায় একঘণ্টা। শহর থেকে বের হয়ে স্টেট রোড ধরে চলছি। দুই লেনের স্টেট হাইওয়ে বলে পরিচিত। আশপাশে গ্রাম্য বাড়িঘর বেশিরভাগই টালির চাল। বড় গ্রামগুলোর পাশে রাস্তার ধারে উন্মুক্ত বাজার। হরেক রকমের শাক-সবজি। তখনও শীতের মৌসুমের শাক-সবজি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। টমেটোসহ সব ধরনের সবজি, কাঁচা মরিচ, বেগুন অন্যান্য শাক। কলকাতায় যতবার এসেছি বাজারের শাক-সবজি দেখেছি কেমন যেনো শ্রীহীন-স্বাস্থ্যহীন মনে হয়েছে। গ্রাম্য বাজারেও তেমন দেখলাম। মনে হয় যে আমাদের দেশের শাক-সবজিগুলো বোধ হয় বেশি হাইব্রিড যে কারণে দেখতেই ভালো লাগে। পশ্চিম বাংলায় বোধ হয় তেমন হাইব্রিড সবজি চাষ হয় না।
কলকাতার বাইরের লোকালয়গুলো দেখলে মনে হয় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে এবং অর্থনৈতিকভাবে তেমন সচ্ছল নয়। ছোট ছোট শহর এমন কি কলকাতার বেশিরভাগ দালান- কোঠাগুলোতে, বিশেষ করে বসতবাড়িগুলোর নকশা দেখে মনে হয় পুরনো ধাঁচের নকশা করা বাড়িঘর। সহজে পরিবর্তন করা হয় না। ঢাকা বা ঢাকার বাইরের বহু জেলা শহরেও পুরনো ধরনের পাকা বসতবাড়ির দেখাও কম মিলে।
আমরা স্টেট রাস্তা ছেড়ে পোলট্র্রিপণ্ড নামক জায়গায় রেললাইন পার হয়ে কৃষ্ণনগরের হাইওয়েতে উঠলাম। ততক্ষণে সবাই ক্ষিদে অনুভব করছিলেন। তাছাড়া একটানা জনবহুল রাস্তায় গাড়ি চালানোতে আমরাও ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। কিন্তু সামনে এগুতে রাস্তার দু’পাশে প্রচুর মোটরসাইকেল আরোহী তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে জটলা দেখা গেল। যদিও রাস্তা চলাচলের জন্যে উন্মুক্ত তবু বেশ জটলা। তেমন কোনো উত্তেজনা বা হৃদয় কাঁপানো স্লোগান নেই। পেছন থেকে জয়ন্ত বললেন যে কয়েকদিন পর পঞ্চায়েত নির্বাচন আর এখন চলছে মনোনয়ন দাখিলের সময়।
ও-তাইতো মনে পড়ল আজ সকালেই খবরের কাগজে দেখলাম বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি)-এর অভিযোগ যে তাদের প্রার্থীরা বহু জায়গায় মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি কারণ তৃণমুলের ‘গুন্ডারা’ জমা দিতে দেয়নি। বিজেপি পশ্চিমবাংলার রাজ্যপালকে অভিযোগ করেছিল। রাজ্যপাল পশ্চিমবাংলার নির্বাচন কমিশনকেও তলব করে বলেছে কিন্তু তেমন কোনো কাজ হয়নি। পশ্চিমবাংলার বিজেপি বিষয়টি হাইকোর্টে উঠালে হাইকোর্ট এই বলে খারিজ করে দেয় যে বিষয়টি দেখার এখতিয়ার রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকারের। প্রসঙ্গত, ভারতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। এসব নির্বাচনে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো এখতিয়ার নেই। অবশ্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং যথেষ্ট স্বাধীন। স্বাধীন হলেও সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের সহযোগিতা ও আন্তরিকতার প্রয়োজন।
ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৩ কে এবং ২৪৩ কে-এর এ অনুযায়ী গঠিত এবং রাজ্যের সব স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা। এই ক্ষমতা দেয়া হয় সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯২ সালে নরসীমা রাও-এর সময়। রাজ্য নির্বাচন কমিশনকেও অনেক ক্ষমতা দেয়া আছে তবে রাজ্য সরকারের জনবল নিয়েই এসব নির্বাচন পরিচালনা করতে হয়। তবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে কারিগরি সহায়তার অনুরোধ অবশ্যই করা যায়।
আমরা নির্বাচনী ভিড় পার হয়ে জাতীয় মহাসড়কে উঠলাম। এনআই ৩৪। সবকটির কাজ এখনও শেষ হয়নি। রানাঘাট এবং ব্যারাকপুর পেছনে রেখে প্রায় আধাঘণ্টা পর আমরা কৃষ্ণনগরের হাইওয়ের পাশের বিখ্যাত এক উন্মুক্ত রেস্তোরাঁতে বলতে গেলে গণ-রেস্তোরাঁতে পৌঁছলাম। এই রেস্তোরাঁতে সমগ্র পশ্চিম বাংলায় কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত স্বরভাজার জন্যে বহুল পরিচিত। আমার মনে পড়ে এই রেস্তোরাঁটিতে ২০১১ সালে মুর্শিদাবাদে আসা-যাওয়ার পথে দুপুরের খাবার খেয়েছিলাম। তখন এত বড় ছিল না। বাঁশের অস্থায়ী স্থাপনা ছিল। এখন বিশাল বড় হয়েছে। পাকা উন্মুক্ত হল ঘরের মতো খাবারের জায়গাটি। টেবিল পাওয়াই দুষ্কর। পাশে আরও দুটি একই ধাঁচের রেস্তোরাঁ রয়েছে। ভাগাভাগি করে ব্যবসা করে। স্বরভাজার জন্যে এই রেস্তোরাঁর সুনাম অনেক বেশি। রেস্তোরাঁটির নাম শংকর মিষ্টান্ন ভান্ডার। আমরা নাস্তা করতে এখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটালাম। সময়ের অভাবে কৃষ্ণনগর শহরের ভিতরে প্রবেশ করা হয়নি। কৃষ্ণনগর অনেক পুরনো জনপদ। বর্তমানে নদীয়া জেলার সদর। তবে পুরনো জনপদ হলেও পৌরসভা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে ১৮৬৪ সালে। নদীয়া এ অঞ্চলের অন্যতম পুরনো পৌরসভার একটি। অনেকেই মনে করেন কৃষ্ণনগরের সবচাইতে ক্ষমতাধর ব্যক্তি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নামানুসারেই এই ছোট শহরের নাম রাখা হয়েছিল। আবার অনেকেই মনে করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামে। তবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজপ্রাসাদ এবং তার স্থাপিত স্কুল কলেজ এবং বহু বিদ্যাপীঠ ও জনহিতকর কাজের জন্যে তিনি অমর হয়েছেন। কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ ভারতবর্ষের প্রথমদিকের সরকারি কলেজ। কলেজটি স্থাপিত হয় ১৮৪৬ সালে। কৃষ্ণনগর এক সময় সর্ববাংলায় মাটির মূর্তির তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ। আজও রয়েছে তবে আগের মতো সেই রমরমা অবস্থা নেই। তবে এই অঞ্চলে বিভিন্ন জাতের মিষ্টির মান বেশভালই রয়েছে। স্বরভাজার কথাতো উল্লেখ করেছি। শংকরের স্বরভাজাই এ অঞ্চলের সবচাইতে সুস্বাদু বলে পরিচিতি।
দুপুরের আগেই আমাদের বহরমপুরে পৌঁছবার কথা। রাস্তার দু’পাশে বাংলার চিরায়ত সবুজ। ক্ষেতগুলো থেকে ধান বহু আগেই কাটা হয়ে গেছে। এখন বিভিন্ন প্রকারের রবি শষ্যে ক্ষেত সবুজ হয়ে আছে। কোথাও কোথাও সর্ষের ক্ষেত। হলুদ ফুলগুলোর উপর বাতাসের ছোয়ায় ঢেউ খেলছে। গ্রামগুলো বেশ দূরে। রাস্তার দু’ধারের গ্রামগুলো তুলনামূলকভাবে বর্ধিষ্ণু। এই ন্যাশনাল হাইওয়ে এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। বেশির ভাগ জায়গায় তৈরিরত রাস্তার ওপর দিয়েই যেতে হচ্ছে। কোথাও পুরনো রাস্তার ব্যবহার। দু’ঘণ্টা পর আমরা পলাশী বাইপাশে উঠলাম। জাকারিয়া বললেন পলাশী গেলে হতো না? আমি বললাম অবশ্যই হতো তবে আগেভাগে বললে হয়তো প্রোগ্রামের মধ্যে সমন্বয় করা যেত। আমরা পলাশী বাইপাস দিয়ে চললাম। পলাশী নামক ঐতিহাসিক এ গ্রামটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমনভাবে জড়িত যে পলাশী ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচিতই হতে পারে না।
আমরা প্রায় দুটোর কাছাকাছি সময়ে বহরমপুরে পৌঁছলাম। ছোট শহর বহরমপুর। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গরিব জেলা সদর। আমাদের থাকার জায়গা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের বহরমপুর গেস্ট হাউসে। সরকারি সংস্থা। যেমন হবার তেমনই। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার আগেই অভ্যর্থনা কেন্দ্র হতে জানালো যে সন্ধ্যায় মতিঝিল পার্কে ‘লাইট এন্ড সাউন্ড শো’ হয়। দুপুরে খাবার পর পর বের হয়ে গেলে কাশিমবাজার দেখে মতিঝিলে যেতে পারব। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো’ অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়। মাত্র কয়েক বছর আগেই এটা নতুন সংযোজন হয়েছে। মতিঝিল-কাশিমবাজার আমি আগেও গিয়েছি। মতিঝিলে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো-র জায়গা কোথায় ভাবছিলাম। কারণ মতিঝিল এর আগে যখন দেখেছি মোটামুটি পরিত্যক্তই দেখেছি। সিরাজের খালা ঘষেটি বেগমের প্রাসাদ ছিল ধ্বংসস্তূপে আর ঝিলটি ছিল অরক্ষিত। অবশ্য তখন শুনেছিলাম যে ঝিল সংস্কারের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে রাজ্য সরকার।
আমরা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। বরহমপুর বেশ পুরনো জনপদ। সিরাজের পতনের পর বহরমপুরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রভাব থেকে যায়। সিরাজ কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিল্কের সুতার কারখানা ধ্বংস করার পর বহরমপুর হয়ে উঠে বাজার। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর হতেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের সৈনিকদের জন্যে সেনা ছাউনি হিসেবে বহরমপুর গড়ে তোলে। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত বহরমপুর ছিল তৎকালীন ভারতের অন্যতম বৃহৎ সেনা ছাউনি। ১৮৭৬ সালে বহরমপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে এখানে সিপাহী বিল্পবীদের সঙ্গে কয়েক মাস যুদ্ধ চলে কোম্পানির অনুগত সৈনিকদের। বহরমপুরের অন্যতম পুরাতন কলেজ কৃষ্ণনাথ কলেজ। কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৩ সালে রাজা কৃষ্ণনাথের নামে। যিনি কোম্পানীর কৃপায় বহরমপুরের রাজা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।
ছোট শহর বহরমপুর। এখন বড় সেনা ছাউনি নেই তবে ওই জায়গায় বিএসএফের সদর দপ্তর রয়েছে। শহরের বাজারগুলো একেবারেই সাদামাটা। আধুনিক শহর হিসেবে যে রকম হবার কথা বহরমপুর তেমন নয়। তবে শীতের মৌসুমে অভ্যন্তরীণ এবং বেশ-বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা থাকে।
আমরা ভাগীরথীর তীর ধরে মতিঝিলের দিকে যাচ্ছি। পেছনে শমসের আর শাহাবুদ্দিন নিজেদের মধ্যেই কথা বলছেন। নাসরুল্লাহ নদীর নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি নদীর নাম বললাম। নদীর পাড়ের রাস্তাটিকে নতুনভাবে পুণর্নির্মিত মনে হলো। পূর্বপাড়ের এ রাস্তার পশ্চিমপাশে মানে নদীর দিকে গ্রিল দিয়ে ঘেরা। ২০১১ সালে এ রাস্তা এমন ছিল না। বেশ খারাপ অবস্থায় ছিল। আমরা নদীর পাড় ছেড়ে একটু ভিতরের দিকে এগিয়ে কাশিমবাজারের রাস্তায় প্রবেশ করলাম। যেহেতু আমি এ জায়গার সঙ্গে পরিচিত তাই আমাকেই গাইড হিসেবে কাজ করতে হলো (আমার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে ‘বাংলা-বিহার প্রান্তরে’ নামক ভ্রমণ কাহিনীতে)। কাশিমবাজারে প্রথমদিকে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিল্ক ব্যবসা ছিল। কিন্তু বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসার পর হতেই ‘ডাচ’রা চলে যায়। ওই সময়কার ডাচ কোম্পানির গভর্নরসহ যাদের মৃত্যু হয়েছিল তাদের সমাধিস্থান রয়েছে রাস্তার পাশেই। এটাই প্রথম ইউরোপিয়ান আঞ্চলিক কবরস্থান। এর কিছু দূরেই বৃটিশ কবরস্থান। এদের বেশির ভাগ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর এবং কলেরায় মৃত্যুবরণ করেছিল।
আমি কাশিমবাজার রাজবাড়ী দেখিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাশিমবাজারের সিল্ক সুতার কারখানার ধ্বংসস্তূপ সবাইকে দেখিয়ে মতিঝিল পার্কের দিকে রওয়ানা হলাম। এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট আগের তুলনায় অনেক ভাল হয়েছে। মমতা ব্যানার্জির সরকার মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে পর্যটন শিল্পকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয়। মুর্শিদাবাদের অন্যতম ঐতিহ্য সিল্ক। তাছাড়া কৃষিকাজ তো রয়েছেই। এ জেলার জনসংখ্যার প্রায় ২৪ ভাগ মুসলমান যাদের সিংহভাগের বাস মুর্শিদাবাদ শহরে।
বলছিলাম কাশিমবাজার-এর কথা। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাগীরথীর তীরে কাশিমবাজার ছিল বড়ধরনের বন্দর এবং এ অঞ্চলের সিল্ক ছিল বিশ্বখ্যাত। এখানে প্রথম ডাচরা সিল্কের ব্যবসায় জড়িত হলেও ক্রমেই বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামনে টিকতে পারেনি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ডাচরা চলে যাওয়ার পর বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করে। ঐতিহাসিক সূত্র মতে, কাশিমবাজারে কারখানা গড়ে উঠে ১৬৪৯ সালে। এর বাইরেও তৎকালীন হিন্দুস্থানের বহু জায়গায় আরও কারখানা গড়ে তোলে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এর মধ্যে হুগলি এবং কলকাতাতে ফ্যাক্টরি ছিল। সিরাজউদ্দোলার সঙ্গে বিবাদ বেঁধেছিল ট্যাক্স ধার্য করা নিয়ে। একপর্যায়ে নবাব এসব কারখানা দখল করে নিয়েছিলেন।
আমরা কাশিমবাজার ছেড়ে কিছুক্ষণের মধ্যে মতিঝিল পার্কের নির্ধারিত গাড়ি পার্কিংয়ে পৌঁছলাম। জয়ন্ত গেলেন পার্কে প্রবেশের টিকিট কিনতে। আমরা পাশের এক ছাপড়া দোকানে চায়ের জন্যে বসলাম। তখনও বিকেলের আলো ডুবেনি। সূর্য অস্তগামী হওয়ার আয়োজন শুরু করেছে। আমরা যেখানে বসেছি সেখান থেকে পার্কের গেট প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে। ছোট একটি গ্রাম্য জনবসতি। এখানে এই পার্কে যে প্রচুর লোক আসে তার প্রমাণ আশেপাশে প্রচুর ‘রাস্তার খাবারের’ দোকান। এগুলোর মধ্যে ফুচকা, চটপটি আর আইসক্রিম প্রধান। আমরা কয়েকজন দোকানের স্বল্পপরিসরে চেয়ারে বসা। সামনে রাস্তার অপর পাড়ে শমসের আর শাহাবুদ্দিন একটি বেঞ্চে বসে স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে গল্পে বিভোর। স্থানীয় লোকগুলো মুসলিম সম্প্রদায়ের। পরে শুনলাম এখানে প্রচুর মুসলমানদের বাস। শাহাবুদ্দিন বললেন, যে তাদের ভাষ্যমতে মমতা ব্যানার্জি ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখলেও পিছিয়ে পরা মুসলমান সংখ্যালঘুদের জন্যে প্রচুর কাজ করেছেন এবং করছেন। মুর্শিদাবাদকে পর্যটন নগরী তৈরি করার প্রয়াশে রয়েছেন। এর অন্যতম উদাহরণ মতিঝিল পার্ক।
মতিঝিল লেক কেটেছিলেন আলীবর্দী খানের জামাতা নওয়াজিশ উদ্দিন যিনি ঘষেটি বেগমকে বিয়ে করেছিলেন। এখানেই তিনি নিজের থাকার জন্যে প্রাসাদও তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র বলে চিহ্নিত করে সিরাজ এখানকার প্রাসাদও দখলে করে নেন। সেই থেকে এটি সিরাজের বাসস্থান হিসেবে পরিচিত। সিরাজের পতনের পর ক্লাইভ বাংলার দেওয়ানী না পাওয়া পর্যন্ত এটিকে বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এখানেই নওয়াজিশ উদ্দিনের সমাধি রয়েছে।
আমরা টিকিট দেখিয়ে নবনির্মিত মতিঝিল পার্কে প্রবেশ করলাম। মুর্শিদাবাদের এই পার্কটি পর্যটকদের জন্য অবশ্য দর্শনীয়। আমরা রাজকীয় ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। সোজা টানা পূর্ব-পশ্চিম রাস্তা। বাগানটি তিন ভাগে কয়েক একরের উপরে নির্মিত। সবুজ ঘাষের চত্বর। জায়গায়-জায়গায় বসার স্থান আর ময়লা ফেলার ঝুড়ি রয়েছে। বাহির হতে কোনো খাবার নিয়ে প্রবেশ নিষেধ একমাত্র পানি ছাড়া। পার্কের পশ্চিম মাথায় একেবারে শেষ প্রান্তে লাইট এন্ড সাউন্ড শো। এটাই সেই মতিঝিল অথচ বুঝবার উপায় নেই। শুধুমাত্র ব্যাটারি চালিত গাড়ি প্রায় দেড় কিলোমিটার লম্বা রাস্তাটিতে চলে। বাকি পথ হেঁটে যেতে হয়। এখানে রাত্রি যাপনের জন্যে মোটেল রয়েছে। রয়েছে ছোট রেস্তোরাঁ। হলরুম এবং গেটের কাছেই খাবারের দোকান। পার্কটিকে বাংলার নবাবী ইতিহাসের থিমপার্ক বলা যেতে পারে। শুধু সবুজ ঘাসই নয় বরং বহু অর্থের খরচে সবুজ গাছের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন সংস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এর রক্ষণাবেক্ষণ করে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন সংস্থা।
পার্কে প্রবেশের পর প্রথমেই হাতের বামে দেখা যাবে বাংলার দেওয়ান মুর্শিদাকুলি খাঁকে যার একটি প্রমাণ সাইজ ব্রোঞ্জের মূর্তি রয়েছে। বেদীর উপরে ছোট করে ইংরেজি-বাংলা আর হিন্দিতে মুর্শিদকুলি খাঁর পরিচিতি দেয়া হয়েছে।
মুর্শিদকুলি খাঁ গরিব ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণাঞ্চলের কোনো এক মোগল দরবারি তাকে খরিদ করে পড়ালেখা করিয়ে বড় করে তোলেন। পরে তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের নেক নজরে পরলে তাকে তৎকালীন মোগলবাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীরনগরে (বর্তমানের ঢাকায়) আওরঙ্গজেবের নাতি আজিম উস্-সান -এর অধীনে দেওয়ান বা খাজনা আদায়ের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং রাজকীয় কোষের জন্যে অর্থ ছাড় দেয়ার ক্ষমতাও দেয়া হয়। আজিম-উস্-সানের সঙ্গে ক্রমেই অর্থ বরাদ্দ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে সম্রাটের সম্মতিতে তিনি দেওয়ানি স্থানান্তরিত করে এককালের মকসুদপুর নামক গ্রামের নাম বদল করে রাখেন মুর্শিদাবাদ। আওরঙ্গজেবের পর ফররুখশিয়রের সময় তিনি নিজেকে বাংলার স্বাধীন নবাব হিসেবে ঘোষণা দেন এবং ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন।
মুর্শিদকুলি খাঁকে ছেড়ে পার্কের মাঝামাঝি আমরা। পেছনে এখানকার রেস্ট হাউস। উল্টোদিকে মাঠের মাঝে বসার জায়গায় মামু বসা। বললেন তিনি হেঁটে হেঁটে সামনে যেতে পারবেন না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। নাসরুল্লাহও বসে পরলেন। আমরা পাঁচজন হেঁটে-হেঁটে নবাব আলীবর্দী খানের মূর্তির সামনে দাঁড়ালাম। মুর্শিদকুলি খাঁর মতোই আলীবর্দী খাঁর ছোট পরিচিতি ও ইতিহাস লেখা। সেখান থেকে সামনের ফোয়ারার আগেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার মূর্তি। সেখানে ছোট ইতিহাস লেখা। পলাশীর যুদ্ধের উল্লেখ এবং বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা হারানোর বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা আরও কিছুদূর এগুতে জাকারিয়াকে পেলাম। তিনি আমাদের আগেই ছিলেন। এসে বললেন, সামনে পলাশীর যুদ্ধের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে অদ্ভুত সুন্দরভাবে।
সামনে আরও একশত মিটার যেখানে এ পার্কের শেষ সীমানা। সেখানেই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হওয়ার কথা। হাঁটতে হাঁটতে বললাম মমতা ব্যানার্জি ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন। মুর্শিদাবাদ এবং বাংলার নবাবদের কাহিনীর সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার বিপর্যস্ত জীবনকেও তুলে ধরেছেন। এখানেই মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে বর্তমান ভারতের অনেক নেতাদের তফাৎ। এই একটি জায়গা যেখানে ন্যূনতমপক্ষে ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা হাঁটতে-হাঁটতে পার্কের শেষ মাথায় পৌঁছলাম। ইতিমধ্যেই পার্কের বাতি জ্বলে উঠেছে। রং-বেরংয়ের বাতিতে পার্ক স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে।
আমরা ঝিলের কাছাকাছি। সামনে হাতি, ঘোড়া এবং পদাতিক বাহিনীর প্রমাণ সাইজের মূর্তির সমাহারে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পলাশী যাত্রার চিত্র ফুটে উঠেছে। তার একটু সামনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নৌবাহিনী কমান্ডার যার অত্যন্ত পটু যুদ্ধবিদ্যা এবং নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তেইশে জুন, ১৭৫৭ সালে মতিঝিল পার্ক থেকে প্রায় ৪০ কি. মি. দূরে পলাশীর আম্রকাননে স্বাধীন বাংলার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। এরপর সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজদের গোলামি করে ১৯০ বছর।
সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো শুরু হয়ে শেষ হলো ৮টায়। দেখানো হলো নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আর পলাশীর যুদ্ধের বিবরণ। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস তুলে ধরা হলো। এ রকম প্রতিকূল (গরম) আবহাওয়াতে অভ্যন্তরীণ পর্যটকের সংখ্যা কম ছিল না। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো শেষ করে বহরমপুরে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় দশটা। রাতের খাবার শেষ করে রুমে এলাম। আগামী দিন সকালে যৎসামান্য নাস্তা খেয়ে মুর্শিদাবাদ হয়ে মালদার পথে রওয়ানা হবো। মালদার পথে আমরা ফরাক্কা বাঁধের উপর দিয়ে যাব। প্রায় সমস্ত রাস্তাটিই আমাদেরকে অসমাপ্ত এনএইচ-৩০ দিয়ে যেতে হবে।
সকালে যৎসামান্য নাস্তা সেরে মুর্শিদাবাদের দিকে রওয়ানা হলাম। বহরমপুর থেকে প্রায় এক ঘণ্টার রাস্তা। আমরা ভাগীরথীর পূর্বপাড় ধরে যাচ্ছি। নদীর পাড়ে বেশ কয়েকটি ঘাট দেখলাম। ঘাটের সঙ্গে ছোট ছোট প্রার্থনাঘর। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি রাখা। এর আগে এতটা দেখিনি। ভাগীরথীকে পবিত্র নদী মনে করা হয় কারণ গঙ্গানদী বিধৌত এই ভাগীরথী। অনেক পুণ্যার্থীকে নদীতে ডুব দিয়ে পবিত্র হতে দেখলাম। এখানকার নদীর পানি বেশ পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ। রাস্তার পূর্ব-পাড় বেশির ভাগই কৃষি জমি। দূরে-দূরে কিছু বিাড়িঘর। মাঠে গরুর সংখ্যাই বেশি। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর আমরা মুর্শিদাবাদের পুরনো শহরের নবাবি দরবারের বড় গেট দিয়ে প্রবেশ করলাম। এখান থেকে মুর্শিদাবাদের পুরাতন নতুন শহরের শুরু। আমাদের চালকের তো কোনো জায়গাই চেনার কথা নয়। আমি একজন গাইড নেয়ার কথা বললাম। আমি আগে দু’বার এলেও সব জায়গাগুলো চিনতে পারব না। মুর্শিদাবাদ ঐতিহাসিক শহর। উপমহাদেশের ইতিহাসের মোড় যে কয়টি ঘটনায় বাঁক নিয়েছে তার সঙ্গেই মুর্শিদাবাদ এবং এখানে কবরস্থ মানুষগুলোর সম্পর্ক। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাতের জায়গা এই মুর্শিদাবাদ। আমি জাকারিয়াকে একটু মজা করে বললাম, আপনার বাড়িতো মুর্শিদাবাদ নবাবদের সঙ্গে জড়িত। আমাদের দায়দায়িত্ব এখন আপনার নেয়া উচিত? আপনিও নিশ্চয়ই মীরের রক্ত বহন করছেন। জাকারিয়া হাসলেন কোনো মন্তব্য করলেন না। প্রথম থেকেই নাসরুল্লাহ জাফরগঞ্জে মীর জাফরের কবর, হাজারদুয়ারি এবং তার সামনে ইমামবাড়া দেখার আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। বস্তুতপক্ষে আমাদের মুর্শিদাবাদ আসার প্রধান কারণই ছিল অনেকের অনুরোধ। আমি আর জাকারিয়া ছাড়া আর কারোরই মুর্শিদাবাদের অভিজ্ঞতা নেই।
আমরা গাইডের খোঁজে ব্যাটারিচালিত রিকশা স্ট্যান্ডে। এর ধারণক্ষমতা চারজনের। এটাও নতুন সংযোজন। কয়েকজন রিকশাচালক এবং এক্কাগাড়ির (এক ঘোড়ার গাড়ি) কয়েকজন চালক এসে গাইড তথা জায়গাগুলো ঘুরে দেখাবার কথা বলে দাম হাঁকলো। অবশেষ দুটো ব্যাটারিচালিত রিকশা বা হিউম্যানহলার নিলাম। যে কয়টি জায়গায় নিয়ে যাবে তার ফর্দ দেখলাম। পরে হাজারদুয়ারির সামনে এসে নামিয়ে দেবে। নদী পার হয়ে খোশবাগে সিরাজউদ্দৌলার এবং আলীবর্দী খাঁর কবরে যাওয়ার সময় হবে না বা যাবে না।
আমরা দু’ভাগ হয়ে উঠে বসলাম দুটো ব্যাটারিচালিত রিকশায়। হাজারদুয়ারির সামনে দিয়ে আমরা প্রথমে কাঠগোলা প্যালেস দেখতে গেলাম। আমি ভেতরে যাইনি। দুবারতো দেখেছি। আর তাছাড়া কাঠগোলা প্যালেস তেরি হয় ইংরেজদের আধিপত্য কায়েম হবার পর আলীবর্দীর খানের সময়। চারতলা প্যালেসটির সামনে বেশ বড় পুকুর রয়েছে যার চার কোণায় প্রহরী পোস্ট রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই জায়গাটির ইতিহাস বলে যে সিরাজ-উত্তর নবাবদের মনোরঞ্জনের অন্যতম জায়গা ছিল এই কাঠগোলা প্যালেস। এখানে বড় ধরনের গোলাপ বাগান ছিল তাই এ জায়গাকে কাঠগোলা বাগানও বলা হয়। এই প্যালেসের প্রথম কর্তা ছিলেন লক্ষ্মীপাত সিং ডোগার। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি এখানে যে বাগান গড়ে তোলেন এখানেই কালো গোলাপের চাষ হতো। ভিতরে একটি দর্শনীয় মন্দির রয়েছে যা পরেশ নাথ মন্দির বলে পরিচিত। এটি জৈনমন্দির। কারণ ডোগাররা ছিলেন জৈন। তাদের বংশধররা এখনও এ জায়গার মালিক।
যতদূর তথ্য পাওয়া যায়, ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের তিনদিন পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উইলিয়াম মি. ওয়াটস এবং ওয়ালস এখানে মীর জাফরের সঙ্গে দেনা-পাওনা নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। পলাশী যুদ্ধের আগেই নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে মীর জাফরকে নবাব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লিখিত মুচলেকা তৈরি করা হয়েছিল। পলাশী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে এবং মীর জাফরকে নবাব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎকালীন বাংলার অর্থের লুট হয়েছিল। আর এ লুটের ভাগ ওই সময়কার অনেক তথাকথিত জমিদাররাও নিয়েছিলেন।
আমরা কাঠগোলা প্যালেসের আম বাগানের কিছু অংশ দেখলাম। এ অঞ্চলে প্রচুর আম হয়। প্রবেশের পথেই আম বাগান। ডোগার (উড়মধৎ) কোনো জমিদার ছিলেন না। যোগার ছিলেন ব্যবসায়ী কিন্তু সিরাজ-উত্তর নবাবদের এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুনজরে থাকতে বহু কিছু করেছিলেন। কথিত আছে তিনি ওই সময়ের উত্তর ভারতের সবচাইতে সুন্দরী নর্তকীকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মনোরঞ্জনের জন্যে নিয়ে এসেছিলেন। ওই নর্তকীর কোমর ছিল ২২ ইঞ্চি। এখনও ওই সুন্দরীর একটি পেইন্টিং রয়েছে কাঠগোলা প্যালেসের দ্বিতীয়তলায়। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি ছাড়া বেশিরভাগ দর্শনীয় স্থানগুলো এখনও ব্যক্তি মালিকানাধীন। কাজেই পার্কে প্রবেশের টিকিট বাবদ যে অর্থ জোগাড় হয় তার বেশির ভাগই ব্যয় হয় এসব জায়গা রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে।
কাঠগোলা প্যালেস থেকে বের হয়ে আমরা রওয়ানা হলাম জাফরগঞ্জে মীরজাফরের বাড়ি আর পারিবারিক কবরস্থানের দিকে। নাসরুল্লাহ, তানভীর আর শমসেরের দেখার খুব শখ মীরজাফরের কবর। আমি বাইরে গাছের ছায়ায় বসে রইলাম। আমার দ্বিতীয়বার দেখার ইচ্ছা হলো না। সামনেই একটি মসজিদ যা এখন বন্ধ। এখানেই জানাজা পড়ানো হয় মীর জাফরের বংশধরদের। মীর জাফরের বংশধররা এখনও মুর্শিদাবাদ এবং ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এখানে পৌঁছবার আগে মীর জাফরের বাড়ির সামনে নেমেছিলাম। পুরনো হাভেলীটি নেই কিন্তু বিশাল আকারের গেটটি রয়েছে। বাড়ির অংশে এখন শিয়া ইমামবাড়া এবং সমস্ত জায়গাটি মীর জাফরের বংশধরদের নিজস্ব সম্পত্তি। গেটটি এবং এ অংশ স্থানীয়দের কাছে এবং মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে ‘নিমক হারাম দেউরী’ নামে পরিচিত। এখানেই কাছাকাছি কোথাও সিরাজউদ্দৌল্লাকে হত্যা করে তার দেহকে কয়েক টুকরো করে হাতিতে চড়িয়ে মুর্শিদাবাদ প্রদক্ষিণ করানো হয়। দেখানো হয় মা আমেনা বেগমকে। জানিনা নিমক হারাম দেউরী সাধারণ মানুষের মুখে শুনলে মীর জাফরের বংশধরদের মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়।
নিমক হারাম দেউরীর যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে উল্লেখ রয়েছে যে এখানে পলাশী যুদ্ধের আগে সিরাজ বিরোধী শেষ গোপন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন কাশিমবাজার কোম্পানির প্রধান উইলিয়াম ওয়ালস। ওয়ালস বাংলা এবং ফারসি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি এখানে মীর জাফরের মাথায় পবিত্র কোরান শরিফ এবং অপর হাত মীর জাফর পুত্র মীরনের মাথায় রেখে শপথ করিয়েছিলেন যে, পলাশীর যুদ্ধে জাফর সিরাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন এবং তার বদলে বাংলার মসনদে তার বংশধররাই থাকবেন। নিমক হারাম দেউরীর গেটটি আজও কালের এবং ভারত ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়ের সাক্ষী হিসেবে শ্রীহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।
নাসরুল্লাহ ফিরে এসে বললেন, দেখলাম এটা মীর জাফরের নাজাফি বংশের কবরস্থান। আমি বললাম, আর খোশবাগ ছিল আলীবর্দী খাঁর প্রতিষ্ঠিত আফসার বংশের। মীর জাফর ছিলেন আলীবর্দী খাঁর বোনের স্বামী। এই কবরস্থানটি ছিল মীর জাফরের বেগম প্রতিষ্ঠিত কিচেন গার্ডেন। খোশবাগে আলীবর্দী খাঁর বংশধররা শায়িত এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার (ASI) হাতে।
মুর্শিদাবাদ দেখতে এবং এর ইতিহাস উপলব্ধি করতে হলে ন্যূনতম পক্ষে দু’দিন সময় লাগার কথা। আমি আমার ভ্রমণ কাহিনী লেখা জন্য ইতিপূর্বে দু’বার এসেছি সে বিষয়ের উল্লেখ আগেই করেছি। তবে গত পাঁচ সাত বছরে মুর্শিদাবাদের রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আমার মনে হয় ঐতিহ্য আর ইতিহাস ধরে রাখতে হলে এএসআইকে (ASI) দায়িত্ব দেয়া উচিত। নিমক হারাম দেউরির প্রধান ফটকটি অবশ্যই সংরক্ষণ করা দরকার।
আমরা আরও এগুলাম। বাঁ দিকে দেবী সিং-এর প্রাসাদ যা অনেকটা হাজারদুয়ারির অনুরূপ তবে আকারে ছোট। এই প্রাসাদটি নাসিপুর রাজবাড়ি নামে পরিচিত। এই প্রাসাদ প্রথমে তৈরি করেছিলেন রাজা দেবী সিং। পরে বর্তমান আদলে পুনঃনির্মাণ করেন তারই বংশধর রাজা কীর্তিচন্দ্র সিং বাহাদুর ১৮৬৫ সালে। দেবী সিং পানিপথ অঞ্চল থেকে এখানে আসেন ব্যবসা করতে। পরে তিনি দেওয়ান রেজা খানের ট্যাক্স কালেক্টর হিসেবে যোগ দেন। পলাশী যুদ্ধের পরপরই দেবী সিং-এর উত্থান ঘটে। ওয়ারেন হেস্টিংস তাকে রাজা উপাধি দিয়ে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। তার ট্যাক্স সংগ্রহ অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছে। সাধারণ মানুষের নিকট দেবী সিং ছিলেন একজন অত্যাচারী লুটেরা। আজও তার বংশধররা কলকাতায় বসবাস করছেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন দেবী সিং-এর কারণে বাংলার বহু ধনাঢ্য কৃষক নিঃস্ব হয়ে যায়। পরে দুর্ভিক্ষের কারণও ছিল দেবী সিং এবং তার উত্তরসূরিদের অত্যাচার।
সময়ের অভাবে দেবী সিং-এর রাজবাড়ি দেখা হয়নি। দেবী সিং-এর প্রাসাদ ছেড়ে আমরা জগৎ শেঠের বাড়ির সামনে থামলাম। আমি আর শাহাবুদ্দিন ছাড়া বাকি সবাই টিকিট কেটে জগৎ শেঠের বাড়ি দেখতে প্রবেশ করলেন। আমি প্রথমবার এই বাড়িটি দেখতে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছিলাম। তাই দ্বিতীয়বার আর যেতে ইচ্ছা হয়নি।
জগৎ শেঠ সম্বন্ধে বেশি বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয় না। জগৎ শেঠের এ বাড়িটি তার আদি বাড়ি নয়। তার আদি বাড়ি ভাগিরথীর তীরে ছিল কিন্তু তা নদী ভাঙনের কারণে বিলীন হয়ে যায়। এখানকার এই বাড়িটি দোতলা তবে- মাটির নিচে একটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে ওখানেই ছিল টাকশাল। জগৎ শেঠ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী এবং অর্থ জোগান দাতা। চড়া সুদে অর্থ বিনিয়োগকারী। ওই সময় জগৎ শেঠ ছিলেন সবচেয়ে বড় ব্যাংকার। জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ এবং মীরজাফর সিরাজকে হটাবার ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা ছিলেন। জগৎ শেঠের বাড়িতে জগৎ শেঠ এবং তার পরবর্তী বংশধরদের ব্যবহৃত বহু বস্তু দর্শনার্থীদের জন্যে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।
প্রায় আধাঘণ্টা পর আমাদের দলটি বের হয়ে এল। এর পরের স্থান হাজারদুয়ারি প্যালেস। আমরা হাজারদুয়ারি প্যালেসে পৌঁছলাম। তখন বেলা প্রায় দশটা। বেশ কড়া রোদ। গরম হয়ে উঠেছিল আবহাওয়া। আমিসহ প্রায় চারজন পেছনে রয়ে গেলাম। কারণ আমরা সবাই আগে হাজারদুয়ারি প্যালেস দেখেছি।
অনেক পাঠক হয়তো ভুল করে মনে করতে পারেন যে হাজারদুয়ারি প্যালেসটির সাথে আলীবর্দী খান অথবা সিরাজউদ্দৌলা সম্পৃক্ত কিন্তু বিষয়টি মোটেও তা নয়। এ প্রাসাদটি তৈরি হয় নওয়াব নাজিম হুমায়ুন খাঁর সময়। নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ১৮২৯ সালে শেষ হয়েছিল প্রায় নয় বছর পর। ভাগীরথীর তীরে এই প্রাসাদ কমপ্লেক্স ‘কিলা নিজামত’ বলেও পরিচিত। এই প্রাসাদে ১০০০ দরজা রয়েছে সে কারণে এর নাম হাজারদুয়ারি। তবে এর মধ্যে ১০০ দরওয়াজা আসল নয়। দেখতে একই রকম দেখা যায়। এই বিশাল তিনতলা প্যালেসে ১১৪টি কক্ষ রয়েছে। এই প্রাসাদ চত্বরটি কয়েক শত একর জায়গা নিয়ে। দৃষ্টিনন্দন সবুজ চত্বর। মাঝখানে টাওয়ার ক্লক বসানো। তার অদূরে শুভ্র রংয়ের একটি ছোট মসজিদ যার নাম মক্কা মসজিদ। মসজিদটির ভিত তৈরি হয়েছিল সিরাজউদ্দৌলার সময়ে পবিত্র নগরী মক্কার মাটির সংমিশ্রণে। পরে মসজিদটির সংস্কার করা হয়। এই মসজিদটিই ভাগীরথীর এপারে একমাত্র স্থাপনা যা সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতি বহন করে। সিরাজের প্রাসাদটি ছিল কাঠের তৈরি যা নদীগর্ভে চলে গিয়েছে বলে কথিত। বাস্তবে পলাশীর পর মীরজাফর সিরাজের কোনো চিহ্নই রাখতে চায়নি। শুধুমাত্র খোসবাগই সিরাজ পরিবারের ইতিহাসকে ধারণ করে আছে। হাজারদুয়ারির অপরপ্রান্তে নিজাম ইমামবাড়া। এটি ভারতের বৃহৎত্তম শিয়া ইমামবাড়া বলে কথিত। এটি মহরমের দশদিন মাত্র খোলা থাকে। হাজারদুয়ারির প্রথমতলায় যেখানে নবাবদের দরবার ছিল সেখানে উঠতে সিঁড়ির দুপাশে দু’টি বৃহদাকারের কামান রয়েছে যেগুলোর নাম বাচ্চা তোপ। বলা হয়ে থাকে যে এগুলোর এমন আওয়াজ হতো যে অন্তঃসত্ত্বা নারীদের সন্তান প্রসব হয়ে যেত। তাই এর নাম রাখা হয়েছিল বাচ্চা তোপ। এই দু’টি কামান পরে মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন নদী পথে। তৃতীয় কামানটি উপরে উঠাবার সময়ে নদীতে পড়ে গিয়েছিল যা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা যে কয়েকজন আগে প্যালেসটি দেখেছি তারা এবার ভিতরে যাইনি। তবে বাইরেও গরমে বসতে পারলাম না। হাঁটতে হাঁটতে গাড়ি পার্কিং পার হয়ে একটি ছাপড়া দোকানে চা খেতে বসলাম। প্রায় একঘণ্টা পরে বাকিরা প্যালেসের ভিতরের জাদুঘরটি দেখে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তানভীর বললেন, সমগ্র প্যালেসে সিরাজের মাত্র একটি পেইন্টিং রয়েছে। আমি বললাম, ইতিহাসের পাতায়ও সিরাজের ওই একটি পেইন্টিং-এরই রিপ্রোডাকসন রয়েছে। তাছাড়া ইংরেজরা সিরাজকে নিয়ে তেমন আলোচনাও করেনি। সিরাজকে ইতিহাসে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ভিলেন হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছে।
মুর্শিদাবাদে সিরাজের তৈরি তেমন কোনো দর্শনীয় স্থাপনা না থাকলেও মুর্শিদকুলি খাঁ এবং আলীবর্দী খাঁর বহু নিদর্শন রয়েছে। কাটরা মসজিদটি ছিল মুর্শিদাবাদের সবচাইতে বড় দুর্গ মসজিদ। ওই মসজিদটির প্রধান প্রবেশ পথের সিঁড়ির নিচে বাংলার দেওয়ান নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ-এর কবর রয়েছে। তথ্যে প্রকাশ যে মুর্শিদকুলি খাঁ তার মৃত্যুর আগে এ রকম জায়গায় তাকে সমাধিস্থ করতে বলেছিলেন যাতে তার জীবনের পাপগুলো মুসল্লিদের নিচে থাকার কারণে কম হয়।
আমরা দুপুর সাড়ে এগারোটার দিকে মালদা-এর পথে মুর্শিদাবাদ ছাড়লাম। ভগবানগোলা পার হয়ে ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠবো। ভগবানগোলার পরেই মালদা জেলা শুরু। এ পথেই পার হতে হবে ফারাক্কা বাঁধ। রাস্তায় কোনো জায়গায় দুপুরের খাবার খেতে হবে। আমাদের যাবার পথে কাটরা মসজিদ পরলেও কেউই নেমে দেখতে চাইলেন না। সবারই উদ্দেশ্য সন্ধ্যার আগে মালদায় পৌঁছা।
মুর্শিদাবাদ হতে ভগবানগোলা মাত্র ১৮ কিলোমিটার। জায়গাটি মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ সাব-ডিভিশনে। এক সময়ের ছোট নদীবন্দর এখন অবশ্যই বেশ বড় হয়েছে। আঁকাবাকা রাস্তা। দু’পাশে বড় গ্রাম দেখা না গেলেও রাস্তার দু’ধারে জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট চায়ের আর মুদি দোকান। এক সময় ভগবান গোলা ভাগীরথীর তীরে নদীবন্দর ছিল। ভগবান গোলার কিছু উত্তর হতেই ভাগীরথী আর পদ্মা নদী দু’ভাগ হয়ে যায়। আমরা ভগবান গোলায় পৌঁছলাম। ছোটখাট বাজার এবং বড় ধরনের গ্রাম। এখানকার জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ ভাগ মুসলমান জনগোষ্ঠী। ১৯৪৭ সালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ খুলনা ভারতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। এর অন্যতম কারণ সে ক্ষেত্রে পদ্মা এবং ভাগীরথীর মিলনস্থল তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে থাকত। সে ক্ষেত্রে আজকের ফরাক্কা পশ্চিম বঙ্গের বাইরে রাজশাহী ডিভিশনে থাকত। ভগবানগোলা পার হতে কিছুটা সময় লাগল কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা রাস্তার পাশে ভিড় জমিয়েছে। অজস্র মোটর সাইকেল মোতায়েন ছিল। আজ এ অঞ্চলের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিল শুরু হয়েছে কাজেই সমর্থকদের ভিড়। এ দৃশ্য প্রায় আমাদের দেশের মতোই তবে প্রধান সড়কে যান চলাচল ধীরগতিতে হলেও থেমে নেই। ভগবানগোলা পার হলেই হাইওয়ে। সময় প্রায় একটা। দুপুরের খাবার সময় হয়ে গিয়েছে। হয়তো হাইওয়েতে কোনো ধাবা বা খাবার জায়গা পাওয়া যাবে। আরও প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে হাইওয়ে। ভগবানগোলা ছোট গ্রাম শহর হলেও ১৭৫৭ সালের জুন মাসের শেষের দিকে ছোট একটি গ্রাম ছিল নদীর পাড়ে। সিরাজ তার পরিবার নিয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্যে খাবারের খোঁজে এখানে তীরে নেমেছিলেন। এখানেই এক ফকিরের আস্তানা ছিল। ফকির দানা শাহ যাকে সিরাজ কান এবং নাকের মাথা কর্তন করে মুর্শিদাবাদ ছাড়া করেছিলেন। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে থাকা দানা শাহ সিরাজের জুতা দেখে চিনতে পেরে তাকে আটকে মীরজাফর পুত্র মীরনকে খবর দিলে তাকে গ্রেফতার করে। নিয়ে আসা হয় মুর্শিদাবাদে। ২রা জুলাই ১৭৫৭ সালে মীরনের হুকুমে সিরাজকে হত্যা করে মোহাম্মদী বেগ যাকে আলীবর্দী খাঁ রাস্তা হতে নিয়ে এসে পেলেছিলেন। মোহাম্মদী বেগ আর দানা শাহ বেশিদিন বেঁচে থাকেনি। তাদেরকেও হত্যা করা হয় এবং সমাধিস্থ করা হয় খোশবাগে সিরাজের কবরে যাবার রাস্তার ধারে।
ভগবানগোলা পার হয়ে আমরা আরেকটি স্টেট হাইওয়েতে উঠে লালগোলা পার হলাম। তখনও আমরা ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠিনি। আশপাশে তেমন খাবারের জায়গাও চোখে পরলো না। লালগোলা সীমান্ত শহরের অপর পারেই রাজশাহী ডিভিশন। এরপরে রঘুনাথগঞ্জ। এখানে ফারাক্কার একটি ফিডার ক্যানেলের উপর দিয়ে সুজনিপাড়া যাবার পথে ফারাক্কার প্রধান ফিডার ক্যানালটি পার হলাম। এই ফিডার (ক্যানাল) দিয়েই অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত ভাগীরথীতে যা কলকাতার আদিগঙ্গায় পৌঁছে। অবশেষে বল্লাপাড়ায় নির্মাণাধীন ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠলাম। একপাশে পদ্মা নদী যার মাঝখানে নতুন তৈরি করা আমবাগান। অপরদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে ফারাক্কার প্রধান ফিডার ক্যানাল। এখান থেকেই ফারাক্কার এলাকা শুরু। বাঁধটি এখনও প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে। সময় প্রায় তিনটা। পুরে পথে কোথাও খাবারের জায়গা চোখে পড়ল না। কিছূদূর এগুতেই রাস্তার পূর্ব পাশে একটু নিচু জায়গায় একটি দোতলা হোটেলের মতো মনে হলো। মনে হলো নিচ তলায় রেস্তোরাঁ। আশপাশে আর কোনো স্থাপনা নেই। দালানের সামনে দুটো গাড়ি দাঁড়ানো।
এ জায়গায় হাইওয়ে বেশ উঁচু। দু’পাশে নিচু কৃষি জমি। এ সময় শুধু কালাই-ই রয়েছে ক্ষেতে। আমরা কথিত হোটেলের সামনে এসে নামলাম। জনমানবের তেমন রা নেই। উপরে হোটেলের নাম ‘স্বপ্না হোটেল অ্যান্ড রেস্তোরাঁ’। শমসের খবর নিয়ে বললেন এখানে ভাত ডাল পাওয়া যাবে। খবর নিয়ে জানলাম খাবার প্রায় শেষ শুনেই মনে হলো খিদে আরও বাড়ল। বাইরে মুখ হাত ধুয়ে নিচের তলায় প্রবেশ করলাম। ভাত বেগুনভাজি আর ডাল রয়েছে। বাকি রয়েছে কয়েক টুকরা পার্শে মাছ। বাঙালি মালিকানায় হোটেলটি। উপর নিচ মিলিয়ে গোটা আটটি কক্ষ আর রেস্তোরাঁ। হোটেলে তেমন বোর্ডার আছে বলে মনে হলো না। সাকুল্যে দুজন মানুষ আর উপরে রান্নাঘরে হয়তো একজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই যা বাকি ছিল পরিবেশিত হলো। পেটে খিদে থাকলে সব খাদ্যই সুস্বাদু মনে হয়। খেলাম সবাই মিলে। বিল চুকিয়ে আমরা আবার উত্তরমুখী ফারাক্কার পথে। এসব হোটেল সস্তা বিশেষ করে ট্রাক ড্রাইভারদের থাকার জায়গা। রাস্তা ব্যস্ত হয়ে উঠল মালবাহী ট্রাকে। যাত্রীবাহী বাসের তেমন দেখা পেলাম না।
আমরা উত্তরমুখী ফারাক্কা হয়ে মালদার দিকে। আমাদের পূর্বে পদ্মা নদীর তীরের রাজশাহী আর পূর্বদিকে ফারাক্কার ফিডার ক্যানাল। মাঝখানে বিস্তীর্ণ কৃষি জমি। বিস্তৃীণ কৃষি জমির দিকে তাকিয়ে মনে করছিলাম মুর্শিদাবাদের কথা। বাংলার শেষ কথিত স্বাধীন রাজধানী- বাংলা বিহার আর ওড়িশ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। আর এখন চলছি কিছু সময়ের জন্যে স্বাধীন বাংলার প্রথম রাজধানী বলে পরিচিত গৌড়ের পথে। এই প্রোগ্রাম করবার পূর্বে কোনোদিন ভাবিনি যে একদার বাংলার রাজধানী গৌড় দেখতে যাব। আমরা গৌড়ের পথে। সামনে ফারাক্কার বাঁধ দিয়ে পদ্মা নদী পার হবার বিষয়ে বিশেষ সতর্কবাণী বিভিন্নস্থানে দৃশ্যমান রাখা হয়েছে।
হাইওয়েটি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হলে চার লেন এবং দু’পাশে সার্ভিস লেনও থাকবে। এ প্রকল্প কবে শেষ হবে তার সঠিক ধারণা পাওয়া যায়নি। এ রাস্তার জমি বরাদ্দ নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। জমি বরাদ্দ করতে দেরি হওয়াতে প্রকল্পটি ধীর গতিতে চলছে।
হাইওয়েটি এ জায়গাটায় বেশ উঁচু কারণ নদীর ধার হওয়াতে জায়গাটি এমনিতেই বেশ নিচু। এই মহাসড়কটিই উত্তরবঙ্গ হয়ে উত্তর পশ্চিমে পণ্য বহনের সহজ পথ। প্রতিদিন হাজার হাজার ট্রাক এ রাস্তা ব্যবহার করে। বিশেষ করে দূরপাল্লার ট্রাকগুলো রাতে যাতায়াত করে বেশি। বিকেল হতেই ট্রাকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। দিনের বেশিরভাগ সময় রাস্তার ধারে ট্রাকের বড় লাইন দেখা যায়। সময়টি বিশ্রাম নেয়ার। ভারতের ট্রাকের ড্রাইভার কেবিনগুলোতে শোয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণত দূরপাল্লার ট্রাকগুলোতে ড্রাইভার এবং সহকারি খাবার তৈরি করার জন্যে প্রয়োজনীয় তৈজশপত্র এবং কিছু বাজার করে রাখে। বেশিরভাগ ড্রাইভারের সহকারি পাচকের কাজ করে থাকে। এখানেও এমন ট্রাকের লাইন রয়েছে। ফারাক্কার দিকে যতই এগুচ্ছি ততই রাস্তায় ট্রাকের সংখ্যা বাড়ছে। প্রাইভেট গাড়ি এবং বাস রাস্তায় তেমন চোখে পড়েনি। ট্রেনই যাত্রীদের প্রধান বাহন।
২
আমরা মালদা হয়ে গৌড়ের পথে ফারাক্কার টোল প্লাজায়। গাড়ির বেশ বড় লাইন। বেশি সময় লাগল না টোল দিয়ে পার হতে। প্রায় এক কিলোমিটার পার হওয়ার পর ফারাক্কা দৃশ্যমান হলো। তেমন কোনো চেকপোস্ট নেই। গাড়ি আস্তে আস্তে চলছে কারণ সামনে বেশ কিছু ট্রাক। বাঁধের দক্ষিণ হতে উত্তরদিকে যাচ্ছি। পূর্বদিকে একটি রিজার্ভ পুলিশ আউট পোস্ট। কোনো সেন্ট্রিকেও ডিউটিরত দেখলাম না। মনে হলো নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ইলেকট্রনিক পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই রয়েছে। কারণ ফারাক্কা তৈরি নিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিরোধ ছিল। বিরোধ ছিল শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে পর্যাপ্ত পানির প্রবাহ নিয়ে। ফারাক্কা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বড় বিষয় হয়েছিল। পরে ১৯৬৬ সালে একচুক্তিতে পানি বণ্টনের পরিমাণ নির্ধারিত হলেও এখনও অভিযোগ রয়েছে যে সে পরিমাণ পানি পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের প্রায় সবার কাছেই ফারাক্কা দেখার অভিজ্ঞতা নতুন। আস্তে আস্তে বাঁধের উপর উঠলাম। পশ্চিম দিকে ফিডার ক্যানাল। পূর্বদিকে দৃশ্যমান হলো পদ্মা যা এখান হতেই বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশ করেছে। কিছুদূরে ভাগীরথীর মুখ যার সাথে ফিডার ক্যানাল যুক্ত।
ফারাক্কা মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর প্রান্তে বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার সীমান্ত হতে প্রায় ১৭ কিঃ মিঃ দূরে। গ্রামটি বা ছোট শহরটি একটি কমিউনিটি যেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে যাচ্ছে ব্লক সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে। ফারাক্কার অপর পার মালদা জেলা। মাঝখানে পদ্মা নদী। যেমনটা আগেই বলেছি ফারাক্কা ব্যারাজ তৈরি শুরু হয় ১৯৬১ সালে এবং শেষ হয় ১৯৭৫ সালে। এর দৈর্ঘ্য ২.২৪ কি. মি. এবং ফিডার ক্যানালটি ৪০ কি. মি. যার প্রবাহিত পানি ভাগীরথী এবং পরে কলকাতার হুগলী নদীর এবং হলদিয়া বন্দরের নাব্যতা রক্ষা করে।
আমরা ধীরে ধীরে বহুল আলোচিত ফারাক্কা বাঁধের উপরদিয়ে ধীর গতিতে যাচ্ছি। পশ্চিম দিকে রেলওয়ে লাইন। পূর্বদিকে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্যে পিলার। বাঁধের পশ্চিমপ্রান্তে অর্থাৎ নদীর পানি যেদিক হতে প্রবাহিত হচ্ছে সেদিকে ১০৮টি গেট এবং আরেকটি মালদা প্রান্তের নিম্ন অঞ্চলে। মোট ১০৯টি গেট। মুর্শিদাবাদ প্রান্তে ফারাক্কা সুপার থরমাল পাওয়ার স্টেশন। এটি কয়লাচালিত পাওয়ার প্লান্ট। প্রায় ২১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম এই পাওয়ার প্লান্ট।
আমরা ফারাক্কা পার হচ্ছি। মনে পরে স্কুলের ছাত্র হিসেবে এই ফারাক্কা নিয়ে বিবাদের কথা শুনেছি, পত্রিকায় পড়েছি। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে তৈরি শেষ হবার পর পানির ভাগাভাগি নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেকখানি শীতল হয়েছিল। এরপর এই বিষয়টি বাংলাদেশ জাতিসংঘেও তুলেছিল। অবশেষে ১৯৯৬ সালে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল তবে সিন্ধু নদের পানির ভাগাভাগি চুক্তির মতো এই চুক্তিতে কোনো আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি নেই।
দেখলাম ফারাক্কার বাঁধের মাত্র দু’টি গেট খোলা যেখান দিয়ে কিছু পানি পদ্মা নদীতে প্রবাহিত হচ্ছে। পূর্বপাশের নদীটি যা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, পানি খুবই কম। নদীতে দু-একটি ছোট পালের নৌকা দেখলাম যা সচরাচর আমাদের দিকের পদ্মায় দেখা যায় না। খুব একটা মাছ আছে বলে মনে হয় না এবং থাকার কথাও নয়। এক সময় বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশের কত গল্প শুনেছি। এখন আর পদ্মায় ইলিশ নেই বললেই চলে অথচ পদ্মার ইলিশ নামে বাজার গরম হয়ে উঠে। এক সময়ের সবচাইতে সস্তা মাছের অন্যতম ইলিশ এখন সবচাইতে দামি মাছের একটি।
বৈশাখে বাংলাদেশের নতুন ফ্যাশন উচ্চ মধ্যবিত্তদের একদিনের বাঙালি হয়ে উঠা শানকিতে পান্তাভাত আর ইলিশ ভাজা খাওয়া। এক প্লেট পান্তা-ইলিশের দাম কয়েক হাজার টাকাও হতে পারে। পয়লা বৈশাখের আগে ইলিশ মাছের বাজার আগুন হয়ে উঠে। আমার শৈশবে এই ইলিশ মাছের হালি চার হতে ছয় আনায় বিক্রি হতে দেখেছি। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ইলিশ মাছ ফেলে দিতে দেখেছি কারণ ইলিশ মাছে পচন ধরে খুব তাড়াতাড়ি। আর এই পচা ইলিশ ওই সময় ওলাউঠা বা কলেরার অন্যতম উপসর্গ হতো। এখনতো সেই অবস্থা নেই। বাজারের ইলিশ ন্যূনতম পক্ষে একবছর পুরাতনতো হবেই। এখন তো পচনের সময়ই নেই। ইলিশ ধরার আধাঘণ্টার মধ্যে বরফে ঢুকে পরে ফ্রিজার ট্রলারে ঢাকায় আসে অথবা বড় আড়ৎদারের কোল্ড স্টোরে চলে যায়। আসল ইলিশের স্বাদতো পাওয়াই যায় না। আর ফরমালিন সে প্রসঙ্গ না আনাই ভালো।
ফারাক্কা বাঁধের উপরের রাস্তাটির অবস্থা তেমন সুবিধার নয়। বেশ এবারোখেবরো অনেকদিন সংস্কার হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রচুর ভিড় মালবাহী ট্রাক চলাচল করার কারণে খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা খারাপ হয়। পশ্চিমপাশের অংশের নদীতে পানি ধরে রাখার কারণে পানি ভরপুর। ফিডার ক্যানালের মুখে বেশ কয়েকটি স্লুইস গেট যার মাধ্যমে ভাগীরথী আর হুগলীর পানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে পশ্চিমের নদীর অংশটিই গঙ্গা নামে পরিচিত যা আমাদের দেশে প্রবেশের পর পদ্মা নাম ধারণ করে।
আমরা ফারাক্কা পার হলাম। সূর্য পশ্চিম দিকে নামতে শুরু করেছে। ক্রমেই রাস্তায় ট্রাকের ভিড় বাড়তে শুরু হয়েছে। যে সব ট্রাক এ পাড়ে সারা দিন অপেক্ষা করছিল সেগুলো পুণরায় যাত্রা শুরু করাতে ক্রমেই হাইওয়েতে যানজট শুরু হয়েছে। আমরা এখন আমের জন্যে বিখ্যাত মালদা জেলায় প্রবেশ করেছি। পশ্চিম পাশে সরকারি কলোনি জায়গাটির নাম জগন্নাথপুর। আধাঘণ্টা পর মালদা অঞ্চলের সবচাইতে বড় বিএসএফ ছাউনি চোখে পড়লো। এটাই রাজশাহী অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত বিএসএফ ব্যাটালিয়ন।
আমরা যখন মালদা শহরের কাছাকাছি জায়গায় জাদুপুরের কাছাকাছি সেখান থেকেই শুরু হলো ভয়াবহ যানজট। মালদা শহরের মুখে প্রবেশ করতে করতে প্রায় সাতটা বেজে গেছে। তখনও আমরা হোটেলের ধারে-কাছে নেই। মালদা বাইপাস তৈরি শেষ না হওয়ার জন্য শহরের মধ্য দিয়ে উত্তরাঞ্চলে যাবার সমস্ত ট্রাক যাতায়াত করে ফলে শহরে বিকেল হতেই ভয়াবহ যানজট শুরু হয়। শহরের বাস, ট্রাক এবং ইজি বাইক রিকশা সবই চলে একই রাস্তায়। শহরের যতটুকু এ পর্যন্ত দেখলাম তাতে খুব একটা আনন্দিত হতে পারলাম না। ঘনবসতির শহর মনে হলো। দোকান-পাট বাড়ি-ঘরগুলোর চেহারা যে খুব উজ্জ্বল তেমন মনে হয়নি। শহরটি পরিষ্কার তেমন বলাও যায় না। অপর পাড়ে রাজশাহী শহরের তুলনায় শহরটি ময়লা এবং ঘিঞ্জি। মালদাতে আমরা আজ এবং কাল দু’রাত থাকব। আমাদের জন্যে জয়ন্তর মাধ্যমে প্রধান সড়কের উপরে কলিঙ্গ নামক হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জয়ন্ত বললেন হোটেলটি দুই তারকা। দুই তারকা আর তিন তারকা এ ধরনের শহরে তারকা হোটেল থাকার কথা নয়। শীতের সময় অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের আনাগোনা বেশি। তবে মাঝে-মধ্যে বিদেশী পর্যটকদেরও দেখা যায়।
আমরা বহু কষ্টে রথখোলা মোড় নামক জায়গায় পৌঁছলাম। এখান থেকে দুটো রাস্তা দু’দিকে গিয়েছে। জয়ন্তও এখানে আগে তেমন আসেনি। হোটেলে ফোন করলে পথনির্দেশনা দিল। জানালো যে সুকান্ত মোড় পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, সেখান হতে ইউটার্ন নিয়ে অপর পাশে এলেই কলিঙ্গ হোটেল পাওয়া যাবে। তার পাশেই চানক্য হোটেল। আর দুই কিলোমিটার যেতে হবে। এতক্ষণে মনে হচ্ছিল যে এ রাস্তা বোধ হয় শেষ হওয়ার নয়। ন্যূনতম পক্ষে আরও একঘণ্টা গাড়িতে থাকতে হবে। দুপুরের পরে আর কোথাও আমরা যাত্রা বিরতি করিনি বা করার জায়গাও পাওয়া যায়নি।
মালদা শহরের জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। দু’টি পৌরসভা সদর এবং ইংলিশ বাজার। ইংলিশ বাজারই পুরনো শহর এবং এখানেই জেলা সদর অবস্থিত। এগারোটি পুলিশ স্টেশনে বিভক্ত শহর। এখানে অন্যান্য বিদ্যাপীঠসহ একটি মেডিকেল কলেজ আছে।
মহানন্দা আর কালিঙ্গি নদীদ্বারা বিধৌত মালদা শহর। মালদা পুরনো জনপদ। এক সময় বাংলার দু’টি রাজধানী ছিল এই অঞ্চলে। এর একটি গৌড় অপরটি পান্ডুয়া। এই দুটো জায়গা কে কেন্দ্র করেই উনিশ শতকের দিকে মালদা আধুনিক শহর গড়ে উঠেছে। এই জেলা আমের জন্যে বিখ্যাত বিশেষ করে মালদার ফজলি আম ভারতবর্ষ জুড়েই বিখ্যাত।
প্রকৃতপক্ষে জেলা শহরটি চলতি ভাষায় মালদা বলে পরিচিত হলে জেলার সদর ইংলিশ বাজারে। এটা ডিভিশন সদরও বটে। এ জেলাটি সংগঠিত হয় পুরনিয়া দিনাজপুর, রাজশাহী অঞ্চল নিয়ে ১৮১৩ সালে। ১৮৩২ সালে আলাদা ট্রেজারি এবং ১৮৫৯ সালে আলাদা ম্যাজিট্রেসি গঠিত হয়। ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত মালদা রাজশাহী ডিভিশনের অন্তর্গত ছিল। পরে ১৮৭৬ সালের পর হতে ১৯০৫ পর্যন্ত ভাগলপুর ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এরপর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পুনরায় রাজশাহী ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আগস্ট ১৯৪৭ এই জেলার অবস্থান অনিশ্চিত ছিল। আগস্ট ১২ হতে ১৫ পর্যন্ত এই জেলার অবস্থান ছিল অনিশ্চিত কারণ স্যার রেডক্লিফের ঘোষণায় এ জেলার অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। এ কয়দিন জেলাটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একজন ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ছিল। অবশেষে ১৭ আগস্ট ১৯৪৭ সালে মালদা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়।
মালদা মেট্রোপলিটন শহর ৮১ বর্গ কিঃ মিঃ বিস্তৃত। ২০১১ সালের শুমারি মোতাবেক শহরের জনসংখ্যা ছিল তিন লাখ পঁচিশ হাজার। জনসংখ্যার এক হাজারের মধ্যে নারীদের সংখ্যা ৮৭৭ জন। শিক্ষার হার শতকরা ৮৫ ভাগ।
সময় প্রায় ৮টা আমরা এখনও হোটেলে পৌঁছিনি যদিও হোটেলটি দৃষ্টি সীমার মধ্যেই। এতক্ষণ যানজটের মধ্যে থেকে শমসের আর বসে থাকতে পারলো না। শমসের আর জয়ন্ত নেমে গিয়ে হেঁটেই হোটেলে পৌঁছল। আমরা আর আধাঘণ্টা পর সুকান্ত চত্বর হতে ইউটার্ন নিয়ে যখন হোটেলের সামনে পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। পশ্চিমপাশের রাস্তায় ভয়াবহ যানজট। হোটেলে কক্ষে পৌঁছে খাবার রেস্তোরাঁতে যেতে যেতে প্রায় সাড়ে নয়টা। আমি আর তানভীর এক রুমেই ছিলাম দুই রাত। রাতের খাবারের অর্ডার আগেই দেয়া হয়েছিল যা জয়ন্ত কলকাতা থেকেই ব্যবস্থা করেছিল। ডাইনিং রুমেই সকালের প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করা হলো। আমাদের সবার জন্যেই গৌড় দেখার প্রথম অভিজ্ঞতা হবে। কেউই-এর আগে গৌড়-এর সাথে তেমন পরিচিতও ছিলাম না। ড্রাইভার সমেত কেউই গৌড়ের রাস্তাও চেনার কথা নয়। কাজেই জায়গায়-জায়গায় জিজ্ঞাসা করে যেতে হবে।
পরদিন সকাল নয়টার মধ্যে নাস্তা শেষ করে আমরা গাড়ি নিয়ে বের হবার আগে রিসিপশনে গৌড় যাবার মোটামুটি রাস্তার ধারণা নিয়ে বের হয়েছিলাম। তবে যা আমরা করতে পারিনি; উচিত ছিল একজন অভিজ্ঞ গাইড নেয়া। যদিও গাইড পাওয়া যেতো কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। হয়তো গৌড় গিয়ে পেতে পারি।
আমরা সকাল নয়টার দিকেই রওয়ানা হলাম। দক্ষিণমুখো হতে হলো। তার মানে গতকাল আমরা গৌড় দক্ষিণে রেখে উত্তরে হোটেলে এসেছিলাম। এখান হতে প্রায় এক ঘণ্টার রাস্তা। আমরা শহরের বাইরে এসে মুসস্থানী মোড় ছেড়ে দক্ষিণ পূর্বদিকের দুমুখো রাস্তা ধরলাম। দু’পাশে ধানের ক্ষেত আর ছোট ছোট আম বাগান। রাস্তার একধারে প্রায় ১ কিলোমিটার লম্বা ট্রাকের লাইন। এগুলো চাঁপাই নবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ বন্দরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। সোজা গেলেই ছোট সোনা মসজিদ আর বাংলাদেশের সীমান্ত। ওই সীমান্ত চৌকিতেও রয়েছে গৌড়ের আরেকটি গেট বা আলাই দরওয়াজা যার ঐতিহাসিক নাম কোতোয়ালী দরওয়াজা। রয়েছে ছোট সোনা মসজিদ এবং মোগল রাজপুত্র আওরঙ্গজেবের ভাই এবং বাংলার সুবেদার শাহ সুজার তোষাখানা। এই পুরো অঞ্চলটিই ছিল এক সময়কার লক্ষণাবতী ও পরে গৌড়। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আগ পর্যন্ত গৌড় গড়ে উঠেছিল বাংলার রাজধানী হিসেবে। কখনও তথাকথিত স্বাধীন এবং বেশি সময়ই দিল্লির শাসকদের অধীন। সে অর্থে বাংলা কখনও স্বাধীন ছিল কিনা তা নিয়ে ইতিহাসে বিতর্ক রয়েছে।
আমরা ট্রাকগুলো পার হয়ে যাওয়ার সময় দিক-নির্দেশনা নিলাম। এবার পশ্চিমদিকের রাস্তা ধরলাম। সরু রাস্তা। এ ধারে জনবসতি কম। বাড়িঘরগুলোর যে চেহারা ফুটে উঠেছে তাতে মনে হয় এলাকাটি বেশ গরিব। মাঠে-ঘাটে কৃষিকাজ এবং আম বাগানে কাজ করাই প্রধান উপার্জনের উৎস। রামকেলী নামক গ্রামের পাড়ে একজনকে পেয়ে নাসরুল্লা গৌড় নামক জায়গার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক এমনভাবে তাকালেন যেন এই নাম জীবনেও শুনেননি। সামনে দেখিয়ে বললেন যে সামনে বাদল্ল্যাবাড়ীর কাছে বেশ পুরনো জায়গা রয়েছে। আমরা আরও কিছুদূর এগুলাম। আমার মনে হলো যে আমরা সঠিক জায়গা যাচ্ছি। আরেকটু এগুতেই একটি পুকুর এবং দু’একটি বাড়ি পার হতেই একটি বড় ঘেরাও দেয়া বহু পুরনো স্থাপনা পেলাম। এখানে আমরা থামিনি কারণ সামনেই গৌড়ের বিখ্যাত প্রবেশপথের আলাই দরওয়াজা বা তোড়ন।
আমি ভেবেছিলাম গৌড়ের এই বিস্তীর্ণ এলাকা দেখার জন্যে এবং দেখাবার জন্যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার (এএসআই) কোনো অফিস থাকবে। সেখানে হয়তো কোনো গাইড ম্যাপ পাওয়া যাবে। তেমন মনে হলো না বা পেলামও না। আমরা আলাই দরওয়াজা দেখে প্রথমে সেখানেই নামলাম। জায়গাটি পরিপাটি করে রাখা। গেটটি দেয়াল বেষ্টিত গৌড়ের প্রধান ফটক। এক সময় সমগ্র শহরটি দেয়াল ঘেরা ছিল। এখনও সে দেয়ালের বহু অংশ দৃশ্যমান।
আমরা নেমে পড়লাম। গেটটি খুলে বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করলাম। এই প্রথম গৌড়ের একটি স্থাপনার সামনে দাঁড়ালাম। ঐতিহাসিক এই রাজধানী শহরটি দৈর্ঘ্যে ৭-৮ কি. মি. এবং প্রস্থে ২ কি. মি. ছিল বলে তথ্যে প্রকাশ। স্থাপিত হয়েছিল অষ্টম শতাব্দিতে এবং ষোড়শ শতাব্দিতে শহরটি রাজধানীর মর্যাদা হারায়। গৌড়ের আদি নাম ছিল লক্ষণাবতী। মনে করা হয় লক্ষণ সেনের নামে এর নামকরণ। লক্ষণ সেন ছিলেন সেন রাজবংশের। যাদের পূর্ব পুরুষরা এসেছিলেন দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকা অঞ্চল থেকে। এই রাজবংশের গোড়াপত্তন করেছিলেন সামন্ত সেন পরে এদেরই রাজবংশের বল্লাল সেন গৌড় দখল করেন। সেন বংশ শুধু বাংলাতেই নয় ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণের বহু অঞ্চলজুড়ে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। লক্ষণ সেন বল্লাল সেনের উত্তরসূরি হিসেবে প্রায় ২০ বছর বাংলা স্থানান্তর করেছিলেন। লক্ষণ সেন শুধু বাংলা নয় বিহার-আসাম এবং ওড়িশ্যা পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। লক্ষণ সেনের রাজগুরু উপদেশ দেয়াতে লক্ষণ সেন দিল্লির আক্রমণ ঠেকাতে রাজধানী নবদ্বীপ-এ নিয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে দিল্লির তুর্কি বংশোদ্ভূত জেনারেল ১২০৪ সালে লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলাকে দিল্লির সুলতানদের অধীনে নিয়ে আসেন।
আমরা দাখিল বা সালামী দরওয়াজা বলে পরিচিত গৌড়ের এককালের প্রধান গেটের চত্বরে প্রবেশ করলাম। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, এর নাম ছিল নীম দরওয়াজা। কিন্তু এএসআই-এর ফলকে লেখা সালামি দরওয়াজা। অনেকটা মোগলদের দরজা বা গেটগুলোর মতোই এর গড়ন। স্থানীয় নকশার সঙ্গে সংমিশ্রণ হয়েছে মধ্য এশিয়া এবং তুর্কি স্থাপত্যের। সমগ্র মধ্যযুগে এবং মোগলদের স্থাপনায় প্রায় একই ধরনের স্থাপত্য দেখা যায়। দাখিল দরওয়াজা তৈরি হয়েছিল ১৪৫৯-৭৪ সালে বাংলার সুলতানি আমলে। এর উচ্চতা ২১ মিটার এবং ৩৪.৫ মিটার প্রস্থ। চার ঘোড়া পাশাপাশি প্রবেশের মত বড় দরওয়াজা। দরওয়াজার দু’ধারে কামান বসাবার জায়গা যার দ্বারা আগত শাহী অতিথিদের স্বাগত জানানো হতো। দরওয়াজার দু’ধারে রক্ষার জন্য সৈনিকদের বাসস্থান ছিল। এই দরওয়াজাটি বানিয়েছিলেন সুলতান বারবাক শাহ।
দাখিল দরওয়াজার ভিতরে প্রবেশ করতেই দু’জন স্থানীয় লোককে বসা দেখলাম। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম তারা এখানে কি করছেন। বললেন যে তারা এএসআইর কর্মচারী। এ জায়গার রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত। যেহেতু এখানকার সব স্থাপনাগুলো ঐতিহাসিক সংরক্ষিত স্থান তাই তাদের নিয়োগ। জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কোনো তথ্য কেন্দ্র রয়েছে কিনা? তারা বললেন নেই। তবে এ রাস্তা ধরে এগুলেই সব দর্শনীয় স্থানগুলো পাওয়া যাবে। এবং রাস্তার উপরেই প্রত্যেকটি স্থানের দিক-নির্দেশনা দেয়া রয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছি যে জায়গাটি আমরা ছেড়ে এসেছি সেটা কোন স্থাপনা। একজন বললেন, বাবু ওটা বড় সোনা মসজিদ নামে পরিচিত। আর একটু সামনে গেলেই পাবেন ‘ফিরোজ’ মিনার। ওখান হতে বাকি সব জায়গার দিক-নির্দেশনা দেয়া রয়েছে।
দাখিল দরওয়াজা তো রীতিমত অট্টালিকা। এর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত ন্যূনতম পক্ষে ২৫ গজ হবে। অপর পাশে সবুজ চত্বরের অপরপ্রান্তে আম বাগান। এখনও আম বড় হয়নি। অনেক গাছে মুকুল হতে আম বের হচ্ছে মাত্র। এগুলো সবই ফজলি আম। দর্শনার্থী আসুক বা নাই আসুক নির্ধারিত ব্যক্তিদের জায়গা পরিস্কার রাখার ব্যাপারে কোনো গাফিলতি দেখিনি। আমি তাদের একজনকে আমাদের পথ নির্দেশক হিসেবে নিতে চাইলাম কিন্তু রাজি হলো না। কারণ তাদের কর্মস্থল ছাড়া নিষেধ। সুপারভাইজার জানলে তাদের চাকরি থাকবে না। জিজ্ঞাসা করলাম কখন এখানে বেশি লোক আসে? জানালেন যে শীত মৌসুমে বহু লোক এসব জায়গা দেখতে আসে এবং অনেক পিকনিক পার্টিও এখানে আসে।
আমরা বেশ কিছুক্ষণ অনেকগুলো ছবি উঠিয়ে রাস্তার ধরে দক্ষিণ পূর্বমুখে রওয়ানা হলাম। আমরা এখন গৌড়ের ভিতরে। তবে এ অঞ্চলের নাম এখন আর গৌড় নেই।
গৌড় রাজধানী না হলেও সেন বংশের পূর্বে এ অঞ্চল পাল বংশের রাজত্বের অংশ ছিল। যদিও পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায় না তবে ভাপাইদা নামক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র যোদ্ধার পুত্র গোপালকে এ অঞ্চলের রাজা নির্বাচন করা হয়েছিল। সময়কাল ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ, শশাঙ্ক ও শক রাজত্ব শেষ হবার পর।
গোপাল এবং পাল বংশের বাংলা বিহার অঞ্চলের রাজা হওয়া নিয়ে একাধিক কিংবদন্তি রয়েছে। শশাঙ্কের রাজত্ব শেষ হওয়ার পর বাংলা অঞ্চল এক অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল। কিংবদন্তি আছে এ অঞ্চলে রাজা হলেই নাগরানীর মোহে পড়ে মৃত্যুবরণ করতো। অবশেষে গোপালকে নির্বাচন করা হয়। গোপাল নাগরানীকে বধ করে রাজত্ব কায়েম করেন। ওই সময়ে গৌড়সহ এ রাজত্বের পরিধি যথেষ্ট বড় ছিল। তবে গোপালকে নির্বাচিত করা হয়েছিল ওই সময়কার জমিদার এবং প্রভাবশালীদের দ্বারা। পালদের শাসনকাল বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্যে ছিল। পাল বংশের পতনের মধ্যে দিয়ে সেন বংশের অভ্যুদয় হয়।
আমরা পাকা রাস্তা ধরে প্রায় অন্ধের মতো দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলাম। এখানে খুব বেশি মানুষের বাস তেমন মনে হয়নি। কারণ তেমন বড় গ্রাম বা জনসংখ্যা চোখে পড়েনি। রাস্তাটি দেখে মনে হলো সার্কুলার রাস্তার মতো। বেশ ভাল অবস্থায় রাস্তাটি রয়েছে। এ রাস্তায় হয়তো গাড়ি ঘোড়ার যাতায়াত কম। এ অঞ্চলে বেশ পুরাতন এবং বড় ধরনের পুকুর চোখে পড়ল। আর আম গাছের অভাব নেই। ছোট বড় নতুন পুরাতন আম গাছে ভরপুর। যেতে যেতে জাকারিয়া বললেন, গৌড় পর্যন্ত কোনোদিন আসা হবে ভাবিনি। তাছাড়া এখানে এত দেখার আছে তাও জানতাম না। শুধু শুনেছি মধ্যযুগের বা তারও আগের বাংলার রাজধানী গৌড়। নাসরুল্লা বললেন, এখানে আসার পরিকল্পনার সকল কৃতিত্ব সাখাওয়াত ভাইয়ের আর ব্যবস্থাপনার জন্যে হাবিব ভাইকে যতই ধন্যবাদ দেয়া হোক তা কমই হবে। অন্যরা সবাই এক বাক্যে দুটো বক্তব্য সমর্থন করলেন।
আমরা দাখিলি দরওয়াজা হতে এক কিলোমিটার পার হতেই রাস্তার পশ্চিম পাশে বড় একটি দীঘি দেখলাম। সেখানে বেশ কিছু লোক মাছের পোনা জাল দিয়ে ধরে এলুমিনিয়ামের বড় বড় ডেকচির মধ্যে রাখছে অন্যত্র নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের গাড়ি থামাতেই একজনকে জিজ্ঞাসা করায় বললেন এই তো ঘাটলার অপর পাশেই তো ‘ফিরোজ মিনার’। তাইতো রাস্তার পূর্ব পাশেই গৌড়ের অন্যতম বিখ্যাত দর্শনীয় বস্তু যার নাম ফিরোজ মিনার। আমরা নামলাম। সবুজ সুন্দর পরিপাটি করে রাখা সবুজ ঘাসের চত্বরের মাঝে একটু উঁচু জায়গায় মধ্যযুগীয় ইটের তৈরি মিনার। মিনারে প্রবেশের পথ নিচের তলায়। মিনারটি ২৬ মিটার উচ্চতায়। উপরে গোলকৃতি ছাদ প্রায় পাঁচতলা হতে উঁচু তিন ধাপের পর উপরের দু’টি ধাপ ব্যালেন্স রাখবার জন্যে একে অপর হতে ব্যাসার্ধে ছোট অনেকেই মনে করেন মিনারটি তৈরি করা হয়েছিল ফিরোজ শাহর সুলতান হবার পর ১৪৮৬ সালে। আবার অনেকে মনে করেন এটা তৈরি শুরু করে হামুজ্জা শাহ ১৪১২ সালে। তবে এএসআইর তথ্য মতে এটি তৈরি করেছিলেন একজন আবেসিনিয়ান ব্যবসায়ী সাইফুদ্দিন ফিরোজ যিনি বারবাক শাহকে হত্যা করে ফিরোজ শাহ নাম ধারণ করে বাংলা অঞ্চলের সুলতান হন। এই মিনারে উঠবার জন্যে তেহাত্তরটি সর্পিল ধাপ রয়েছে তবে এখন এখানে উঠা বন্ধ করা হয়েছে। মিনারের এক পাশে বেশ বড় ধরনের প্রাচীন পাকুর গাছ। তার চারিদিকে সবুজ বেষ্টনী।
ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আমাদের সবার বাংলাদেশের সীম কার্ড চালু হয়ে গেল। গ্রামীণ ফোন ব্যবহার করে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশে যোগাযোগ করলাম। আমার ফোনে বিভিন্ন ধরনের প্রায় পঁচিশটি এসএমএস এলো। এ জায়গা চাঁপাই নবাবগঞ্জ সীমান্ত এলাকা হতে পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার দূরে মাত্র। এ জায়গাটির নাম কনকপুর। গৌড় বলে পরিচিত নয়। ফিরোজ মিনার হতে আমরা সোজা রাস্তায় যাবার উদ্যোগ নিলে স্থানীয় একজন বললেন যে আমরা পুকুরের উত্তর পাশ দিয়ে আম বাগানের মধ্যে দিয়ে গেলে বল্লাল প্রাসাদের ভগ্নাংশ দেখতে পারব এবং দেখতে পারব গৌড়ের সুউচ্চ দেয়ালের একাংশ। ওই রাস্তা ধরে আরেকটু সামনে এগুলেই প্রাসাদের এবং মন্দিরের অংশ পাওয়া যাবে আর নদীর পাড়ে পুরনো ঘাটের ভগ্নাংশ দেখতে পাব। বাকি সব এই একই রাস্তায় রয়েছে। আমরা এবার বল্লাল বাড়ি দেখার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আদি ভাগীরথীর তীরের এই বাড়ির ভগ্নাংশ বল্লাল সেনের না সুলতানদের প্রাসাদের ভিত তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। আর ভাগীরথী নদীর এ জায়গার অংশ এখন মৃত। এই নদীটিই ছিল গৌড়ের প্রাণ।
বলছিলাম গৌড় অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই অঞ্চলে বা বাংলার আলাদা সত্ত্বার গোড়াপত্তন করেন রাজা শশাঙ্ক গৌড় রাজত্ব নামে। শশাঙ্কের রাজত্বকাল ধরা হয় ৫৯০ হতে ৬২৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। তার রাজত্বকাল ধরা হয় হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক সময়ে। শশাঙ্কের সাথে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধও হয়েছিল। হর্ষবর্ধন বঙ্গ আক্রমণও করেছিলেন কয়েকবার। শশাঙ্ক বাংলা অঞ্চল স্থাপন করলেও গৌড় হতে অনেক দূরে বর্তমানের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কর্ণ সুর্বণতে রাজধানী স্থাপন করেন। সময়টি বাংলার বৌদ্ধদের রাজত্বকাল ও বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রসারণের সময়। শশাঙ্ককে বাংলা পঞ্জিকার প্রবক্তা বলে মনে করা হয়।
আমরা বেশ উঁচু মধ্যযুগীয় দেয়ালের একাংশের ধারে উপস্থিত হলাম। কয়েকজন লোক এখনও মাটি খোঁড়াখুঁড়িতে লেগে আছে। দেয়ালের পূর্ব পাশে অনেকখানি জায়গাজুড়ে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে। এটাই বল্লাল বাড়ি বা বল্লাল সেনের তৈরি কথিত প্রাসাদের ভিত। সামনে পিছনে আমের বাগান। অনেকগুলো গাছ বেশ পুরনো। একটি গাছের নিচে কয়েকজন দিবানিদ্রায় মগ্ন। দেয়ালের অপর প্রান্তে কিছু পিলারের ভগ্নাংশ রয়েছে। তবে আমাদেরকে একজন বললেন একটু সামনে আম বাগানের ভিতরে নদীর ধারে গেলে আমরা প্রাসাদের ভিত আর নদীর ঘাটটিও দেখতে পারবো। এই ঘাটটি মোগল আমলের অন্যতম কৃতি বলে অনেক ঐতিহাসিকরা মনে করেন। ইতিহাসের তথ্য মোতাবেক মোগল সম্রাট হুমায়ুন এখানে বেশ কিছু সময় কাটান এবং জায়গা বিশেষ করে আম তার অত্যন্ত পছন্দনীয় ফলে পরিণত হয়। তিনি এ জায়গার নাম দিয়েছিলেন ‘জান্নাতাবাদ’। কিন্তু এ নামে গৌড় কোনোদিন পরিচিত হয়নি।
আমরা গাড়িতে চড়ে নদীর ঘাটের দিকে রওয়ানা হবার জন্যে তৈরি হবার পথে একজন স্থানীয় লোক টলতে টলতে হাজির। মনে হলো সকাল হতেই বাংলা টেনে টাল হয়েছেন। এসে বললেন যে তাকে কিছু টাকা দিলে তিনি সব জায়গায় আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি আছেন। তার যে অবস্থা তাতে মনে হলো আরও কিছু টাকা পেলে তার দু’দিনের বাংলা টানার নিশ্চয়তা হবে। আমরা তার কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে রওয়ানা হলাম। নদীরপাড়ে আম বাগানে গাড়ি রেখে হেঁটে নদীর পাড়ে যাবার পথে বল্লাল বাড়ির মূলভিতের একাংশ দেখলাম। খনন কাজ চলছে। শেষ হতে অনেক সময় লাগবে। কাজ বেশ ধীরগতিতে চলছে। পাশেই বেশ বড় আমবাগান। কয়েকজন মিলে আমের গাছে ওষুধ ছড়াচ্ছে। এদের সবাই অবাঙালি। বিহারের শ্রমিক বাগানের মালিক মালদাতে থাকেন। এই বাগানসহ অনেক বাগান লিজ নিয়েছেন।
আমরা এবার পাকা রাস্তা ধরে চললাম কিছু দূর গিয়ে রাস্তার ধারে এক সাইকেল চালককে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে আর কি দেখার আছে। তিনি বললেন এ রাস্তা ধরে এগুলেই সব দর্শনীয় জায়গায় পৌঁছতে পারবো। এগুলো সবই বাংলার সুলতানি আমলের স্থাপনা। আমরা রওয়ানা হলাম তা দেখার উদ্দেশে। প্রায় এক কিলোমিটার পর অনেকগুলো স্থাপনার সামনে এসে দাঁড়ালাম। এখানে রয়েছে আরেকটি গেট। তার পাশে আমবাগানের মধ্যে এক গম্বুজের মসজিদ এবং রাস্তার অপর প্রান্তে আরেকটি মাঝারি ধরনের মসজিদ। সুন্দর পরিপার্টি করে রাখা।
সামনের গেটটির নাম ‘লুকোচুরি দরওয়াজা’। তৈরি হয়েছিল ১৬৫৫ খৃস্টাব্দে। দিল্লিতে তখন মোগল সাম্রাজ্যের মধ্য পড়ন্ত গগনে। তার পাশে বড় একটি চত্বরে ঘেরা দেয়া। রাস্তার অপর পাশে বেশ কিছু দোকান। চা আর বিভিন্ন খাবার আর কোল্ড ড্রিং-এর সমাহার। সামনের মসজিদ কমপ্লেক্সের নাম ‘কদম রসুল মসজিদ’। আমরা কয়েকজন চত্বরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। পাশে দু’টি পুরনো কবর। তার পাশে একটি পাকা স্থাপনার মধ্যে একটি বড় সড় কবর। সামনে একজন মাথায় টুপি পড়ে দাঁড়ানো। নাম জিজ্ঞাসা করলে বললেন আব্দুল করিম। মসজিদটির নাম কদম রসুল মসজিদ। সুন্দর পরিপাটি করে রাখা। স্বল্প পরিচিতি লেখা এএসআই-এর তথ্য। অন্যটিতে লেখা রয়েছে এই চতুষ্কোণ এই গৃহটি সুলতান নসরত শাহ দ্বারা নির্মিত মসজিদ। এর ভেতরে স্থাপিত হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর পদচিহ্ন। এটি তৈরি করেন সুলতান নসরত শাহ। সামনে বিশ্রামাগার যার কিছু ধ্বংসাবিশেষ দেখা যায়। সামনের এক রুমের কুটুরির ভিতরে একটি কবর। যার সামনে করিম দাঁড়ানো। সামনে সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য। তাতে লেখা রয়েছে এটি ফতে খাঁয়ের সমাধি। এখানে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনাপতি দেলোয়ার খাঁর পুত্র ফতে খাঁ সমাধিস্থ হয়েছেন। সময়কাল ১৬৫৮ হতে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ। আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা সুলতান সুজাকে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরামর্শদানের জন্যে পীর শাহ নিয়ামুতুল্লাকে হত্যা করার জন্য সম্রাট পাঠিয়েছিলেন। কথিত রয়েছে যে গৌড়ে পৌঁছার পর ফতেহ খাঁ রক্ত বমি করে মারা গেলে তাকে এখানে সমাধিস্থ করা হয়।
নাসরুল্লাহ চত্বরে এসে কয়েকটা ছবি তুলে বাইরে গিয়ে একটি দোকানে বসলেন। বাকি সবাই একই জায়গায়। চত্বরের মাঝে গাছের নিচে একটি বেঞ্চে বসে জাকারিয়া সিগারেট ধরালেন। আমি মসজিদের দিকে রওয়ানা হলাম। সামনে পাকা চত্বর আর ছোট বারান্দায় একজন কথিত খাদেম বসা। তিনি জানালেন যে, ভিতরে রসুল (স.)-এর কদম মোবারকের ছাপটি রক্ষিত। আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। ছোট কামরার মাঝখানে একটি উঁচু বেদিতে একটি কালো পাথরখণ্ডের উপরে একজন পরিপূর্ণ মানুষের পায়ের ছাপ। খাদেম জানালেন এটাই হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর কদম মোবারকের ছাপ। জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কিভাবে এই কদমের পাথরটি এসেছে। তিনি তেমন কিছুই বলতে পারলেন না। আমাকে জিজ্ঞাসা করায় বললাম বাংলাদেশ থেকে এসেছি। তিনি বললেন বাংলাদেশ থেকে অনেকে এখানে আসেন। বারান্দায় নামাজও আদায় করেন। আমি একাই কিছুক্ষণ থেকে বের হয়ে এলাম। বের হওয়ার পথে দেখলাম তিনজন বিদেশি পর্যটক একটি গাড়িতে মসজিদ দেখতে এসেছেন। সঙ্গে একজন গাইড।
কদমরসুল মসজিদ থেকে বের হয়ে সামনের একটি চায়ের স্টলে বাকি সবাইকে পেলাম। গ্রামের চায়ের স্টল। পাশে একটা খাবারের দোকান। সেখানে গিয়ে মসজিদের কথা বলাতে আমাদের কয়েকজন বললেন আগে জানলে তারাও যেতেন দেখতে।
শমসের বললেন, নারায়ণগঞ্জে কদমরসুল মসজিদে এরকম আরেকটি কদম মোবারক রক্ষিত রয়েছে। আমি বললাম, হ্যাঁ আমি দেখছি, তবে ওই পদচিহ্নের চাইতে এটা আকারে ছোট এবং স্বাভাবিক মানের। নারায়ণগঞ্জের কদমের চিহ্নের পাথরটি বেশ যত্নে রাখা। সবসময় নাকি দেখানো হয় না। মসজিদটিও একটু উঁচু যায়গায়। আমাকে ওই মসজিদের খাদেম বলেছিলেন যে সম্রাট শাহজাহান এখানে অবস্থানকালে এটা দিয়েছিলেন এবং মসজিদের যায়গাটিও তিনি দান করেছিলেন। ওই সময়কার সামান্য স্থাপনাও রয়েছে। খাদেম আরও বলেছিলেন যে দানপত্রটি এখনও সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। নারায়ণগঞ্জেও একটি মোগলদূর্গ রয়েছে যেখানে মোগল সৈনিকদের অবস্থান ছিল। ১৬৩২ সালে সম্রাট শাহজাহানের হুকুমে পুর্তুগিজদের হাত হতে হুগলি বন্দর উদ্ধার করেছিলেন।
চা শেষ করে আমি, শাহাবুদ্দিন, জাকারিয়া এবং তানভীর পাশের আম বাগান দিয়ে অপর প্রান্তে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি স্থাপনা যা চিকা মসজিদ নামে পরিচিত সেদিকে রওয়ানা হলাম। আম বাগানে ঢুকতেই একটি বড় গাছের নিচে অস্থায়ী নরসুন্দরের দোকান দেখলাম। একটি চেয়ারে কাস্টমার বসা। সামনের গাছে মধ্যম সাইজের আয়না ঝুলানো। চুল কাটা শেষ হবার পর ক্ষৌরকর্মের জন্যে মুখে সেভিং ফোম লাগিয়ে হালকা ম্যাসাজ চলছিল। এমন আরামে খদ্দের আমেজে চোখ বুঝে রইলেন। হয়ত আমাদের আগমন তার আরামের কিছুটা ব্যাঘাত ঘটালো কারণ তিনি চোখ খুলে একবার আমাদেরকে দেখে নিলেন। এক সময়ে আমাদের গ্রামেগঞ্জে বিশেষ করে হাটের দিনে এরকম দৃশ্য অহরহ দেখা যেত এখন আর তেমন দেখা যায় না। এখন গ্রামের বাজার হাটেও চুল কাটার ছোটখাট দোকান রয়েছে। শহরে এখন আর ক্ষৌরকর্ম বলা হয় না বলা হয় হেয়ার কাট আর আধুনিক নরসুন্দরদের এখন পরিচিতি হেয়ার ড্রেসার। আমি তানভীরকে বললাম, মনে হয় না এখানে এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে ক্ষৌরকর্ম করি আর ওর ওই পাতা মাদুরে শুয়ে গা হাত পা মর্দন করাই। তানভীর বললেন, হোটের নিচতলায় স্পা (ঝঢ়ধ) রয়েছে সেখানে যাব।
হাঁটতে হাঁটতে আমরা চিকা মসজিদ নামক স্থাপনার গেটে চলে এলাম। একে গম্বুজ বিশিষ্ট স্থাপনাটি চারদিকে চারটি দরওয়াজা। ভিতরে আর কোনো জানালা নেই। সম্পূর্ণ ছাদটাই গম্বুজ আকৃতির। তথ্য ফলকে লেখা রয়েছে যে এই স্থাপনাটি তৈরি করেছিলেন সুলতান ইউসুফ শাহ ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে। তবে নামটি বেশ চমকপ্রদ। কেন এমন নাম তার একটি ব্যাখ্যা হল যে মসজিদের অভ্যন্তরে অগণিত চিকা বাদুরের বাস। তাই এ মসজিদের নামকরণ। মসজিদের খিলানে কোরানের সূরা খোদিত ছিল যার কিছুটা এখনও দেখা যায়। তবে মসজিদের নকশায় মন্দিরের ছাপ রয়েছে যে কারণে এটি অন্যান্য মসজিদ হতে আলাদা। মধ্যযুগীয় ইটে তৈরি মসজিদটির উপরে কোন আস্তর নেই।
তবে অনেকে মনে করেন এটা সুলতান জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ রাজা গণেশের পুত্র-এর সমাধি। হতেও পারে কারণ কোনো আঙ্গিকেই তথাকথিত চিকা মসজিদটি মসজিদ মনে হয় না। আমার কাছেও তেমনই মনে হয়েছে। তবে এখানে সমাধির কোনো চিহ্নও দেখা যায়নি। তবে এখানকার অনেক দর্শনীয় স্থানের ইতিহাস তেমনভাবে লিপিবদ্ধ নেই।
আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম যা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে তবে আশেপাশের সবুজ ঘাসের চত্বর পরিপাটি করে সাজানো। দক্ষিণদিকে কয়েকটি বাসস্থান। এখানে এএসআইর লোকজন থাকে। পূর্বপাশে একসময় হয়তো একটি জৈন মন্দির ছিল যার খণ্ডিত কয়েকটি পিলার এখনও দণ্ডায়মান। একটু সামনে প্রায় আট বা নয় ফুট লম্বা একটি পাথরের পিলার রক্ষিত। যেটি মন্দিরের পিলার। আরেকটু দক্ষিণে উঁচু ঢিবির মত। যার পেছনে শহরের দেয়ালের সামান্য ভগ্নাংশ এখন দৃশ্যমান। পূর্বপ্রান্তে লুকোচুরি দরওয়াজার পেছনের অংশ।
চিকা মসজিদটির নামের সাথে সুলতান সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের নাম জড়িত। তিনি ছিলেন সুলতান বারবাক শাহর পুত্র। তিনি বাংলার শাসক হন ১৪৭৪ সালে। শুধু এই মসজিদটিই নয় সুলতান ইউসুফ শাহ গৌড়ের আরও কয়েকটি মসজিদ তৈরি করেছিলেন। এমনকি কদমরসুল মসজিদের ভিতও তিনি স্থাপন করেন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। তিনি নিজেও ইসলামিক চিন্তাবিদ ছিলেন। তার স্থাপনাগুলোর মধ্যে বাংলার নির্মাণশৈলীর ঐতিহ্যও মিশ্রিত রয়েছে। তিনি ১৪৭৪ সাল হতে ১৪৮১ সাল পর্যন্ত বাংলার শাসক ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র দ্বিতীয় সিকন্দার শাহ বাংলার সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হয় ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে। তবে তার মানসিক ভারসাম্যের সমস্যা হওয়াতে মাত্র কয়েকদিন সুলতান ছিলেন। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার ভাই জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ।
বাংলায় হাবসী শাসকবৃন্দ ইলিয়াস শাহী বংশের মাঝখানে রাজত্ব করেছিলেন। এরা ছিলেন আবেসিনিয়ার হাবসী। এদের মধ্যে চারজন ছিলেন হাবসী সুলতান। বারবাক শাহ, ফিরোজ শাহ, কুতুবউদ্দিন মাহমুদ শাহ এবং শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ। যাই হোক বাংলার সুলতানদের ইতিহাসের অনেক যায়গা অস্পষ্ট রয়েছে।
আমরা চিকা মসজিদ থেকে ফিরে আসছিলাম তখনও দেখলাম আগে বর্ণিত নরসুন্দরের খদ্দের তখনও আরামে চোখ বন্ধ করে ক্ষৌরকর্ম উপভোগ করছেন। গাছের নিচে এমনিতেই বেশ শীতল পরিবেশ এই গরমে। এ ধরনের পরিবেশে এমনিতেই ঝিমুনি আসার কথা। আমারও খুব ইচ্ছে হচ্ছিল এখানেই এমনভাবে বসে চুল কাটাই।
চায়ের দোকানে ফিরে এসে আবার চা খাবার ইচ্ছে হলো। চা খেতে খেতে দেখছিলাম কিভাবে স্বামী-স্ত্রী দুজনে চায়ের দোকানটি পরিচালনা করছেন।
চায়ের দোকানটি একেবারে গ্রামেগঞ্জের পরিবেশে তৈরি। পাতা বেঞ্চে বসলাম। বিস্কুট চাইলে মহিলা বিস্কুটের ভাণ্ডটি এগিয়ে দিয়ে বললেন যে, আমাদের পছন্দমত বিস্কুট যেন তুলে নেই। জিজ্ঞাসা করলাম কেমন চলে? বললেন যে এই মৌসুমে আশেপাশের গ্রামের লোকছাড়া বাইরের লোক তেমন আসে না। তবে শীতের কয়েক মাস বেশ ভাল চলে। পর্যটকরাও যেমন আসে তেমনি এখানে প্রচুর পিকনিক পার্টি আসে। অবশ্য তার কিছুটা ধারণা আমরাও পেয়েছি আম বাগানে প্লাস্টিকের গ্লাস এবং খাবারের পরিত্যাক্ত পাত্র দেখে। আরও বললেন যে, আমের মৌসুমেও বেশ ভাল বেচাকেনা হয়।
অনেকক্ষণ বসে রইলাম এমন একটি ঐতিহাসিক যায়গায় সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে। আম গাছের প্রাচুর্য আর সবুজের মাঝে। শান্ত পরিবেশ দুপুরের রোদে পাশের আম বাগান হতে চিরপরিচিত ঘুঘুর ডাক শুনতে বড় ভাল লাগছিল। মনে হলো আরও কিছু সময় বসে থাকি কিন্তু সবাই উঠবার তাড়া দিলেন। ফেরার পথে বড় সোনা মসজিদটি দেখে মালদাতে গিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ সারব। বিকেলটায় সময় পেলে একবার ইংলিশ বাজারটা ঘুরে আসব।
গাড়িতে ফেরার পথে ভাবছিলাম যে এই শহরটি ওই সময় কেমন ছিল? প্রশ্ন জাগল যে এতগুলো স্থাপনা দেখলাম সবই বাংলার সুলতানি আমলের কিন্তু বল্লাল সেনের বাড়ি বলে কথিত রাজবাড়ি ছাড়া শাসকদের বাসস্থান বলে কোনো নির্দিষ্ট যায়গার খোঁজ পেলাম না। চোখেও পড়েনি। জাকারিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনিও বললেন, তাইতো? বললাম হয়ত ওই সময় পাকা প্রাসাদের চল তেমন ছিল না যেমনটি পরবর্তীতে মোগলদের সময় দুর্গের ভিতরে সম্রাটদের বাসস্থান ঘিরেই দুর্গের বিন্যাস ছিল। কিন্তু দিল্লি সালতানাতেও একমাত্র মোহাম্মদ বিন তুগলকের দুর্গ জাহানপনা ছাড়া আর কোনো স্থাপনায় বাসস্থান দেখা যায়নি।
আমরা গৌড়ের সবচেয়ে আলোচিত এবং পরিচিত বড় সোনা মসজিদের সামনে পৌঁছলাম। সামনে ছোট একটি পাড়া বা বাসস্থান। সামনে একটি বড় বটগাছ তার পাশে দুটি ছোট মুদির দোকান। সামনেই উঁচু একটি যায়গায় বড় সোনা মসজিদের অবশিষ্ট অংশ। বড় ধরনের ঘেরা দেয়া। সামনের গেটটি ভেজানো। দোকান থেকে একজন বললেন ভিতরে গিয়ে দেখতে পারেন। যদিও একটি টিকেট ঘর ছিল কিন্তু টিকেটের ব্যবস্থা নেই। আমরা গেটটি খুলে প্রবেশ করলাম। মসজিদটি মধ্যযুগীয় স্থাপত্যে তৈরি। ইট আর বড় পাথরের তৈরি। সামনে একটি বড় ঘাসের লন। সুন্দর পরিপাটি করে ছেটে রাখা। তার উল্টোদিকে সুলতানি দরওয়াজা। উত্তর দিকে আরেকটি প্রবেশ গেট তবে পূর্বদিকের প্রধান ফটক হতে ছোট। আমরা যে পথে এসেছি সেখানেও একটি গেট ছিল বলে মনে হয়।
মসজিদটি তৈরি করা শেষ হয়েছিল ১৫২৬ সালে। গৌড়ের সবচেয়ে বড় স্থাপনা এই বড় সোনা মসজিদ। সামনে পায়ে চলা পথ। লনের দু’পাশে হাঁটু সমান ফ্যান্সিং (স্টিলের তৈরি তারের বেড়া)। খুবই সুন্দর করে গাথা মসজিদটি ৫০.৪ মিটার লম্বা, ২২.৮ মিটার প্রশ্বস্থ এবং ১২ মিটার উঁচু। মূল মসজিদের অংশটিতে এখনও ছাদ রয়েছে। মেঝেটি পরিষ্কার তকতকে করে রাখা। এই মসজিদটি তৈরি শুরু হয়েছিল সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সময় এবং শেষ হয় তার পুত্র নাসিরুদ্দিন নসরতের সময়। মসজিদটির আদি নাম বারো দুয়ারি।
বারোদুয়ারি মসজিদটিতে বাস্তবে ১১টি প্রবেশ পথ রয়েছে, যার নকশা ইন্দো-আরব ধরণের। দু’পাশে দুটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার এবং চারকোনায় চারটি মিনার রয়েছে। মিনারগুলোর উচ্চতা বর্তমানের প্রচলিত মিনারের মতো নয়। উপরের ছাদে ৪৪টি আধা গম্বুজের মত তৈরি। ছাদের উপরের অংশে রয়েছে এই ৪৪টি গম্বুজ। তবে অনেকাংশ নষ্ট হলেও এখনও ১১টি বারান্দা রয়েছে যে জায়গায় নামাজ পড়া হতো। এই মসজিদের আদিনাম কুতুবশাহী মসজিদ। নামকরণ করা হয়েছিল সুফি দরবেশ নূর কতুব আলম যারা পিতার নাম সুফি মখদুম আলাউল হক পাণ্ডভী। সোনা মসজিদটির পিলারগুলো এক সময় সোনালি পাত দিয়ে মোড়ানো ছিল-তাই প্রচলিত নাম সোনা মসজিদ।
আমরা মসজিদের পশ্চিমদিকে গেলাম। সেখানে যে বারান্দাটি ছিল তার ছাদ ধসে পড়েছে। পিলারগুলো এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে বেশ কয়েকটি মেহরাব ছিল। পেছনে মানে পশ্চিম দিকে বেশ বড় বড় কয়েকটি পাকুর গাছ রয়েছে। নিচের দিকে সীমানার বাইরে পায়ে চলা পথ এবং বেশ জঙ্গলের মতো।
বেশ অনেকক্ষণ আমরা ঘুরে ঘুরে গৌড়ের সবচাইতে বড় স্থাপনাটি দেখলাম। বের হবার পথে উত্তর মাথায় দু’জন লোককে বসে থাকতে দেখলাম। আমি ওই দু’জনের কাছে গেলে তারা উঠে দাঁড়ালেন। লুঙ্গি গেঞ্জি পরিচিত এই দু’জনের একজন এএসআইর কর্মচারী যিনি এই জায়গায় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আর অপরজন পাশের পাড়ার যিনি এখানে পারিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজের জন্য খণ্ডকালীন নিযুক্ত। পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলাম এখানে এত ফ্লাড লাইট দেখছি এগুলো কি লাইট এন্ড সাউন্ড শোর জন্যে? উত্তরে জানালেন যে শীতের সময় লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হয় তবে প্রতিদিন হয় না। সপ্তাহে দু’ তিন দিন হয়। একজন বললেন আপনাদের ওখানেও তো ছোট সোনা মসজিদ আছে বলে শুনেছি। আমি বললাম হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন তবে ওই মসজিদটি বেশ ছোট। পরে আমি আদিনা মসজিদের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে আদিনা মসজিদ মালদা হতে উত্তর দিকে প্রায় ১৮ কি. মি. প্রধান সড়কের ধারে। ওই জায়গাটির এক সময়ের নাম ছিল ‘পাণ্ডু’। পাণ্ডু বেশ অনেক যুগ বাংলার রাজধানী ছিল। আমরা বড় সোনা মসজিদ হতে বের হয়ে মালদাতে ফেরার পথ ধরলাম। বললাম বিকেল চারটার দিকে আদিনা মসজিদ দেখতে যাব। জাকারিয়া, শমসের রাজি হল আমার সঙ্গে যেতে। পরে তানভীরও যুক্ত হয়েছিল।
গৌড় দেখার পর্ব এখানেই শেষ হলো। গৌড়ে এত স্থাপনা দেখতে পাবো তেমন ধারণা ছিল না। স্থাপনাগুলো যেভাবে সংরক্ষিত আছে সে রকম দেখতে পারব তেমন ধারণাও ছিল না। আমার মনে হল আমাদের এই সফর অন্যদের কাছে কেমন লাগল জানাবার প্রয়োজন। সবাই একবাক্যে বললেন যে এখানে না আসা পর্যন্ত ধারণাই করতে পারেননি যে এখানে এত কিছু দেখার রয়েছে। কয়েকজন তো নামই শুনেননি।
আমরা যে রাস্তায় এসেছিলাম সে রাস্তা ধরেই ফিরছি। এতক্ষণ টের পাইনি যে গরমে শরীর ক্লান্ত হয়ে পরেছে। হোটেলে গিয়ে আরেকবার গোসল করতে হবে।
গৌড় আর পাণ্ডু বা পাণ্ডুয়াতে এখনও যা রয়েছে সেগুলো মুসলিম শাসকদের কীর্তি। এদের কেউই এখনকার মাটির মানুষ ছিলেন না। যেমন ছিলেন না হিন্দু শাসকরাও। এরা সবাই বাংলায় এসেছিলেন সমৃদ্ধির খোঁজে, ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। বাংলায় বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, মুসলিম এবং ইংরেজ সবাই রাজত্ব করেছে।
বাংলায় মুসলমান সৈনিকদের আগমন এবং এখানে রাজত্ব কায়েমের সূত্রপাত হয় ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজির সময়। ভাগ্যান্বেষী একজন আফগান যোদ্ধা কুতুবউদ্দিন আইবেকের দিল্লি জয়ের পর ১২০২ সালে বিহার এবং ১২০৩ সালে নদীয়ার নবদ্বীপে সেন বংশের শেষ নৃপতি লক্ষণ সেনকে পরাজিত করেন। পরে গৌড়ে তিনি অস্থায়ী রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষণ সেন কুসংস্কারে বিশ্বাস করার কারণে বিনা যুদ্ধে পরাজিত হন। মাত্র ১৮ জন সৈনিক নিয়ে রাজধানী আক্রমণ করে সহজেই বখতিয়ার খিলজীর কাছে হার মানেন। লক্ষণ সেনের দরবারের জ্যোতিষী আজানু লম্বিত হাত বিশিষ্ট এক সিপাহশালারের হাতে তার পরাজয়ের ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন বলে তথ্যে পাওয়া যায়। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই লক্ষণ সেন তার রাজধানী পরিত্যাগ করেছিলেন।
বখতিয়ার খিলজি দক্ষিণ আফগানিস্তানের তুর্কি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বহু চড়াই উৎরাই পার হয়ে খিলজি বাংলা জয় করে রাজত্ব কায়েম করেন। খিলজী পরে তিব্বতের দিকে অভিযান চালান তবে কৃতকার্য হতে পারেননি। সেই হতেই বাংলায় মুসলমানদের শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল। এর পরে চতুর্দশ শতাব্দি হতে বাংলা স্বাধীন সুলতানদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। বাংলার সুলতানি শাসন বা শাহী বাংলা বেশির ভাগ সময়েই স্বাধীনভাবে শাসিত হয়। এর স্থায়ীকাল হয় ১৩৫২ হতে ১৫৭৬ পর্যন্ত। এর গোড়া পত্তন করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। এই রাজত্ব শাসন করেন পাঁচটি বংশ। ষোড়শ শতাব্দিতে শেরশাহ সূরীর বাংলা জয়ের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলার পতন হয়। শের শাহর পর মোগল সম্রাট হুমায়ুন বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করেন। আরও পরে ১৫৭৬ সালে সম্রাট আকবর পূর্ববাংলার শেষ সুলতান দাউদখান কররানীকে পরাজিত করেন। এরপর হতেই সমগ্র বাংলা অঞ্চল মোগল বাংলায় পরিণত হয়।
বাংলায় বারো ভূইয়াদের পরাজিত করে ১৬১০ সালে মোগল সিপাহসালার ইসলাম খাঁ রাজমহলে সুবে বাংলার রাজধানী স্থাপন করলেও পরে ঢাকাকে রাজধানী করেন। ওই সময়ে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শহরের নামকরণ করেন জাহাঙ্গীর নগর। গৌড় পরিত্যক্ত হয়। এরপর গৌড় আর পুরাতন ঐতিহ্য ফিরে পায়নি। মুর্শিদকুলি খাঁ দেওয়ানী ঢাকা হতে নতুন শহর মুর্শিদাবাদ পত্তনের পর বাংলার স্বাধীন নবাব ঘোষণার মধ্যদিয়ে রাজধানী ঢাকা হতে মুর্শিদাবাদ স্থানান্তর করেন। ইতিহাসে যা ঘটে যায় তাকে হয়তো ফিরিয়ে আনা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন থাকে ‘যদি’ রাজধানী ঢাকাতেই থাকত তবে কি ‘পলাশী’ ঘটতো।
আমরা দুপুর আড়াইটার দিকে হোটেলে ফিরে এলাম। রিসিপশন থেকে আদিনা মসজিদ, আদিনা পার্ক এবং পাণ্ডুয়ার অবস্থান জেনে নিলাম। তাড়াতাড়ি দুপুরের খাবার শেষ করে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে আমি, জাকারিয়া, শমসের আর তানভীর রওয়ানা হলাম আদিনা মসজিদ দেখতে। মাত্র ১৮ কি. মি. আধা ঘণ্টা সময় লাগার কথা। আমরা মালদা শহরের সুকান্ত মোড় পার হয়ে উত্তরদিকে রওয়ানা হলাম। এ ধারের রাস্তা ৪ লেনের বেশ প্রশস্ত। মাঝের ডিভাইডারও বেশ চওড়া। শহরের এ-প্রান্তে রাস্তায় কিছুটা ভিড়। ট্রাকের সমারোহই বেশি। আশেপাশের শ্রীহীন দোকানগুলো দেখে মনে হলো যে শহরটি তেমন বিত্তবানদের নয়। মাঝপথে এক যায়গায় থামলাম ফল কেনার জন্য। শমসের পাশের হকারের কাছ থেকে একটা তরমুজ কিনলেন আর এক ডজন কলা। আমি কাছাকাছি এক ঠেলাগাড়ি হতে আঙ্গুর কিনব বলে দাঁড়ালাম। এ সময় আঙ্গুরের মৌসুম। বেশ সুস্বাদু। আসে নাসিক অঞ্চল এবং জম্মু কাশ্মীর হতে। আমার পাশে শমসের এসে দাঁড়ালেন। বললাম কিছু আঙ্গুর নিয়ে যাই। বিক্রেতাকে দাম জিজ্ঞাসা করলে বললেন, ২৫০-২৫। আমি মানেটা বুঝলাম না। ২৫০-২৫ মানে কি জিজ্ঞাসা করতেই পাশে দাঁড়ানো শমসের বললেন মানে ২৫০ গ্রামের দাম ২৫ রুপী। তার মানে ১ কেজি ১০০ রুপী। বিক্রেতা বিগলিত হয়ে বললেন, তাই বাবু। আমি বললাম আমি তো ১ কেজি নেব। শুনে দারুণ উল্লসিত হয়ে ১ কেজি মেপে দিলেন। শমসের বললেন, এখানে আমাদের মত ১ কেজি করে খুব কম কেনে তাই ২৫০ গ্রামের হিসাব।
আমরা অনেকগুলো ফলফলাদি কিনে পুনরায় আদিনা মসজিদের পথে রওয়ানা হলাম। আদিনা মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন বিশাল পার্কের নাম আদিনা সাফারি পার্ক। আদিনা মসজিদটি ওই সময়ে এশিয়ার তথা তৎকালীন ভারতের সবচাইতে বড় মসজিদ ছিল। মসজিদটি ছিল বাংলার আরেক রাজধানীর এক প্রান্তে।
পাণ্ডুয়া কোন সুলতানের সময় স্থাপিত হয়েছিল তা খুব একটা নিশ্চিত নয় তবে ঐতিহাসিক তথ্য মোতাবেক ধারণা করা হয় যে শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ-এর সময় এ শহরটি তৈরি করা হয়। পরে ১৩৩৯ সালে আলাউদ্দিন আলী শাহ গৌড় হতে রাজধানী পাণ্ডুয়াতে স্থানান্তরিত করেন। যদিও দুটি ঐতিহাসিক শহর খুব দূরে নয় তথাপি এই দুই জায়গা বাংলার রাজধানী ছিল। পাণ্ডুয়া রাজধানীর মর্যাদা হারায় ১৪৫৩ সালে যখন নাসিরুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ পুনরায় গৌড়ে রাজধানী নিয়ে যান। পাণ্ডুয়া মালদার ইংলিশ বাজার হতে মাত্র ১৮ কিলোমিটার। পাণ্ডুয়াতে এখন দেখার তেমন কিছু নেই। আদিনা মসজিদ ছাড়াও ঐতিহাসিক স্থাপনার মধ্যে আরও রয়েছে এখলাখি সমাধি সৌধ এবং কুতুবশাহী মসজিদ। আদিনা মসজিদটি অনেকটা দামেস্কের গ্রান্ড মসজিদের আদলে তৈরি করেছিলেন সিকান্দার শাহ ১৩৬৯ সালে। আর এখলাখি সমাধী সৌধটি সুফি সাধক বলে পরিচিত জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহের। জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ প্রায় ১৫ বছর রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন বাংলার রাজা গনেশের পুত্র।
রাজা গনেশ বাংলার সুলতান বংশ প্রথম ইলিয়াছ শাহীদের দুর্বলতার কারণে ক্ষমতা দখল করেন ১৪১৫ সালে। পরে তার পুত্র ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করে বাংলার সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হয়। তার সময়েই আরাকান রাজ্যের স্বাধীনতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্বাধীন আরাকান তখন বাংলার করদ রাষ্ট্র হিসেবে ছিল। চিকা মসজিদে তার কবরের ধারণাটি হয়ত সঠিক নয়।
রাজা গনেশের নাম জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহের মুদ্রায় উল্লেখিত রয়েছে কানস রাও অথবা কানস শাহ হিসাবে। তিনি মাত্র ১ বছর (১৪১৪-১৪১৫) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে রাজা গনেশ ভাটুরিয়ার শক্তিশালী জমিদার এবং দিনাজপুরের গভর্নর হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন। বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাস যথেষ্ট জটিল। দিল্লির ইতিহাসের মত এতটা পরিচিত নয়।
আমরা পুরাতন মালদা ছেড়ে হাইওয়েতে। দুপাশে কৃষিক্ষেত। আমের বাগান। এ অঞ্চলে কিছু শিল্প কারখানা রয়েছে। চার লেনের হাইওয়ে। আমরা উত্তরমুখী। ছোট উন্নত গ্রাম সুলতান দিঘী পার হলাম। বেশ কিছু পাকাবাড়ি। ফাঁকে ফাঁকে বাঁশের বেড়া আর মাটির দেয়ালের বাড়িগুলোর উপরে লাল টালি দেয়া। রাস্তায় তেমন ভিড় নেই। সুলতান দিঘি পার হওয়ার পর পশ্চিম দিকে বিএসএফ-এর ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর। মাঠে কিছু সদস্য ফুটবল খেলায় রত। অতি পরিচিত দৃশ্য। সামনে দিক নির্দেশনা বোর্ডে লেখা পাণ্ডুয়া সামনে। আমরা আদিনা মসজিদের কাছাকাছি। পশ্চিমে একটি ছোট রাস্তা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেছে। রাস্তার জংশনের কাছাকাছি একটি মধ্যযুগীয় ছোট মসজিদের মত দেখলাম। রাস্তার দিক নির্দেশনা বোর্ডে লেখা পাণ্ডুয়া। একটু ভিতরে গেলেই পাণ্ডুয়া গ্রাম যা এক সময় বাংলার রাজধানী ছিল। আদিনা মসজিদটিও পাণ্ডুয়ার একাংশে। যে পুরনো মসজিদটি আমরা ছেড়ে এসেছি সম্ভবত ওটাই কুতুবশাহী মসজিদ। ওখানে যাওয়া হয়নি কারণ আমাদের হাতে সময় ছিল না। সূর্য হেলে পড়েছে প্রায় পাঁচটা বাজে। প্রায় আরও এক কিলোমিটার যাওয়ার পর হাইওয়ের পশ্চিম পাশে একটি ছোট রাস্তা, মোড়ে বেশ কিছু কাচাঘরে চায়ের আর রকমারি দোকান। লেখা আদিনা মসজিদ। রাস্তা থেকেই মসজিদের ভগ্নাংশ দৃশ্যমান হল। এটাই ইতিহাস খ্যাত আদিনা মসজিদ।
গাড়ি এক পাশে দাঁড় করিয়ে আমরা চারজন নামলাম। উত্তরেই আদিনা মসজিদ। সুন্দর করে ফ্যাঞ্চিং (স্টিলে তৈরি তারের বেড়া) ঘেরাও দেয়া। আমরা গেটের সামনে গিয়ে দেখলাম গেট বন্ধ। তারই সামনে মোবাইল আইসক্রিম বিক্রেতা। পাশে পানিপুরির ঠেলা গাড়ি। চিকন রাস্তার অপর পাড়ে কয়েকটি বসতবাটি। কয়েকজন মহিলা আর পুরুষ বসে রসুন পরিস্কার করছে। বেশ কয়েক মণ হবে। মনে হলো খেত হতে উঠানোর পর রাস্তার উপরেই শুকানো সেরে পরিস্কার করতে ব্যস্ত। আমরা গেটের কাছে এসে দেখলাম বড় তালা ঝুলছে। পাশে এএসআই-এর সাইন বোর্ড। টিকিট ঘরটি বন্ধ। ওখানে কাউকে দেখলাম না। আইসক্রিম বিক্রেতা জানালেন যে পাঁচটায় গেট বন্ধ হয়ে যায়। সকাল ৮টায় দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেয়া হয়।
আমরা বেশ মর্মাহত হলাম। এত দূর এসে ভিতরে যেতে পারলাম না। মাত্র ১০ মিনিট দেরি করে এসেছি। আশপাশে এএসআইর কাউকেই দেখলাম না যাকে অনুরোধ করে গেট খোলতে পারতাম। আমাদের চেহারায় হতাশা দেখে আইসক্রিম বিক্রেতা জিজ্ঞাসা করলেন কোথা থেকে এসেছি? বাংলাদেশ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজশাহী? বললাম না ঢাকা হতে। বললেন, রাজশাহী তো অনেক কাছে। তার কথা কানে ঢুকল না।
অগত্যা দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানো ছাড়া এ পর্যায়ে আর গতি পেলাম না। বেষ্টনীর বাইরে দাঁড়িয়ে যতটুকু দেখা যায়। মসজিদটি ওই সময়ে ভারতবর্ষের সবচাইতে বড় মসজিদ ছিল। এখন পরিত্যক্ত ভগ্ন দশায়। উপরের বেশির ভাগ জায়গায় ছাদ ভেঙে পরেছে। ভিতরে যতটুকু দেখা গেল তাতে মনে হল ভিতরের অংশ উত্তর দক্ষিণে বড় আয়তনের নামাজের জায়গা ছিল। পশ্চিম প্রান্তে বেশ বড় জায়গায় সবুজঘাসের চত্বর। আশপাশে পুরাতন বেশ কিছু আমের গাছ। সামনে দাঁড়িয়ে এএসআই-এর তথ্য কনিকা পড়লিাম। এ ধারের সব গ্রামগুলোতেই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকের বাস। চেহারায় চলন বলনে তেমনই মনে হলো। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে যতটুকু সম্ভব দেখলাম। পূর্বদিকে লম্বা টানা বারান্দা ছিল। বেশ কয়েকটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরদিকে একটু উচু বেদী যেখানে সুলতানের বসবার জায়গা ছিল।
মসজিদটি দামেস্কের উমাইয়া মসজিদের আদলে তৈরি। এই মসজিদটি তৈরি হয় বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় সুলতান সিকান্দার শাহের সময়-চতুর্দশ শতাব্দীতে। সিকান্দার শাহ ছিলেন সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের পুত্র। সিকান্দার শাহ দিল্লির সুলতানদের আধিপত্যকে পরাজিত করে বাংলাকে পুর্ণাঙ্গ স্বাধীন সালতানাতে পরিণত করেন। সিকান্দার শাহ দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করাতে বাধ্য করেন একটি একটি চুক্তির মাধ্যমে। সিকান্দার শাহ প্রায় তিন দশক শাসন করেন এবং সম্রাট শাহজাহানের মতই শিল্প পিপাসু ছিলেন। তার সময়েই বেশিরভাগ স্থাপনা তৈরি হয়েছিল। এএসআইর তথ্য মতে, এর নির্মাণকাল ১৩৭৩ সাল। বর্তমানে এসব দর্শনীয় জায়গা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে।
জাকারিয়া, তানভীর আর শমসের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছবি উঠাতে ব্যস্ত। আমি এএসআইর তথ্য কনিকা পড়ছিলাম। সামান্য কিছু তথ্য রয়েছে বোর্ডে। মসজিদটি বাংলার সুলতানদের এবং বাংলার স্থাপত্যের গর্বের বিষয় যদিও এখন এর ভগ্নাংশই রয়ে গিয়েছে। মসজিদের দৈর্ঘ্য মোট ১৫৫ মিটার প্রস্থ ৮৭ মিটার। নামাজের জায়গা ২৪ মিটার প্রশ্বস্থ। উচ্চতায় ছিল ১৮ মিটার বারান্দাটি ছিল ১২ মিটার প্রশ্বস্থ। ইট পাথরের সমন্বয়ে তৈরি মসজিদটি। মসজিদের চারদিকেই বারান্দা ছিল যার ভগ্নাংশ এখনও দেখা যায়। উত্তরের একাংশে ছাদ এখনও রয়েছে। রয়েছে ছাদের কলামগুলো অনেক মৌমাছির বাসার মতো, হানি কম্ব সাদৃশ্য।
সমগ্র, গৌড়, যতটুকু দেখিছি প্রায় দশ বছর আগ পর্যন্ত এসব নিদর্শনগুলো প্রায় অজত্নে ছিল যা মুর্শিদাবাদে আমার প্রথম ভ্রমণেই দেখেছিলাম। একথা স্বীকার করতেই হবে যে মমতা ব্যানার্জীর সরকার বাংলার গৌরবময় ইতিহাসের নিদর্শনগুলো তা যে ধর্মেরই-কালের হোক সংরক্ষিত করে রাখছেন যার উদাহরণ মুর্শিদাবাদের মতিঝিল পার্ক এবং মুর্শিদাবাদের ইতিহাস। গৌড় বা লক্ষনাবতীর ইতিহাসই বা আমরা কতখানি জানি বা দেখতে বা বুঝতে চাই। এখানে এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে না এলে বুঝতে পারতাম না। হয়ত আরও আগে এলে আরও ভাল হতো। গৌড় বা পাণ্ডুয়ায় যা দেখেছি তা ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যের নিদর্শন হলেও এর সাথে মিশ্রণ হয়েছে বাংলার স্থাপনা এবং সামাজিক ঐতিহ্য। ছাদ এবং পিলারগুলো দেখলেই সহজে ধারণা করা যায়। অনেক স্থাপনার ছাদ বাংলার সাধারণ বাড়ির বা ঘরের ছাদের আদলেরও দেখেছি। এগুলো দিল্লি বা উত্তর ভারতে স্থাপত্যের চাইতে আলাদা।
প্রায় ৪০ মিনিট কাটালাম। জাকারিয়া বললেন, আফসোস পাণ্ডুয়ার অন্যান্য জায়গায় ঘুরে দেখতে পারলাম না। আমি বললাম পাণ্ডুয়ায় দেখার মতো এই আদিনা মসজিদ। একে ঘিরে অনেক ইতিহাস রয়েছে। এমন হতে পারে যে আগামীকাল আমরা কলকাতায় ফেরার পথে ৮টায় এখানে এসে যদি ৯টাতেও রওয়ানা হই তাতেও আমরা সময়মতো পৌঁছতে পারব। তবে সেক্ষেত্রে হোটেলে গিয়ে বাকিদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কলকাতা মালদা হতে দক্ষিণে কাজেই এ জায়গায় এলে আসা যাওয়াতে আর ৩৬ কি. মি. যোগ করতে হবে। আমার সন্দেহ হল যে আদৌ সকালে আমরা আসতে পারব কিনা?
আমাদের ফেরার পালা। হঠাৎ মনে হলো শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে। প্রচুর ধোঁয়া উঠছে আশপাশের বসতবাড়িগুলো হতে। এ অঞ্চলে এখনও জ্বালানি হিসেবে শুকনা গোবর ব্যবহার করা হয়। প্রায় সব বাড়িতেই ব্যবহার হয় গোবরের ঘুটে যা ছোট বেলায় আমাদের গ্রামগঞ্জেও দেখেছি। এখনও হয়ত ব্যবহার হয় তবে খুব কম। উত্তরবঙ্গের গ্রামের দিকে দেখা যায় মাঝে মধ্যে। তবে এখন তেমন প্রচলন নেই। এখন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থাপন্ন বাড়িঘরে এলএনজি ব্যবহার হয়। দেয়ালে ঘুটে শুকানোর দৃশ্য কলকাতা শহরের প্রান্তেও দেখেছি বিশেষ করে হুগলী নদীর পূর্বপাড়ে।
আমরা ফিরছিলাম সূর্যের আলো তখনও রয়েছে। উত্তরমুখী লেনগুলোতে ক্রমেই ট্রাকের ভিড় বাড়ছে। আমি আদিনা মসজিদের ইতিহাসের সামান্য অংশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম এখানে আসার আগেই। যারা উত্তর বঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে জানেন তারা হয়তো আদিনা মসজিদের নাম আগেই শুনেছেন। এই মসজিদটিই ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম ঘাটি।
উত্তরবঙ্গে বৃটিশ এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল। সদ্য ধর্মান্তরিত হিন্দু-ধর্মালম্বী সাঁওতালরা এ এলাকাসহ উত্তরবঙ্গে সাঁওতালদের আলাদা আবাসভূমির দাবিতে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৯২৪ সালে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন জিতু সাঁওতাল। এর আগে দিনাজপুর-রাজশাহী এবং উত্তর মালদা সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হলে মালদা অঞ্চলে জিতু নামক সাঁওতালের নেতৃত্বে শুরু হয় এবং ১৯৩২ সালে জিতুর হত্যার মধ্যদিয়ে বৃটিশ এবং এ অঞ্চলের জমিদার বাহিনী এ বিদ্রোহ দমন করে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে জিতু আদিনা মসজিদকে দখল করে দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করেন। এমনকি মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তরিত করেন। পরে এখানেই জিতুর মৃত্যু হয় একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মসজিদটি পুনঃদখল করা হয়েছিল। ওই সময়েই মসজিদটি প্রচুর ক্ষতি হয়। তথ্যে প্রকাশ যে, মসজিদের দেয়ালে এখনও বৃটিশদের ছোড়া বুলেটের চিহ্ন রয়েছে।
আমরা যখন হোটেলে ফিরলাম তখন সন্ধ্যা সাতটার উপরে। আঙ্গুরগুলো ধুয়ে আনতে বললাম। গোসল করে চা পানের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। রাত নয়টায় হোটেলের পাঁচতলায় রেস্তোরাঁতে খাবারের অর্ডার দেয়া ছিল। এতক্ষণ সময় আমার রুমমেট তানভীর কলকাতার সিরিয়াল দেখে কাটালেন। বললেন, রাত দশটায় নাকি আরেকটি জমজমাট সিরিয়াল হয়। কয়েকটি সিরিয়াল নাকি তিনি কিছুতেই মিস করেন না। এ সব সিরিয়াল আমার কোনোদিন পছন্দ হয়নি কারণ বেশিরভাগ সিরিয়ালে বাঙালি পরিবারের ঐতিহ্যকে পরিহাস করা হচ্ছে। শ্বশুরের বিরুদ্ধে ছেলের বউয়ের ষড়যন্ত্র বউয়ের বিরুদ্ধে শাশুড়ি, ছেলের বিরুদ্ধে শাশুড়ি এমনকি বউ ছেলে মা বাবার বিরুদ্ধে নানা ধরনের কূটনামি। মাত্র কয়েকদিন আগে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন।
রাতের খাবার টেবিলে এসে বুঝলাম যে সকালে আমাদের আদিনা মসজিদে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা কার্যকর হচ্ছে না কারণ জয়ন্ত আর শার্শার মান্নানকে তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। তারা কেউই উত্তরে মোট ৩৬ মাইল যেতে আসতে চাইবে না। আমি অনেক আগেই বিষয়টি আঁচ করেছিলাম।
অবশেষে সকাল সাড়ে আট টায় আমরা কলকাতার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। রাস্তায় নাস্তা সেরে আমরা দুপুরের খাবার কৃষ্ণনগরে খেয়েছিলাম। কলকাতায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে গেল। পরের দিন আমরা ঢাকার পথে রওয়ানা হলাম। শেষ হল আমাদের মধ্যযুগীয় স্বাধীন বাংলার রাজধানী গৌড় দর্শন। আমাদের বাড়ির কত কাছে বাংলার ইতিহাসের এই গৌরবময় অধ্যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে এত কাছে। গৌড়ের ব্যাপ্তি চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত ছিল যার সাক্ষী ছোট সোনা মসজিদ এবং কোতোয়ালি দরওয়াজা। বলতে হয় যে, ‘দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে দু’পা ফেলিয়া একটি ধানের শীষে একটু শিশির বিন্দু।’
কয়েকদিন আগে আমাদের সকালের আড্ডায় বসে মনে হলো অনেকদিন দেশের বাইরে যাওয়া হয় না। আমাদের আড্ডার সংগঠক হাবিবুর রহমান খান আর দেরি করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন। কোথায় যাব? আর কোথায় ঢাকা-কলকাতা। আমি বললাম কলকাতায় আর কত যাব? হাবিব বললেন, তা হলে কলকাতা থেকে বাইরে কোথাও যাই। জায়গা নির্ধারণ করার দায়িত্ব আপনার (মানে আমার)। তা কি আর বলতে এ কাজটা আমার জন্যে অবধারিত। সঙ্গে সঙ্গে বললাম চলুন এবার ঐতিহাসিক স্বাধীন বাংলার রাজধানী গৌড় আর পাণ্ডুয়া দেখে আসি। প্রশ্ন সেগুলো কোথায়? বললাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জের অপর পাড়ে বর্ধমানের মালদা জেলায়। এরপরেই দলভারি হতে থাকল। মোট সাতজন প্রস্তুত হলেন প্রস্তাবিত গৌড় দর্শনে। তখনও বেশির ভাগেরই গৌড় সম্বন্ধে তেমন ধারণা ছিল না।
প্রথমে ভেবেছিলাম কলকাতা হতে ট্রেনে ‘মালদা’ গিয়ে স্থানীয় কোনো মাইক্রোবাস ভাড়ায় নেবো। তবে কলকাতা হতে খবর নিয়ে হাবিব জানলেন যে সড়ক পথে যাওয়াটাই উত্তম কারণ ট্রেনের সময় এবং বিড়ম্বনা হতে পরিত্রাণ পাবার সহজ উপায় সড়ক পথ। সড়ক পথে যাওয়ার এবং মালদাতে থাকার হোটেল বুকিং সব ব্যবস্থাই সম্পন্ন হলো। এ ব্যবস্থা হাবিবের মাধ্যমেই হয়েছিল। টিমে হাবিব আর আমার পরিকল্পনায় যোগ দিলেন ডা. নাসরুল্লাহ, ড. তানভীর আহমেদ খান, হাবিবের দুই বন্ধু শমসের এবং শাহাবুদ্দিন এবং সর্বশেষে যোগ দিলেন আমাদের ভ্রমণ গ্রুপের অন্যতম সদস্য জাকারিয়া। এদের সবার পরিচয় আমার একাধিক ভ্রমণ কাহিনীতে রয়েছে তাই নতুন করে পরিচয় দিলাম না। এ সফরের উদ্যোক্তা হাবিবুর রহমান খানের মন পারিবারিক কারণে খারাপ থাকলেও মেজাজ বেশ ফুরফুরে ছিল। কারণ এর মধ্যেই জানতে পেরেছেন যে তার প্রযোজিত ছায়াছবি ‘শঙ্খচিল’-এ অভিনয়ের জন্যে নায়িকা কুসুম সিকদার এবং শিশু শিল্পী হিসেবে তার ছেলের ঘরের নাতনী সাঁজবাতি শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্যে রাষ্ট্রীয় পুরষ্কার পেতে যাচ্ছে। ছবিটি গৌতম ঘোষ পরিচালিত যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছিল। আমার ভ্রমণ সঙ্গীদের আদি দলটি গঠিত হয়েছিল ২০১২ সালে জর্ডান সফরের মধ্যদিয়ে (জর্ডান নদীর তীরে দ্রষ্টব্য)। দলটি মাঝে-মধ্যে কলেবরে কমলে বা বাড়লেও সফর পাগল হাবিবুর রহমান বাদ পড়েন না।
যাই হোক আমাদের সফর শুরু হলো। আমরা আগেই সীদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে একবার মৈত্রী ট্রেনে ঢাকা-কলকাতা যাব। এর অন্যতম কারণ যে এদিকের কাস্টমস পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ঢাকায় আর কলকাতাতে কাস্টমস ইমিগ্রেশন সবই সম্পন্ন হয়। যথারীতি নিয়মমাফিক অগ্রিম টিকিট কেনা হলো। আমার সঙ্গে কনিষ্ঠপুত্র সাফাকও তৈরি হলো। তবে সে কলকাতার বাইরে যেতে পারবে না তার কিছু কাজের চাপে। আমরা ঢাকার ক্যান্টনম্যান্ট স্টেশন হতে কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে ট্রেনে চাপলাম। পুরো ট্রেন এসি আর চেয়ার কোচ। সব মিলে প্রায় ৪৫০ জন যাত্রী। সম্পূর্ণটাই ভর্তি।
ঢাকায় কাস্টমস ইমিগ্রেশন শেষ করতেও বেশ সময় নেয় কারণ স্টেশনটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও ছোট। তথধিক ছোট স্টেশনের দালানটি। কাজেই হুড়োহুড়ি আর গাদাগাদি হয়েই থাকে। এর আগে ২০১১ সালে প্রথম ট্রেন চেপে কলকাতা গিয়েছিলাম। প্রচুর সময় লেগেছিল দর্শনা আর ভারতের গেদেতে কাস্টমস সম্পন্ন করতে। সব যাত্রীদের দুবার করে মালপত্র নিয়ে নামতে হয়েছিল (বাংলা-বিহার প্রান্তরে দ্রষ্টব্য)। অন্তত সে বিড়ম্বনা লাঘব হয়েছে এবার। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল। সবাই বাসা থেকে হালকা নাস্তা করে আসার কথা ছিল তবে তেমনটা হয়েছে বলে মনে হয় না কারণ ভোর ৬টায় স্টেশনে আসতে হয়েছে। কাজেই প্রথমে নাস্তার অর্ডার নিতে এল ক্যাটারিংয়ের ওয়েটার। তার পেছনে টিটি এবং এসি কোচের সুপারভাইজার। সুপারভাইজার আমাকে দেখে অভিবাদন দিয়ে বললেন, স্যার খেয়াল করিনি যে আপনি ট্রেনে। ২০১১ সালে আপনি ট্রেনে চড়েছিলেন সে সময়ে আমরা আপনাকে আমাদের হাল শুনিয়েছিলাম। তাঁর কথা শেষ না হতেই ট্রেন এক্সামিনার যোগ দিলেন। তিনিও জানালেন যে ওই সময় থেকেই তিনি এই ট্রেনে ডিউটি করে আসছেন। তখনও যে অবস্থায় ছিল এখনও তাদের সেই অবস্থানই রয়েছে।
ওই সময়ে তারা বলেছিলেন যে তাদের প্রতিপক্ষ ভারতীয় রেলওয়ে স্টাফদের বাংলাদেশে অবস্থানের জন্যে ডলারের হিসাবে ভাতা দেয়া হয়। দিন প্রতি ৭২ ইউএস ডলার। অথচ বাংলাদেশী রেলওয়ে কর্মচারী যারা কলকাতায় রাত কাটান। তাদের জন্য আজ পর্যন্ত কোনো আলাদা ভাতা নির্ধারণ করা হয়নি বা বৈদেশিক মুদ্রাতে পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। তাদের নিজেদের পয়সাতেই ভারতে অবস্থানকালে থাকা-খাওয়া মিটাতে হয়। আমার মনে পরে যে ওই সময় আমি রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এ বিষয়টি জানিয়েছিলাম। আজ প্রায় ৭ বছর পর একই অনুযোগ শুনতে পেয়ে দুঃখই পেলাম। এত দিনে আমাদের দেশ মধ্যম আয়ের পথে রয়েছে বলে যখন সরকার উৎসব উদযাপন করছে তখনও তাদের এই নিম্ন বেতনভূক কর্মচারীদের সামান্য ভাতার ব্যবস্থাও করতে পারছে না বা করছে না। আমি বললাম যে যদি সম্ভব হয় তবে এ বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো আর না হলে নূন্যতম আমি যা করতে পারি তা হল আমার কোনো লেখনীতে তুলে ধরব। তাদের একথা আমার মনে রয়েছে তবে এখন পর্যন্ত তেমন কাউকে বলতে পারিনি।
কিছুক্ষণ পর নাস্তা এবং আরও পরে দুপুরের খাবারও সরবরাহ করলো তারা। বিল খুব বেশি নাহলেও খাবারের মান খুব ভাল ছিল তা বলা যাবে না। এদিক থেকে ভারতের রেল কর্তৃপক্ষ বেশ এগিয়ে। লম্বা সফরে বেশ কয়েকবার উচ্চক্লাসের যাত্রীদের খাবার ও নাস্তা সরবরাহ করে যার ন্যূনতম দাম টিকিটের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। যারা দূরপাল্লায় ভারতীয় ট্রেনে সফর করেছেন তাদের অভিজ্ঞতা বেশ সুখকর। এতদিনে আমরা আমাদের ট্রেন সার্ভিসে এমন কিছু চালু করতে পারিনি। যেহেতু পথে যাত্রীদের ট্রেন ছাড়বার বিধান নেই সেহেতু আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থাও নেই।
যাই হোক ট্রেনের সফর বেশভালই ছিল তবে যারা বিমান যাতায়াতে অভ্যস্থ তাদের জন্যে সময়টা একটু বেশি। কলকাতা স্টেশনে পৌঁছুতে স্থানীয় সময় প্রায় চারটা বেজে গেল। প্রথমদিকে থাকায় তাড়াতাড়ি বের হতে পেরেছিলাম তবে ট্যাক্সি পেতে সময় লেগেছিল। কলকাতায় হাবিবের কথিত এবং কমন মামু শার্শার জনাব মান্নান আমাদের সঙ্গে সড়ক পথে গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। সঙ্গে আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় জয়ন্ত শর্মা এবং কলকাতার আড্ডার আরেক সদস্য অলক মুখার্জি। কলকাতা মানেই আমাদের সঙ্গে এই দুজন। এ দু’জন হাবিবের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে আমাদের সকলের সঙ্গেই যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। যাদের বাদ দিয়ে আমাদের কলকাতার কোনো সফর পূর্ণ হওয়ার নয়। মাঝে-মধ্যে দু’জনই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে ঢাকাতেও আসা-যাওয়া করে। জয়ন্ত শর্মার মাধ্যমেই এবারের সফরের ব্যবস্থা করেছেন হাবিবুর রহমান। জাকারিয়া দেরি করাতে ট্রেনের টিকিট পায়নি তাই সন্ধ্যায় বিমানে পৌঁছবার কথা। আমাদের নিবাস হবে সল্ট লেকের একটি গেস্ট হাউস। যেখানে আমরা আগেও ছিলাম।
পাঠকদের কাছে এই দুই ব্যক্তির পরিচয় না দিলেই নয়। জয়ন্ত শর্মা এক সময় ছোটখাট ব্যবসা করতেন। তিনি এক সময়ের নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা। বয়স প্রায় ৭৪ বছর। এখন তেমন কিছু করেন না তবে জয়ন্ত মানেই আমাদের কলকাতার গাইড। অতি উৎসাহের সঙ্গে প্রায় সারাদিন আমাদের সঙ্গে কাটান আর যখন যা প্রয়োজন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে সে কাজগুলো করেন। বাজার করার অপরিহার্য গাইড জয়ন্ত শর্মা। লম্বা একহারা গড়ন কিন্তু দারুণ উদ্যোমী একজন মানুষ। এমনই অবস্থা যে জয়ন্ত ছাড়া কলকাতায় আমরা প্রকৃতপক্ষে বিকল। জয়ন্ত শর্মা একজন পারিবারিক সদস্যই হয়ে গিয়েছেন। কলকাতার বাইরে এ সফরেও জয়ন্ত আমাদের গাইড।
হাবিবের সঙ্গে জয়ন্ত শর্মার পরিচয় প্রায় ৩৮ বছর গড়িয়েছে। সেই হতেই এক ধরনের হরিহর আত্মা। অলক মুখার্জির সঙ্গেও প্রায় ৩০ বছরের পরিচয় চলচ্চিত্র নির্মাণের সূত্রে। অলক এক সময় ব্যাংকে চাকরি করতেন বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। দারুণ আড্ডাপ্রিয় মানুষ। এমন আরও কয়েকজন যাদের সঙ্গে আমরা এখন সবাই পরিচিত। আগেই বলেছি কলকাতায় কাটিয়ে আমরা মালদার পথে রওয়ানা হবো। তবে রাস্তায় একরাত থাকব বহরমপুরে। এর কারণ আমাদের সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন মুর্শিদাবাদ দেখেননি। আমি অবশ্য দুবার মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম কাজেই আমার উৎসাহ তেমন না থাকলেও আমাদের অন্যতম সদস্য ড. নাসরুল্লাহ মুর্শিদাবাদ বেড়াতে আগ্রহী। তবে তার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখলাম জাফরগঞ্জে মীর জাফরের এবং তার বংশের কবরগুলো দেখার। তার মতে মীর জাফরের কারণেই ইংরেজ শাসন এবং উপমহাদেশের আধুনিক হবার দ্বার উন্মোচন। জানি না তার এ ধারণার সঙ্গে কতজন একাত্ম হবেন। তবে এগুলো ইতিহাসের ‘যদি।’ যদি সিরাজ পরাজিত না হতেন তবে বাংলা কি স্বাধীন থাকতো বা আধুনিক রাষ্ট্র হতো। এসবের উত্তর কোনো পণ্ডিতের পক্ষেই দেয়া সম্ভব বলে মনে হয় না।
কলকাতায় দুদিন ছবি দেখা আর আড্ডা দেয়া ছাড়া আমাদের তেমন কিছুই করার ছিল না। জাকারিয়া সেদিন রাতে পৌঁছে ছিল তবে ঠিকানা বিভ্রাটে আমাদের খুঁজে না পেয়ে তার বন্ধুর বাড়িতেই রাত কাটিয়েছিল। কলকাতায় থাকাকালীন দ্বিতীয় দিনেই হাবিব পারিবারিক কারণে ঢাকায় ফিরে এল। এরপর সম্পূর্ণ সময় আমরা হাবিবের অনুপস্থিতি দারুণভাবে উপলব্ধি করেছি। আমাদের আড্ডা আর ভ্রমণের মধ্যমনি বরাবরই হাবিব। সাফাকও দ্বিতীয় দিনে ঢাকায় চলে এল। আর আমরা সকাল ৮টার দিকে বহরমপুর হয়ে মুর্শিদাবাদ এবং মালদার পথে রওয়ানা হলাম। কলকাতা হতে মালদা সরাসরি গেলে ৩০০ কি. মি.-এর বেশি যেহেতু আমরা বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ হয়ে যাব তাই দূরত্ব এবং সময় দুটোই বেশি লাগবে। তবে বহরমপুর মধ্যহ্নভোজের সময়েই পৌঁছব বলে আশা রাখি। সকালেই জাকারিয়া এসে যোগ দিলেন। কিছুক্ষণ পর জয়ন্ত গাড়ি নিয়ে হাজির। একটি মাইক্রোবাস। আটজন যাত্রী মালামাল সব নিয়ে রওয়ানা হলাম। মাইক্রোটি আহামরি কিছু নয়। লিকলিকে লম্বাটে ড্রাইভার। বয়সে তরুণ। প্রায় সড়কই তার চেনা। তবে আশপাশে চেনার কথা নয়। ড্রাইভারের নাম রাজু দেবনাথ মনে হলো জয়ন্তর পাড়ার বা পূর্ব পরিচিত। ছেলেটির মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। একেবারে ভাবলেশহীন মনে হলো। ড্রাইভার বাসটি চালায় মাত্র পরিষ্কার করা বা ধোয়ামোছা বোধ হয় বহুদিন করা হয়নি।
আমরা কলকাতা ছেড়েছি প্রায় একঘণ্টা। শহর থেকে বের হয়ে স্টেট রোড ধরে চলছি। দুই লেনের স্টেট হাইওয়ে বলে পরিচিত। আশপাশে গ্রাম্য বাড়িঘর বেশিরভাগই টালির চাল। বড় গ্রামগুলোর পাশে রাস্তার ধারে উন্মুক্ত বাজার। হরেক রকমের শাক-সবজি। তখনও শীতের মৌসুমের শাক-সবজি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। টমেটোসহ সব ধরনের সবজি, কাঁচা মরিচ, বেগুন অন্যান্য শাক। কলকাতায় যতবার এসেছি বাজারের শাক-সবজি দেখেছি কেমন যেনো শ্রীহীন-স্বাস্থ্যহীন মনে হয়েছে। গ্রাম্য বাজারেও তেমন দেখলাম। মনে হয় যে আমাদের দেশের শাক-সবজিগুলো বোধ হয় বেশি হাইব্রিড যে কারণে দেখতেই ভালো লাগে। পশ্চিম বাংলায় বোধ হয় তেমন হাইব্রিড সবজি চাষ হয় না।
কলকাতার বাইরের লোকালয়গুলো দেখলে মনে হয় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে এবং অর্থনৈতিকভাবে তেমন সচ্ছল নয়। ছোট ছোট শহর এমন কি কলকাতার বেশিরভাগ দালান- কোঠাগুলোতে, বিশেষ করে বসতবাড়িগুলোর নকশা দেখে মনে হয় পুরনো ধাঁচের নকশা করা বাড়িঘর। সহজে পরিবর্তন করা হয় না। ঢাকা বা ঢাকার বাইরের বহু জেলা শহরেও পুরনো ধরনের পাকা বসতবাড়ির দেখাও কম মিলে।
আমরা স্টেট রাস্তা ছেড়ে পোলট্র্রিপণ্ড নামক জায়গায় রেললাইন পার হয়ে কৃষ্ণনগরের হাইওয়েতে উঠলাম। ততক্ষণে সবাই ক্ষিদে অনুভব করছিলেন। তাছাড়া একটানা জনবহুল রাস্তায় গাড়ি চালানোতে আমরাও ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। কিন্তু সামনে এগুতে রাস্তার দু’পাশে প্রচুর মোটরসাইকেল আরোহী তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে জটলা দেখা গেল। যদিও রাস্তা চলাচলের জন্যে উন্মুক্ত তবু বেশ জটলা। তেমন কোনো উত্তেজনা বা হৃদয় কাঁপানো স্লোগান নেই। পেছন থেকে জয়ন্ত বললেন যে কয়েকদিন পর পঞ্চায়েত নির্বাচন আর এখন চলছে মনোনয়ন দাখিলের সময়।
ও-তাইতো মনে পড়ল আজ সকালেই খবরের কাগজে দেখলাম বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি)-এর অভিযোগ যে তাদের প্রার্থীরা বহু জায়গায় মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি কারণ তৃণমুলের ‘গুন্ডারা’ জমা দিতে দেয়নি। বিজেপি পশ্চিমবাংলার রাজ্যপালকে অভিযোগ করেছিল। রাজ্যপাল পশ্চিমবাংলার নির্বাচন কমিশনকেও তলব করে বলেছে কিন্তু তেমন কোনো কাজ হয়নি। পশ্চিমবাংলার বিজেপি বিষয়টি হাইকোর্টে উঠালে হাইকোর্ট এই বলে খারিজ করে দেয় যে বিষয়টি দেখার এখতিয়ার রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকারের। প্রসঙ্গত, ভারতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। এসব নির্বাচনে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো এখতিয়ার নেই। অবশ্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং যথেষ্ট স্বাধীন। স্বাধীন হলেও সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের সহযোগিতা ও আন্তরিকতার প্রয়োজন।
ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৩ কে এবং ২৪৩ কে-এর এ অনুযায়ী গঠিত এবং রাজ্যের সব স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা। এই ক্ষমতা দেয়া হয় সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯২ সালে নরসীমা রাও-এর সময়। রাজ্য নির্বাচন কমিশনকেও অনেক ক্ষমতা দেয়া আছে তবে রাজ্য সরকারের জনবল নিয়েই এসব নির্বাচন পরিচালনা করতে হয়। তবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে কারিগরি সহায়তার অনুরোধ অবশ্যই করা যায়।
আমরা নির্বাচনী ভিড় পার হয়ে জাতীয় মহাসড়কে উঠলাম। এনআই ৩৪। সবকটির কাজ এখনও শেষ হয়নি। রানাঘাট এবং ব্যারাকপুর পেছনে রেখে প্রায় আধাঘণ্টা পর আমরা কৃষ্ণনগরের হাইওয়ের পাশের বিখ্যাত এক উন্মুক্ত রেস্তোরাঁতে বলতে গেলে গণ-রেস্তোরাঁতে পৌঁছলাম। এই রেস্তোরাঁতে সমগ্র পশ্চিম বাংলায় কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত স্বরভাজার জন্যে বহুল পরিচিত। আমার মনে পড়ে এই রেস্তোরাঁটিতে ২০১১ সালে মুর্শিদাবাদে আসা-যাওয়ার পথে দুপুরের খাবার খেয়েছিলাম। তখন এত বড় ছিল না। বাঁশের অস্থায়ী স্থাপনা ছিল। এখন বিশাল বড় হয়েছে। পাকা উন্মুক্ত হল ঘরের মতো খাবারের জায়গাটি। টেবিল পাওয়াই দুষ্কর। পাশে আরও দুটি একই ধাঁচের রেস্তোরাঁ রয়েছে। ভাগাভাগি করে ব্যবসা করে। স্বরভাজার জন্যে এই রেস্তোরাঁর সুনাম অনেক বেশি। রেস্তোরাঁটির নাম শংকর মিষ্টান্ন ভান্ডার। আমরা নাস্তা করতে এখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটালাম। সময়ের অভাবে কৃষ্ণনগর শহরের ভিতরে প্রবেশ করা হয়নি। কৃষ্ণনগর অনেক পুরনো জনপদ। বর্তমানে নদীয়া জেলার সদর। তবে পুরনো জনপদ হলেও পৌরসভা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে ১৮৬৪ সালে। নদীয়া এ অঞ্চলের অন্যতম পুরনো পৌরসভার একটি। অনেকেই মনে করেন কৃষ্ণনগরের সবচাইতে ক্ষমতাধর ব্যক্তি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নামানুসারেই এই ছোট শহরের নাম রাখা হয়েছিল। আবার অনেকেই মনে করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামে। তবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজপ্রাসাদ এবং তার স্থাপিত স্কুল কলেজ এবং বহু বিদ্যাপীঠ ও জনহিতকর কাজের জন্যে তিনি অমর হয়েছেন। কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ ভারতবর্ষের প্রথমদিকের সরকারি কলেজ। কলেজটি স্থাপিত হয় ১৮৪৬ সালে। কৃষ্ণনগর এক সময় সর্ববাংলায় মাটির মূর্তির তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ। আজও রয়েছে তবে আগের মতো সেই রমরমা অবস্থা নেই। তবে এই অঞ্চলে বিভিন্ন জাতের মিষ্টির মান বেশভালই রয়েছে। স্বরভাজার কথাতো উল্লেখ করেছি। শংকরের স্বরভাজাই এ অঞ্চলের সবচাইতে সুস্বাদু বলে পরিচিতি।
দুপুরের আগেই আমাদের বহরমপুরে পৌঁছবার কথা। রাস্তার দু’পাশে বাংলার চিরায়ত সবুজ। ক্ষেতগুলো থেকে ধান বহু আগেই কাটা হয়ে গেছে। এখন বিভিন্ন প্রকারের রবি শষ্যে ক্ষেত সবুজ হয়ে আছে। কোথাও কোথাও সর্ষের ক্ষেত। হলুদ ফুলগুলোর উপর বাতাসের ছোয়ায় ঢেউ খেলছে। গ্রামগুলো বেশ দূরে। রাস্তার দু’ধারের গ্রামগুলো তুলনামূলকভাবে বর্ধিষ্ণু। এই ন্যাশনাল হাইওয়ে এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। বেশির ভাগ জায়গায় তৈরিরত রাস্তার ওপর দিয়েই যেতে হচ্ছে। কোথাও পুরনো রাস্তার ব্যবহার। দু’ঘণ্টা পর আমরা পলাশী বাইপাশে উঠলাম। জাকারিয়া বললেন পলাশী গেলে হতো না? আমি বললাম অবশ্যই হতো তবে আগেভাগে বললে হয়তো প্রোগ্রামের মধ্যে সমন্বয় করা যেত। আমরা পলাশী বাইপাস দিয়ে চললাম। পলাশী নামক ঐতিহাসিক এ গ্রামটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমনভাবে জড়িত যে পলাশী ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচিতই হতে পারে না।
আমরা প্রায় দুটোর কাছাকাছি সময়ে বহরমপুরে পৌঁছলাম। ছোট শহর বহরমপুর। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গরিব জেলা সদর। আমাদের থাকার জায়গা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের বহরমপুর গেস্ট হাউসে। সরকারি সংস্থা। যেমন হবার তেমনই। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার আগেই অভ্যর্থনা কেন্দ্র হতে জানালো যে সন্ধ্যায় মতিঝিল পার্কে ‘লাইট এন্ড সাউন্ড শো’ হয়। দুপুরে খাবার পর পর বের হয়ে গেলে কাশিমবাজার দেখে মতিঝিলে যেতে পারব। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো’ অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়। মাত্র কয়েক বছর আগেই এটা নতুন সংযোজন হয়েছে। মতিঝিল-কাশিমবাজার আমি আগেও গিয়েছি। মতিঝিলে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো-র জায়গা কোথায় ভাবছিলাম। কারণ মতিঝিল এর আগে যখন দেখেছি মোটামুটি পরিত্যক্তই দেখেছি। সিরাজের খালা ঘষেটি বেগমের প্রাসাদ ছিল ধ্বংসস্তূপে আর ঝিলটি ছিল অরক্ষিত। অবশ্য তখন শুনেছিলাম যে ঝিল সংস্কারের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে রাজ্য সরকার।
আমরা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। বরহমপুর বেশ পুরনো জনপদ। সিরাজের পতনের পর বহরমপুরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রভাব থেকে যায়। সিরাজ কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিল্কের সুতার কারখানা ধ্বংস করার পর বহরমপুর হয়ে উঠে বাজার। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর হতেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের সৈনিকদের জন্যে সেনা ছাউনি হিসেবে বহরমপুর গড়ে তোলে। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত বহরমপুর ছিল তৎকালীন ভারতের অন্যতম বৃহৎ সেনা ছাউনি। ১৮৭৬ সালে বহরমপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে এখানে সিপাহী বিল্পবীদের সঙ্গে কয়েক মাস যুদ্ধ চলে কোম্পানির অনুগত সৈনিকদের। বহরমপুরের অন্যতম পুরাতন কলেজ কৃষ্ণনাথ কলেজ। কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৩ সালে রাজা কৃষ্ণনাথের নামে। যিনি কোম্পানীর কৃপায় বহরমপুরের রাজা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।
ছোট শহর বহরমপুর। এখন বড় সেনা ছাউনি নেই তবে ওই জায়গায় বিএসএফের সদর দপ্তর রয়েছে। শহরের বাজারগুলো একেবারেই সাদামাটা। আধুনিক শহর হিসেবে যে রকম হবার কথা বহরমপুর তেমন নয়। তবে শীতের মৌসুমে অভ্যন্তরীণ এবং বেশ-বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা থাকে।

আমরা ভাগীরথীর তীর ধরে মতিঝিলের দিকে যাচ্ছি। পেছনে শমসের আর শাহাবুদ্দিন নিজেদের মধ্যেই কথা বলছেন। নাসরুল্লাহ নদীর নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি নদীর নাম বললাম। নদীর পাড়ের রাস্তাটিকে নতুনভাবে পুণর্নির্মিত মনে হলো। পূর্বপাড়ের এ রাস্তার পশ্চিমপাশে মানে নদীর দিকে গ্রিল দিয়ে ঘেরা। ২০১১ সালে এ রাস্তা এমন ছিল না। বেশ খারাপ অবস্থায় ছিল। আমরা নদীর পাড় ছেড়ে একটু ভিতরের দিকে এগিয়ে কাশিমবাজারের রাস্তায় প্রবেশ করলাম। যেহেতু আমি এ জায়গার সঙ্গে পরিচিত তাই আমাকেই গাইড হিসেবে কাজ করতে হলো (আমার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে ‘বাংলা-বিহার প্রান্তরে’ নামক ভ্রমণ কাহিনীতে)। কাশিমবাজারে প্রথমদিকে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিল্ক ব্যবসা ছিল। কিন্তু বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসার পর হতেই ‘ডাচ’রা চলে যায়। ওই সময়কার ডাচ কোম্পানির গভর্নরসহ যাদের মৃত্যু হয়েছিল তাদের সমাধিস্থান রয়েছে রাস্তার পাশেই। এটাই প্রথম ইউরোপিয়ান আঞ্চলিক কবরস্থান। এর কিছু দূরেই বৃটিশ কবরস্থান। এদের বেশির ভাগ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর এবং কলেরায় মৃত্যুবরণ করেছিল।
আমি কাশিমবাজার রাজবাড়ী দেখিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাশিমবাজারের সিল্ক সুতার কারখানার ধ্বংসস্তূপ সবাইকে দেখিয়ে মতিঝিল পার্কের দিকে রওয়ানা হলাম। এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট আগের তুলনায় অনেক ভাল হয়েছে। মমতা ব্যানার্জির সরকার মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে পর্যটন শিল্পকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয়। মুর্শিদাবাদের অন্যতম ঐতিহ্য সিল্ক। তাছাড়া কৃষিকাজ তো রয়েছেই। এ জেলার জনসংখ্যার প্রায় ২৪ ভাগ মুসলমান যাদের সিংহভাগের বাস মুর্শিদাবাদ শহরে।
বলছিলাম কাশিমবাজার-এর কথা। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাগীরথীর তীরে কাশিমবাজার ছিল বড়ধরনের বন্দর এবং এ অঞ্চলের সিল্ক ছিল বিশ্বখ্যাত। এখানে প্রথম ডাচরা সিল্কের ব্যবসায় জড়িত হলেও ক্রমেই বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামনে টিকতে পারেনি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ডাচরা চলে যাওয়ার পর বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করে। ঐতিহাসিক সূত্র মতে, কাশিমবাজারে কারখানা গড়ে উঠে ১৬৪৯ সালে। এর বাইরেও তৎকালীন হিন্দুস্থানের বহু জায়গায় আরও কারখানা গড়ে তোলে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এর মধ্যে হুগলি এবং কলকাতাতে ফ্যাক্টরি ছিল। সিরাজউদ্দোলার সঙ্গে বিবাদ বেঁধেছিল ট্যাক্স ধার্য করা নিয়ে। একপর্যায়ে নবাব এসব কারখানা দখল করে নিয়েছিলেন।
আমরা কাশিমবাজার ছেড়ে কিছুক্ষণের মধ্যে মতিঝিল পার্কের নির্ধারিত গাড়ি পার্কিংয়ে পৌঁছলাম। জয়ন্ত গেলেন পার্কে প্রবেশের টিকিট কিনতে। আমরা পাশের এক ছাপড়া দোকানে চায়ের জন্যে বসলাম। তখনও বিকেলের আলো ডুবেনি। সূর্য অস্তগামী হওয়ার আয়োজন শুরু করেছে। আমরা যেখানে বসেছি সেখান থেকে পার্কের গেট প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে। ছোট একটি গ্রাম্য জনবসতি। এখানে এই পার্কে যে প্রচুর লোক আসে তার প্রমাণ আশেপাশে প্রচুর ‘রাস্তার খাবারের’ দোকান। এগুলোর মধ্যে ফুচকা, চটপটি আর আইসক্রিম প্রধান। আমরা কয়েকজন দোকানের স্বল্পপরিসরে চেয়ারে বসা। সামনে রাস্তার অপর পাড়ে শমসের আর শাহাবুদ্দিন একটি বেঞ্চে বসে স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে গল্পে বিভোর। স্থানীয় লোকগুলো মুসলিম সম্প্রদায়ের। পরে শুনলাম এখানে প্রচুর মুসলমানদের বাস। শাহাবুদ্দিন বললেন, যে তাদের ভাষ্যমতে মমতা ব্যানার্জি ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখলেও পিছিয়ে পরা মুসলমান সংখ্যালঘুদের জন্যে প্রচুর কাজ করেছেন এবং করছেন। মুর্শিদাবাদকে পর্যটন নগরী তৈরি করার প্রয়াশে রয়েছেন। এর অন্যতম উদাহরণ মতিঝিল পার্ক।
মতিঝিল লেক কেটেছিলেন আলীবর্দী খানের জামাতা নওয়াজিশ উদ্দিন যিনি ঘষেটি বেগমকে বিয়ে করেছিলেন। এখানেই তিনি নিজের থাকার জন্যে প্রাসাদও তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র বলে চিহ্নিত করে সিরাজ এখানকার প্রাসাদও দখলে করে নেন। সেই থেকে এটি সিরাজের বাসস্থান হিসেবে পরিচিত। সিরাজের পতনের পর ক্লাইভ বাংলার দেওয়ানী না পাওয়া পর্যন্ত এটিকে বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এখানেই নওয়াজিশ উদ্দিনের সমাধি রয়েছে।
আমরা টিকিট দেখিয়ে নবনির্মিত মতিঝিল পার্কে প্রবেশ করলাম। মুর্শিদাবাদের এই পার্কটি পর্যটকদের জন্য অবশ্য দর্শনীয়। আমরা রাজকীয় ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। সোজা টানা পূর্ব-পশ্চিম রাস্তা। বাগানটি তিন ভাগে কয়েক একরের উপরে নির্মিত। সবুজ ঘাষের চত্বর। জায়গায়-জায়গায় বসার স্থান আর ময়লা ফেলার ঝুড়ি রয়েছে। বাহির হতে কোনো খাবার নিয়ে প্রবেশ নিষেধ একমাত্র পানি ছাড়া। পার্কের পশ্চিম মাথায় একেবারে শেষ প্রান্তে লাইট এন্ড সাউন্ড শো। এটাই সেই মতিঝিল অথচ বুঝবার উপায় নেই। শুধুমাত্র ব্যাটারি চালিত গাড়ি প্রায় দেড় কিলোমিটার লম্বা রাস্তাটিতে চলে। বাকি পথ হেঁটে যেতে হয়। এখানে রাত্রি যাপনের জন্যে মোটেল রয়েছে। রয়েছে ছোট রেস্তোরাঁ। হলরুম এবং গেটের কাছেই খাবারের দোকান। পার্কটিকে বাংলার নবাবী ইতিহাসের থিমপার্ক বলা যেতে পারে। শুধু সবুজ ঘাসই নয় বরং বহু অর্থের খরচে সবুজ গাছের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন সংস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এর রক্ষণাবেক্ষণ করে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন সংস্থা।
পার্কে প্রবেশের পর প্রথমেই হাতের বামে দেখা যাবে বাংলার দেওয়ান মুর্শিদাকুলি খাঁকে যার একটি প্রমাণ সাইজ ব্রোঞ্জের মূর্তি রয়েছে। বেদীর উপরে ছোট করে ইংরেজি-বাংলা আর হিন্দিতে মুর্শিদকুলি খাঁর পরিচিতি দেয়া হয়েছে।
মুর্শিদকুলি খাঁ গরিব ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণাঞ্চলের কোনো এক মোগল দরবারি তাকে খরিদ করে পড়ালেখা করিয়ে বড় করে তোলেন। পরে তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের নেক নজরে পরলে তাকে তৎকালীন মোগলবাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীরনগরে (বর্তমানের ঢাকায়) আওরঙ্গজেবের নাতি আজিম উস্-সান -এর অধীনে দেওয়ান বা খাজনা আদায়ের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং রাজকীয় কোষের জন্যে অর্থ ছাড় দেয়ার ক্ষমতাও দেয়া হয়। আজিম-উস্-সানের সঙ্গে ক্রমেই অর্থ বরাদ্দ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে সম্রাটের সম্মতিতে তিনি দেওয়ানি স্থানান্তরিত করে এককালের মকসুদপুর নামক গ্রামের নাম বদল করে রাখেন মুর্শিদাবাদ। আওরঙ্গজেবের পর ফররুখশিয়রের সময় তিনি নিজেকে বাংলার স্বাধীন নবাব হিসেবে ঘোষণা দেন এবং ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন।
মুর্শিদকুলি খাঁকে ছেড়ে পার্কের মাঝামাঝি আমরা। পেছনে এখানকার রেস্ট হাউস। উল্টোদিকে মাঠের মাঝে বসার জায়গায় মামু বসা। বললেন তিনি হেঁটে হেঁটে সামনে যেতে পারবেন না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। নাসরুল্লাহও বসে পরলেন। আমরা পাঁচজন হেঁটে-হেঁটে নবাব আলীবর্দী খানের মূর্তির সামনে দাঁড়ালাম। মুর্শিদকুলি খাঁর মতোই আলীবর্দী খাঁর ছোট পরিচিতি ও ইতিহাস লেখা। সেখান থেকে সামনের ফোয়ারার আগেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার মূর্তি। সেখানে ছোট ইতিহাস লেখা। পলাশীর যুদ্ধের উল্লেখ এবং বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা হারানোর বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা আরও কিছুদূর এগুতে জাকারিয়াকে পেলাম। তিনি আমাদের আগেই ছিলেন। এসে বললেন, সামনে পলাশীর যুদ্ধের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে অদ্ভুত সুন্দরভাবে।
সামনে আরও একশত মিটার যেখানে এ পার্কের শেষ সীমানা। সেখানেই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হওয়ার কথা। হাঁটতে হাঁটতে বললাম মমতা ব্যানার্জি ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন। মুর্শিদাবাদ এবং বাংলার নবাবদের কাহিনীর সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার বিপর্যস্ত জীবনকেও তুলে ধরেছেন। এখানেই মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে বর্তমান ভারতের অনেক নেতাদের তফাৎ। এই একটি জায়গা যেখানে ন্যূনতমপক্ষে ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা হাঁটতে-হাঁটতে পার্কের শেষ মাথায় পৌঁছলাম। ইতিমধ্যেই পার্কের বাতি জ্বলে উঠেছে। রং-বেরংয়ের বাতিতে পার্ক স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে।
আমরা ঝিলের কাছাকাছি। সামনে হাতি, ঘোড়া এবং পদাতিক বাহিনীর প্রমাণ সাইজের মূর্তির সমাহারে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পলাশী যাত্রার চিত্র ফুটে উঠেছে। তার একটু সামনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নৌবাহিনী কমান্ডার যার অত্যন্ত পটু যুদ্ধবিদ্যা এবং নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তেইশে জুন, ১৭৫৭ সালে মতিঝিল পার্ক থেকে প্রায় ৪০ কি. মি. দূরে পলাশীর আম্রকাননে স্বাধীন বাংলার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। এরপর সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজদের গোলামি করে ১৯০ বছর।
সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো শুরু হয়ে শেষ হলো ৮টায়। দেখানো হলো নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আর পলাশীর যুদ্ধের বিবরণ। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস তুলে ধরা হলো। এ রকম প্রতিকূল (গরম) আবহাওয়াতে অভ্যন্তরীণ পর্যটকের সংখ্যা কম ছিল না। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো শেষ করে বহরমপুরে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় দশটা। রাতের খাবার শেষ করে রুমে এলাম। আগামী দিন সকালে যৎসামান্য নাস্তা খেয়ে মুর্শিদাবাদ হয়ে মালদার পথে রওয়ানা হবো। মালদার পথে আমরা ফরাক্কা বাঁধের উপর দিয়ে যাব। প্রায় সমস্ত রাস্তাটিই আমাদেরকে অসমাপ্ত এনএইচ-৩০ দিয়ে যেতে হবে।
সকালে যৎসামান্য নাস্তা সেরে মুর্শিদাবাদের দিকে রওয়ানা হলাম। বহরমপুর থেকে প্রায় এক ঘণ্টার রাস্তা। আমরা ভাগীরথীর পূর্বপাড় ধরে যাচ্ছি। নদীর পাড়ে বেশ কয়েকটি ঘাট দেখলাম। ঘাটের সঙ্গে ছোট ছোট প্রার্থনাঘর। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি রাখা। এর আগে এতটা দেখিনি। ভাগীরথীকে পবিত্র নদী মনে করা হয় কারণ গঙ্গানদী বিধৌত এই ভাগীরথী। অনেক পুণ্যার্থীকে নদীতে ডুব দিয়ে পবিত্র হতে দেখলাম। এখানকার নদীর পানি বেশ পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ। রাস্তার পূর্ব-পাড় বেশির ভাগই কৃষি জমি। দূরে-দূরে কিছু বিাড়িঘর। মাঠে গরুর সংখ্যাই বেশি। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর আমরা মুর্শিদাবাদের পুরনো শহরের নবাবি দরবারের বড় গেট দিয়ে প্রবেশ করলাম। এখান থেকে মুর্শিদাবাদের পুরাতন নতুন শহরের শুরু। আমাদের চালকের তো কোনো জায়গাই চেনার কথা নয়। আমি একজন গাইড নেয়ার কথা বললাম। আমি আগে দু’বার এলেও সব জায়গাগুলো চিনতে পারব না। মুর্শিদাবাদ ঐতিহাসিক শহর। উপমহাদেশের ইতিহাসের মোড় যে কয়টি ঘটনায় বাঁক নিয়েছে তার সঙ্গেই মুর্শিদাবাদ এবং এখানে কবরস্থ মানুষগুলোর সম্পর্ক। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাতের জায়গা এই মুর্শিদাবাদ। আমি জাকারিয়াকে একটু মজা করে বললাম, আপনার বাড়িতো মুর্শিদাবাদ নবাবদের সঙ্গে জড়িত। আমাদের দায়দায়িত্ব এখন আপনার নেয়া উচিত? আপনিও নিশ্চয়ই মীরের রক্ত বহন করছেন। জাকারিয়া হাসলেন কোনো মন্তব্য করলেন না। প্রথম থেকেই নাসরুল্লাহ জাফরগঞ্জে মীর জাফরের কবর, হাজারদুয়ারি এবং তার সামনে ইমামবাড়া দেখার আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। বস্তুতপক্ষে আমাদের মুর্শিদাবাদ আসার প্রধান কারণই ছিল অনেকের অনুরোধ। আমি আর জাকারিয়া ছাড়া আর কারোরই মুর্শিদাবাদের অভিজ্ঞতা নেই।
আমরা গাইডের খোঁজে ব্যাটারিচালিত রিকশা স্ট্যান্ডে। এর ধারণক্ষমতা চারজনের। এটাও নতুন সংযোজন। কয়েকজন রিকশাচালক এবং এক্কাগাড়ির (এক ঘোড়ার গাড়ি) কয়েকজন চালক এসে গাইড তথা জায়গাগুলো ঘুরে দেখাবার কথা বলে দাম হাঁকলো। অবশেষ দুটো ব্যাটারিচালিত রিকশা বা হিউম্যানহলার নিলাম। যে কয়টি জায়গায় নিয়ে যাবে তার ফর্দ দেখলাম। পরে হাজারদুয়ারির সামনে এসে নামিয়ে দেবে। নদী পার হয়ে খোশবাগে সিরাজউদ্দৌলার এবং আলীবর্দী খাঁর কবরে যাওয়ার সময় হবে না বা যাবে না।
আমরা দু’ভাগ হয়ে উঠে বসলাম দুটো ব্যাটারিচালিত রিকশায়। হাজারদুয়ারির সামনে দিয়ে আমরা প্রথমে কাঠগোলা প্যালেস দেখতে গেলাম। আমি ভেতরে যাইনি। দুবারতো দেখেছি। আর তাছাড়া কাঠগোলা প্যালেস তেরি হয় ইংরেজদের আধিপত্য কায়েম হবার পর আলীবর্দীর খানের সময়। চারতলা প্যালেসটির সামনে বেশ বড় পুকুর রয়েছে যার চার কোণায় প্রহরী পোস্ট রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই জায়গাটির ইতিহাস বলে যে সিরাজ-উত্তর নবাবদের মনোরঞ্জনের অন্যতম জায়গা ছিল এই কাঠগোলা প্যালেস। এখানে বড় ধরনের গোলাপ বাগান ছিল তাই এ জায়গাকে কাঠগোলা বাগানও বলা হয়। এই প্যালেসের প্রথম কর্তা ছিলেন লক্ষ্মীপাত সিং ডোগার। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি এখানে যে বাগান গড়ে তোলেন এখানেই কালো গোলাপের চাষ হতো। ভিতরে একটি দর্শনীয় মন্দির রয়েছে যা পরেশ নাথ মন্দির বলে পরিচিত। এটি জৈনমন্দির। কারণ ডোগাররা ছিলেন জৈন। তাদের বংশধররা এখনও এ জায়গার মালিক।
যতদূর তথ্য পাওয়া যায়, ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের তিনদিন পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উইলিয়াম মি. ওয়াটস এবং ওয়ালস এখানে মীর জাফরের সঙ্গে দেনা-পাওনা নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। পলাশী যুদ্ধের আগেই নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে মীর জাফরকে নবাব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লিখিত মুচলেকা তৈরি করা হয়েছিল। পলাশী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে এবং মীর জাফরকে নবাব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎকালীন বাংলার অর্থের লুট হয়েছিল। আর এ লুটের ভাগ ওই সময়কার অনেক তথাকথিত জমিদাররাও নিয়েছিলেন।
আমরা কাঠগোলা প্যালেসের আম বাগানের কিছু অংশ দেখলাম। এ অঞ্চলে প্রচুর আম হয়। প্রবেশের পথেই আম বাগান। ডোগার (উড়মধৎ) কোনো জমিদার ছিলেন না। যোগার ছিলেন ব্যবসায়ী কিন্তু সিরাজ-উত্তর নবাবদের এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুনজরে থাকতে বহু কিছু করেছিলেন। কথিত আছে তিনি ওই সময়ের উত্তর ভারতের সবচাইতে সুন্দরী নর্তকীকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মনোরঞ্জনের জন্যে নিয়ে এসেছিলেন। ওই নর্তকীর কোমর ছিল ২২ ইঞ্চি। এখনও ওই সুন্দরীর একটি পেইন্টিং রয়েছে কাঠগোলা প্যালেসের দ্বিতীয়তলায়। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি ছাড়া বেশিরভাগ দর্শনীয় স্থানগুলো এখনও ব্যক্তি মালিকানাধীন। কাজেই পার্কে প্রবেশের টিকিট বাবদ যে অর্থ জোগাড় হয় তার বেশির ভাগই ব্যয় হয় এসব জায়গা রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে।
কাঠগোলা প্যালেস থেকে বের হয়ে আমরা রওয়ানা হলাম জাফরগঞ্জে মীরজাফরের বাড়ি আর পারিবারিক কবরস্থানের দিকে। নাসরুল্লাহ, তানভীর আর শমসেরের দেখার খুব শখ মীরজাফরের কবর। আমি বাইরে গাছের ছায়ায় বসে রইলাম। আমার দ্বিতীয়বার দেখার ইচ্ছা হলো না। সামনেই একটি মসজিদ যা এখন বন্ধ। এখানেই জানাজা পড়ানো হয় মীর জাফরের বংশধরদের। মীর জাফরের বংশধররা এখনও মুর্শিদাবাদ এবং ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এখানে পৌঁছবার আগে মীর জাফরের বাড়ির সামনে নেমেছিলাম। পুরনো হাভেলীটি নেই কিন্তু বিশাল আকারের গেটটি রয়েছে। বাড়ির অংশে এখন শিয়া ইমামবাড়া এবং সমস্ত জায়গাটি মীর জাফরের বংশধরদের নিজস্ব সম্পত্তি। গেটটি এবং এ অংশ স্থানীয়দের কাছে এবং মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে ‘নিমক হারাম দেউরী’ নামে পরিচিত। এখানেই কাছাকাছি কোথাও সিরাজউদ্দৌল্লাকে হত্যা করে তার দেহকে কয়েক টুকরো করে হাতিতে চড়িয়ে মুর্শিদাবাদ প্রদক্ষিণ করানো হয়। দেখানো হয় মা আমেনা বেগমকে। জানিনা নিমক হারাম দেউরী সাধারণ মানুষের মুখে শুনলে মীর জাফরের বংশধরদের মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়।
নিমক হারাম দেউরীর যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে উল্লেখ রয়েছে যে এখানে পলাশী যুদ্ধের আগে সিরাজ বিরোধী শেষ গোপন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন কাশিমবাজার কোম্পানির প্রধান উইলিয়াম ওয়ালস। ওয়ালস বাংলা এবং ফারসি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি এখানে মীর জাফরের মাথায় পবিত্র কোরান শরিফ এবং অপর হাত মীর জাফর পুত্র মীরনের মাথায় রেখে শপথ করিয়েছিলেন যে, পলাশীর যুদ্ধে জাফর সিরাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন এবং তার বদলে বাংলার মসনদে তার বংশধররাই থাকবেন। নিমক হারাম দেউরীর গেটটি আজও কালের এবং ভারত ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়ের সাক্ষী হিসেবে শ্রীহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।
নাসরুল্লাহ ফিরে এসে বললেন, দেখলাম এটা মীর জাফরের নাজাফি বংশের কবরস্থান। আমি বললাম, আর খোশবাগ ছিল আলীবর্দী খাঁর প্রতিষ্ঠিত আফসার বংশের। মীর জাফর ছিলেন আলীবর্দী খাঁর বোনের স্বামী। এই কবরস্থানটি ছিল মীর জাফরের বেগম প্রতিষ্ঠিত কিচেন গার্ডেন। খোশবাগে আলীবর্দী খাঁর বংশধররা শায়িত এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার (ASI) হাতে।
মুর্শিদাবাদ দেখতে এবং এর ইতিহাস উপলব্ধি করতে হলে ন্যূনতম পক্ষে দু’দিন সময় লাগার কথা। আমি আমার ভ্রমণ কাহিনী লেখা জন্য ইতিপূর্বে দু’বার এসেছি সে বিষয়ের উল্লেখ আগেই করেছি। তবে গত পাঁচ সাত বছরে মুর্শিদাবাদের রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আমার মনে হয় ঐতিহ্য আর ইতিহাস ধরে রাখতে হলে এএসআইকে (ASI) দায়িত্ব দেয়া উচিত। নিমক হারাম দেউরির প্রধান ফটকটি অবশ্যই সংরক্ষণ করা দরকার।
আমরা আরও এগুলাম। বাঁ দিকে দেবী সিং-এর প্রাসাদ যা অনেকটা হাজারদুয়ারির অনুরূপ তবে আকারে ছোট। এই প্রাসাদটি নাসিপুর রাজবাড়ি নামে পরিচিত। এই প্রাসাদ প্রথমে তৈরি করেছিলেন রাজা দেবী সিং। পরে বর্তমান আদলে পুনঃনির্মাণ করেন তারই বংশধর রাজা কীর্তিচন্দ্র সিং বাহাদুর ১৮৬৫ সালে। দেবী সিং পানিপথ অঞ্চল থেকে এখানে আসেন ব্যবসা করতে। পরে তিনি দেওয়ান রেজা খানের ট্যাক্স কালেক্টর হিসেবে যোগ দেন। পলাশী যুদ্ধের পরপরই দেবী সিং-এর উত্থান ঘটে। ওয়ারেন হেস্টিংস তাকে রাজা উপাধি দিয়ে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। তার ট্যাক্স সংগ্রহ অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছে। সাধারণ মানুষের নিকট দেবী সিং ছিলেন একজন অত্যাচারী লুটেরা। আজও তার বংশধররা কলকাতায় বসবাস করছেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন দেবী সিং-এর কারণে বাংলার বহু ধনাঢ্য কৃষক নিঃস্ব হয়ে যায়। পরে দুর্ভিক্ষের কারণও ছিল দেবী সিং এবং তার উত্তরসূরিদের অত্যাচার।
সময়ের অভাবে দেবী সিং-এর রাজবাড়ি দেখা হয়নি। দেবী সিং-এর প্রাসাদ ছেড়ে আমরা জগৎ শেঠের বাড়ির সামনে থামলাম। আমি আর শাহাবুদ্দিন ছাড়া বাকি সবাই টিকিট কেটে জগৎ শেঠের বাড়ি দেখতে প্রবেশ করলেন। আমি প্রথমবার এই বাড়িটি দেখতে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছিলাম। তাই দ্বিতীয়বার আর যেতে ইচ্ছা হয়নি।
জগৎ শেঠ সম্বন্ধে বেশি বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয় না। জগৎ শেঠের এ বাড়িটি তার আদি বাড়ি নয়। তার আদি বাড়ি ভাগিরথীর তীরে ছিল কিন্তু তা নদী ভাঙনের কারণে বিলীন হয়ে যায়। এখানকার এই বাড়িটি দোতলা তবে- মাটির নিচে একটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে ওখানেই ছিল টাকশাল। জগৎ শেঠ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী এবং অর্থ জোগান দাতা। চড়া সুদে অর্থ বিনিয়োগকারী। ওই সময় জগৎ শেঠ ছিলেন সবচেয়ে বড় ব্যাংকার। জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ এবং মীরজাফর সিরাজকে হটাবার ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা ছিলেন। জগৎ শেঠের বাড়িতে জগৎ শেঠ এবং তার পরবর্তী বংশধরদের ব্যবহৃত বহু বস্তু দর্শনার্থীদের জন্যে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।
প্রায় আধাঘণ্টা পর আমাদের দলটি বের হয়ে এল। এর পরের স্থান হাজারদুয়ারি প্যালেস। আমরা হাজারদুয়ারি প্যালেসে পৌঁছলাম। তখন বেলা প্রায় দশটা। বেশ কড়া রোদ। গরম হয়ে উঠেছিল আবহাওয়া। আমিসহ প্রায় চারজন পেছনে রয়ে গেলাম। কারণ আমরা সবাই আগে হাজারদুয়ারি প্যালেস দেখেছি।
অনেক পাঠক হয়তো ভুল করে মনে করতে পারেন যে হাজারদুয়ারি প্যালেসটির সাথে আলীবর্দী খান অথবা সিরাজউদ্দৌলা সম্পৃক্ত কিন্তু বিষয়টি মোটেও তা নয়। এ প্রাসাদটি তৈরি হয় নওয়াব নাজিম হুমায়ুন খাঁর সময়। নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ১৮২৯ সালে শেষ হয়েছিল প্রায় নয় বছর পর। ভাগীরথীর তীরে এই প্রাসাদ কমপ্লেক্স ‘কিলা নিজামত’ বলেও পরিচিত। এই প্রাসাদে ১০০০ দরজা রয়েছে সে কারণে এর নাম হাজারদুয়ারি। তবে এর মধ্যে ১০০ দরওয়াজা আসল নয়। দেখতে একই রকম দেখা যায়। এই বিশাল তিনতলা প্যালেসে ১১৪টি কক্ষ রয়েছে। এই প্রাসাদ চত্বরটি কয়েক শত একর জায়গা নিয়ে। দৃষ্টিনন্দন সবুজ চত্বর। মাঝখানে টাওয়ার ক্লক বসানো। তার অদূরে শুভ্র রংয়ের একটি ছোট মসজিদ যার নাম মক্কা মসজিদ। মসজিদটির ভিত তৈরি হয়েছিল সিরাজউদ্দৌলার সময়ে পবিত্র নগরী মক্কার মাটির সংমিশ্রণে। পরে মসজিদটির সংস্কার করা হয়। এই মসজিদটিই ভাগীরথীর এপারে একমাত্র স্থাপনা যা সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতি বহন করে। সিরাজের প্রাসাদটি ছিল কাঠের তৈরি যা নদীগর্ভে চলে গিয়েছে বলে কথিত। বাস্তবে পলাশীর পর মীরজাফর সিরাজের কোনো চিহ্নই রাখতে চায়নি। শুধুমাত্র খোসবাগই সিরাজ পরিবারের ইতিহাসকে ধারণ করে আছে। হাজারদুয়ারির অপরপ্রান্তে নিজাম ইমামবাড়া। এটি ভারতের বৃহৎত্তম শিয়া ইমামবাড়া বলে কথিত। এটি মহরমের দশদিন মাত্র খোলা থাকে। হাজারদুয়ারির প্রথমতলায় যেখানে নবাবদের দরবার ছিল সেখানে উঠতে সিঁড়ির দুপাশে দু’টি বৃহদাকারের কামান রয়েছে যেগুলোর নাম বাচ্চা তোপ। বলা হয়ে থাকে যে এগুলোর এমন আওয়াজ হতো যে অন্তঃসত্ত্বা নারীদের সন্তান প্রসব হয়ে যেত। তাই এর নাম রাখা হয়েছিল বাচ্চা তোপ। এই দু’টি কামান পরে মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন নদী পথে। তৃতীয় কামানটি উপরে উঠাবার সময়ে নদীতে পড়ে গিয়েছিল যা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা যে কয়েকজন আগে প্যালেসটি দেখেছি তারা এবার ভিতরে যাইনি। তবে বাইরেও গরমে বসতে পারলাম না। হাঁটতে হাঁটতে গাড়ি পার্কিং পার হয়ে একটি ছাপড়া দোকানে চা খেতে বসলাম। প্রায় একঘণ্টা পরে বাকিরা প্যালেসের ভিতরের জাদুঘরটি দেখে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তানভীর বললেন, সমগ্র প্যালেসে সিরাজের মাত্র একটি পেইন্টিং রয়েছে। আমি বললাম, ইতিহাসের পাতায়ও সিরাজের ওই একটি পেইন্টিং-এরই রিপ্রোডাকসন রয়েছে। তাছাড়া ইংরেজরা সিরাজকে নিয়ে তেমন আলোচনাও করেনি। সিরাজকে ইতিহাসে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ভিলেন হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছে।
মুর্শিদাবাদে সিরাজের তৈরি তেমন কোনো দর্শনীয় স্থাপনা না থাকলেও মুর্শিদকুলি খাঁ এবং আলীবর্দী খাঁর বহু নিদর্শন রয়েছে। কাটরা মসজিদটি ছিল মুর্শিদাবাদের সবচাইতে বড় দুর্গ মসজিদ। ওই মসজিদটির প্রধান প্রবেশ পথের সিঁড়ির নিচে বাংলার দেওয়ান নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ-এর কবর রয়েছে। তথ্যে প্রকাশ যে মুর্শিদকুলি খাঁ তার মৃত্যুর আগে এ রকম জায়গায় তাকে সমাধিস্থ করতে বলেছিলেন যাতে তার জীবনের পাপগুলো মুসল্লিদের নিচে থাকার কারণে কম হয়।
আমরা দুপুর সাড়ে এগারোটার দিকে মালদা-এর পথে মুর্শিদাবাদ ছাড়লাম। ভগবানগোলা পার হয়ে ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠবো। ভগবানগোলার পরেই মালদা জেলা শুরু। এ পথেই পার হতে হবে ফারাক্কা বাঁধ। রাস্তায় কোনো জায়গায় দুপুরের খাবার খেতে হবে। আমাদের যাবার পথে কাটরা মসজিদ পরলেও কেউই নেমে দেখতে চাইলেন না। সবারই উদ্দেশ্য সন্ধ্যার আগে মালদায় পৌঁছা।
মুর্শিদাবাদ হতে ভগবানগোলা মাত্র ১৮ কিলোমিটার। জায়গাটি মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ সাব-ডিভিশনে। এক সময়ের ছোট নদীবন্দর এখন অবশ্যই বেশ বড় হয়েছে। আঁকাবাকা রাস্তা। দু’পাশে বড় গ্রাম দেখা না গেলেও রাস্তার দু’ধারে জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট চায়ের আর মুদি দোকান। এক সময় ভগবান গোলা ভাগীরথীর তীরে নদীবন্দর ছিল। ভগবান গোলার কিছু উত্তর হতেই ভাগীরথী আর পদ্মা নদী দু’ভাগ হয়ে যায়। আমরা ভগবান গোলায় পৌঁছলাম। ছোটখাট বাজার এবং বড় ধরনের গ্রাম। এখানকার জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ ভাগ মুসলমান জনগোষ্ঠী। ১৯৪৭ সালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ খুলনা ভারতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। এর অন্যতম কারণ সে ক্ষেত্রে পদ্মা এবং ভাগীরথীর মিলনস্থল তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে থাকত। সে ক্ষেত্রে আজকের ফরাক্কা পশ্চিম বঙ্গের বাইরে রাজশাহী ডিভিশনে থাকত। ভগবানগোলা পার হতে কিছুটা সময় লাগল কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা রাস্তার পাশে ভিড় জমিয়েছে। অজস্র মোটর সাইকেল মোতায়েন ছিল। আজ এ অঞ্চলের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিল শুরু হয়েছে কাজেই সমর্থকদের ভিড়। এ দৃশ্য প্রায় আমাদের দেশের মতোই তবে প্রধান সড়কে যান চলাচল ধীরগতিতে হলেও থেমে নেই। ভগবানগোলা পার হলেই হাইওয়ে। সময় প্রায় একটা। দুপুরের খাবার সময় হয়ে গিয়েছে। হয়তো হাইওয়েতে কোনো ধাবা বা খাবার জায়গা পাওয়া যাবে। আরও প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে হাইওয়ে। ভগবানগোলা ছোট গ্রাম শহর হলেও ১৭৫৭ সালের জুন মাসের শেষের দিকে ছোট একটি গ্রাম ছিল নদীর পাড়ে। সিরাজ তার পরিবার নিয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্যে খাবারের খোঁজে এখানে তীরে নেমেছিলেন। এখানেই এক ফকিরের আস্তানা ছিল। ফকির দানা শাহ যাকে সিরাজ কান এবং নাকের মাথা কর্তন করে মুর্শিদাবাদ ছাড়া করেছিলেন। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে থাকা দানা শাহ সিরাজের জুতা দেখে চিনতে পেরে তাকে আটকে মীরজাফর পুত্র মীরনকে খবর দিলে তাকে গ্রেফতার করে। নিয়ে আসা হয় মুর্শিদাবাদে। ২রা জুলাই ১৭৫৭ সালে মীরনের হুকুমে সিরাজকে হত্যা করে মোহাম্মদী বেগ যাকে আলীবর্দী খাঁ রাস্তা হতে নিয়ে এসে পেলেছিলেন। মোহাম্মদী বেগ আর দানা শাহ বেশিদিন বেঁচে থাকেনি। তাদেরকেও হত্যা করা হয় এবং সমাধিস্থ করা হয় খোশবাগে সিরাজের কবরে যাবার রাস্তার ধারে।

ভগবানগোলা পার হয়ে আমরা আরেকটি স্টেট হাইওয়েতে উঠে লালগোলা পার হলাম। তখনও আমরা ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠিনি। আশপাশে তেমন খাবারের জায়গাও চোখে পরলো না। লালগোলা সীমান্ত শহরের অপর পারেই রাজশাহী ডিভিশন। এরপরে রঘুনাথগঞ্জ। এখানে ফারাক্কার একটি ফিডার ক্যানেলের উপর দিয়ে সুজনিপাড়া যাবার পথে ফারাক্কার প্রধান ফিডার ক্যানালটি পার হলাম। এই ফিডার (ক্যানাল) দিয়েই অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত ভাগীরথীতে যা কলকাতার আদিগঙ্গায় পৌঁছে। অবশেষে বল্লাপাড়ায় নির্মাণাধীন ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠলাম। একপাশে পদ্মা নদী যার মাঝখানে নতুন তৈরি করা আমবাগান। অপরদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে ফারাক্কার প্রধান ফিডার ক্যানাল। এখান থেকেই ফারাক্কার এলাকা শুরু। বাঁধটি এখনও প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে। সময় প্রায় তিনটা। পুরে পথে কোথাও খাবারের জায়গা চোখে পড়ল না। কিছূদূর এগুতেই রাস্তার পূর্ব পাশে একটু নিচু জায়গায় একটি দোতলা হোটেলের মতো মনে হলো। মনে হলো নিচ তলায় রেস্তোরাঁ। আশপাশে আর কোনো স্থাপনা নেই। দালানের সামনে দুটো গাড়ি দাঁড়ানো।
এ জায়গায় হাইওয়ে বেশ উঁচু। দু’পাশে নিচু কৃষি জমি। এ সময় শুধু কালাই-ই রয়েছে ক্ষেতে। আমরা কথিত হোটেলের সামনে এসে নামলাম। জনমানবের তেমন রা নেই। উপরে হোটেলের নাম ‘স্বপ্না হোটেল অ্যান্ড রেস্তোরাঁ’। শমসের খবর নিয়ে বললেন এখানে ভাত ডাল পাওয়া যাবে। খবর নিয়ে জানলাম খাবার প্রায় শেষ শুনেই মনে হলো খিদে আরও বাড়ল। বাইরে মুখ হাত ধুয়ে নিচের তলায় প্রবেশ করলাম। ভাত বেগুনভাজি আর ডাল রয়েছে। বাকি রয়েছে কয়েক টুকরা পার্শে মাছ। বাঙালি মালিকানায় হোটেলটি। উপর নিচ মিলিয়ে গোটা আটটি কক্ষ আর রেস্তোরাঁ। হোটেলে তেমন বোর্ডার আছে বলে মনে হলো না। সাকুল্যে দুজন মানুষ আর উপরে রান্নাঘরে হয়তো একজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই যা বাকি ছিল পরিবেশিত হলো। পেটে খিদে থাকলে সব খাদ্যই সুস্বাদু মনে হয়। খেলাম সবাই মিলে। বিল চুকিয়ে আমরা আবার উত্তরমুখী ফারাক্কার পথে। এসব হোটেল সস্তা বিশেষ করে ট্রাক ড্রাইভারদের থাকার জায়গা। রাস্তা ব্যস্ত হয়ে উঠল মালবাহী ট্রাকে। যাত্রীবাহী বাসের তেমন দেখা পেলাম না।
আমরা উত্তরমুখী ফারাক্কা হয়ে মালদার দিকে। আমাদের পূর্বে পদ্মা নদীর তীরের রাজশাহী আর পূর্বদিকে ফারাক্কার ফিডার ক্যানাল। মাঝখানে বিস্তীর্ণ কৃষি জমি। বিস্তৃীণ কৃষি জমির দিকে তাকিয়ে মনে করছিলাম মুর্শিদাবাদের কথা। বাংলার শেষ কথিত স্বাধীন রাজধানী- বাংলা বিহার আর ওড়িশ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। আর এখন চলছি কিছু সময়ের জন্যে স্বাধীন বাংলার প্রথম রাজধানী বলে পরিচিত গৌড়ের পথে। এই প্রোগ্রাম করবার পূর্বে কোনোদিন ভাবিনি যে একদার বাংলার রাজধানী গৌড় দেখতে যাব। আমরা গৌড়ের পথে। সামনে ফারাক্কার বাঁধ দিয়ে পদ্মা নদী পার হবার বিষয়ে বিশেষ সতর্কবাণী বিভিন্নস্থানে দৃশ্যমান রাখা হয়েছে।
হাইওয়েটি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হলে চার লেন এবং দু’পাশে সার্ভিস লেনও থাকবে। এ প্রকল্প কবে শেষ হবে তার সঠিক ধারণা পাওয়া যায়নি। এ রাস্তার জমি বরাদ্দ নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। জমি বরাদ্দ করতে দেরি হওয়াতে প্রকল্পটি ধীর গতিতে চলছে।
হাইওয়েটি এ জায়গাটায় বেশ উঁচু কারণ নদীর ধার হওয়াতে জায়গাটি এমনিতেই বেশ নিচু। এই মহাসড়কটিই উত্তরবঙ্গ হয়ে উত্তর পশ্চিমে পণ্য বহনের সহজ পথ। প্রতিদিন হাজার হাজার ট্রাক এ রাস্তা ব্যবহার করে। বিশেষ করে দূরপাল্লার ট্রাকগুলো রাতে যাতায়াত করে বেশি। বিকেল হতেই ট্রাকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। দিনের বেশিরভাগ সময় রাস্তার ধারে ট্রাকের বড় লাইন দেখা যায়। সময়টি বিশ্রাম নেয়ার। ভারতের ট্রাকের ড্রাইভার কেবিনগুলোতে শোয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণত দূরপাল্লার ট্রাকগুলোতে ড্রাইভার এবং সহকারি খাবার তৈরি করার জন্যে প্রয়োজনীয় তৈজশপত্র এবং কিছু বাজার করে রাখে। বেশিরভাগ ড্রাইভারের সহকারি পাচকের কাজ করে থাকে। এখানেও এমন ট্রাকের লাইন রয়েছে। ফারাক্কার দিকে যতই এগুচ্ছি ততই রাস্তায় ট্রাকের সংখ্যা বাড়ছে। প্রাইভেট গাড়ি এবং বাস রাস্তায় তেমন চোখে পড়েনি। ট্রেনই যাত্রীদের প্রধান বাহন।
২
আমরা মালদা হয়ে গৌড়ের পথে ফারাক্কার টোল প্লাজায়। গাড়ির বেশ বড় লাইন। বেশি সময় লাগল না টোল দিয়ে পার হতে। প্রায় এক কিলোমিটার পার হওয়ার পর ফারাক্কা দৃশ্যমান হলো। তেমন কোনো চেকপোস্ট নেই। গাড়ি আস্তে আস্তে চলছে কারণ সামনে বেশ কিছু ট্রাক। বাঁধের দক্ষিণ হতে উত্তরদিকে যাচ্ছি। পূর্বদিকে একটি রিজার্ভ পুলিশ আউট পোস্ট। কোনো সেন্ট্রিকেও ডিউটিরত দেখলাম না। মনে হলো নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ইলেকট্রনিক পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই রয়েছে। কারণ ফারাক্কা তৈরি নিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিরোধ ছিল। বিরোধ ছিল শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে পর্যাপ্ত পানির প্রবাহ নিয়ে। ফারাক্কা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বড় বিষয় হয়েছিল। পরে ১৯৬৬ সালে একচুক্তিতে পানি বণ্টনের পরিমাণ নির্ধারিত হলেও এখনও অভিযোগ রয়েছে যে সে পরিমাণ পানি পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের প্রায় সবার কাছেই ফারাক্কা দেখার অভিজ্ঞতা নতুন। আস্তে আস্তে বাঁধের উপর উঠলাম। পশ্চিম দিকে ফিডার ক্যানাল। পূর্বদিকে দৃশ্যমান হলো পদ্মা যা এখান হতেই বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশ করেছে। কিছুদূরে ভাগীরথীর মুখ যার সাথে ফিডার ক্যানাল যুক্ত।
ফারাক্কা মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর প্রান্তে বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার সীমান্ত হতে প্রায় ১৭ কিঃ মিঃ দূরে। গ্রামটি বা ছোট শহরটি একটি কমিউনিটি যেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে যাচ্ছে ব্লক সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে। ফারাক্কার অপর পার মালদা জেলা। মাঝখানে পদ্মা নদী। যেমনটা আগেই বলেছি ফারাক্কা ব্যারাজ তৈরি শুরু হয় ১৯৬১ সালে এবং শেষ হয় ১৯৭৫ সালে। এর দৈর্ঘ্য ২.২৪ কি. মি. এবং ফিডার ক্যানালটি ৪০ কি. মি. যার প্রবাহিত পানি ভাগীরথী এবং পরে কলকাতার হুগলী নদীর এবং হলদিয়া বন্দরের নাব্যতা রক্ষা করে।
আমরা ধীরে ধীরে বহুল আলোচিত ফারাক্কা বাঁধের উপরদিয়ে ধীর গতিতে যাচ্ছি। পশ্চিম দিকে রেলওয়ে লাইন। পূর্বদিকে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্যে পিলার। বাঁধের পশ্চিমপ্রান্তে অর্থাৎ নদীর পানি যেদিক হতে প্রবাহিত হচ্ছে সেদিকে ১০৮টি গেট এবং আরেকটি মালদা প্রান্তের নিম্ন অঞ্চলে। মোট ১০৯টি গেট। মুর্শিদাবাদ প্রান্তে ফারাক্কা সুপার থরমাল পাওয়ার স্টেশন। এটি কয়লাচালিত পাওয়ার প্লান্ট। প্রায় ২১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম এই পাওয়ার প্লান্ট।
আমরা ফারাক্কা পার হচ্ছি। মনে পরে স্কুলের ছাত্র হিসেবে এই ফারাক্কা নিয়ে বিবাদের কথা শুনেছি, পত্রিকায় পড়েছি। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে তৈরি শেষ হবার পর পানির ভাগাভাগি নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেকখানি শীতল হয়েছিল। এরপর এই বিষয়টি বাংলাদেশ জাতিসংঘেও তুলেছিল। অবশেষে ১৯৯৬ সালে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল তবে সিন্ধু নদের পানির ভাগাভাগি চুক্তির মতো এই চুক্তিতে কোনো আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি নেই।
দেখলাম ফারাক্কার বাঁধের মাত্র দু’টি গেট খোলা যেখান দিয়ে কিছু পানি পদ্মা নদীতে প্রবাহিত হচ্ছে। পূর্বপাশের নদীটি যা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, পানি খুবই কম। নদীতে দু-একটি ছোট পালের নৌকা দেখলাম যা সচরাচর আমাদের দিকের পদ্মায় দেখা যায় না। খুব একটা মাছ আছে বলে মনে হয় না এবং থাকার কথাও নয়। এক সময় বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশের কত গল্প শুনেছি। এখন আর পদ্মায় ইলিশ নেই বললেই চলে অথচ পদ্মার ইলিশ নামে বাজার গরম হয়ে উঠে। এক সময়ের সবচাইতে সস্তা মাছের অন্যতম ইলিশ এখন সবচাইতে দামি মাছের একটি।
বৈশাখে বাংলাদেশের নতুন ফ্যাশন উচ্চ মধ্যবিত্তদের একদিনের বাঙালি হয়ে উঠা শানকিতে পান্তাভাত আর ইলিশ ভাজা খাওয়া। এক প্লেট পান্তা-ইলিশের দাম কয়েক হাজার টাকাও হতে পারে। পয়লা বৈশাখের আগে ইলিশ মাছের বাজার আগুন হয়ে উঠে। আমার শৈশবে এই ইলিশ মাছের হালি চার হতে ছয় আনায় বিক্রি হতে দেখেছি। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ইলিশ মাছ ফেলে দিতে দেখেছি কারণ ইলিশ মাছে পচন ধরে খুব তাড়াতাড়ি। আর এই পচা ইলিশ ওই সময় ওলাউঠা বা কলেরার অন্যতম উপসর্গ হতো। এখনতো সেই অবস্থা নেই। বাজারের ইলিশ ন্যূনতম পক্ষে একবছর পুরাতনতো হবেই। এখন তো পচনের সময়ই নেই। ইলিশ ধরার আধাঘণ্টার মধ্যে বরফে ঢুকে পরে ফ্রিজার ট্রলারে ঢাকায় আসে অথবা বড় আড়ৎদারের কোল্ড স্টোরে চলে যায়। আসল ইলিশের স্বাদতো পাওয়াই যায় না। আর ফরমালিন সে প্রসঙ্গ না আনাই ভালো।
ফারাক্কা বাঁধের উপরের রাস্তাটির অবস্থা তেমন সুবিধার নয়। বেশ এবারোখেবরো অনেকদিন সংস্কার হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রচুর ভিড় মালবাহী ট্রাক চলাচল করার কারণে খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা খারাপ হয়। পশ্চিমপাশের অংশের নদীতে পানি ধরে রাখার কারণে পানি ভরপুর। ফিডার ক্যানালের মুখে বেশ কয়েকটি স্লুইস গেট যার মাধ্যমে ভাগীরথী আর হুগলীর পানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে পশ্চিমের নদীর অংশটিই গঙ্গা নামে পরিচিত যা আমাদের দেশে প্রবেশের পর পদ্মা নাম ধারণ করে।
আমরা ফারাক্কা পার হলাম। সূর্য পশ্চিম দিকে নামতে শুরু করেছে। ক্রমেই রাস্তায় ট্রাকের ভিড় বাড়তে শুরু হয়েছে। যে সব ট্রাক এ পাড়ে সারা দিন অপেক্ষা করছিল সেগুলো পুণরায় যাত্রা শুরু করাতে ক্রমেই হাইওয়েতে যানজট শুরু হয়েছে। আমরা এখন আমের জন্যে বিখ্যাত মালদা জেলায় প্রবেশ করেছি। পশ্চিম পাশে সরকারি কলোনি জায়গাটির নাম জগন্নাথপুর। আধাঘণ্টা পর মালদা অঞ্চলের সবচাইতে বড় বিএসএফ ছাউনি চোখে পড়লো। এটাই রাজশাহী অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত বিএসএফ ব্যাটালিয়ন।
আমরা যখন মালদা শহরের কাছাকাছি জায়গায় জাদুপুরের কাছাকাছি সেখান থেকেই শুরু হলো ভয়াবহ যানজট। মালদা শহরের মুখে প্রবেশ করতে করতে প্রায় সাতটা বেজে গেছে। তখনও আমরা হোটেলের ধারে-কাছে নেই। মালদা বাইপাস তৈরি শেষ না হওয়ার জন্য শহরের মধ্য দিয়ে উত্তরাঞ্চলে যাবার সমস্ত ট্রাক যাতায়াত করে ফলে শহরে বিকেল হতেই ভয়াবহ যানজট শুরু হয়। শহরের বাস, ট্রাক এবং ইজি বাইক রিকশা সবই চলে একই রাস্তায়। শহরের যতটুকু এ পর্যন্ত দেখলাম তাতে খুব একটা আনন্দিত হতে পারলাম না। ঘনবসতির শহর মনে হলো। দোকান-পাট বাড়ি-ঘরগুলোর চেহারা যে খুব উজ্জ্বল তেমন মনে হয়নি। শহরটি পরিষ্কার তেমন বলাও যায় না। অপর পাড়ে রাজশাহী শহরের তুলনায় শহরটি ময়লা এবং ঘিঞ্জি। মালদাতে আমরা আজ এবং কাল দু’রাত থাকব। আমাদের জন্যে জয়ন্তর মাধ্যমে প্রধান সড়কের উপরে কলিঙ্গ নামক হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জয়ন্ত বললেন হোটেলটি দুই তারকা। দুই তারকা আর তিন তারকা এ ধরনের শহরে তারকা হোটেল থাকার কথা নয়। শীতের সময় অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের আনাগোনা বেশি। তবে মাঝে-মধ্যে বিদেশী পর্যটকদেরও দেখা যায়।
আমরা বহু কষ্টে রথখোলা মোড় নামক জায়গায় পৌঁছলাম। এখান থেকে দুটো রাস্তা দু’দিকে গিয়েছে। জয়ন্তও এখানে আগে তেমন আসেনি। হোটেলে ফোন করলে পথনির্দেশনা দিল। জানালো যে সুকান্ত মোড় পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, সেখান হতে ইউটার্ন নিয়ে অপর পাশে এলেই কলিঙ্গ হোটেল পাওয়া যাবে। তার পাশেই চানক্য হোটেল। আর দুই কিলোমিটার যেতে হবে। এতক্ষণে মনে হচ্ছিল যে এ রাস্তা বোধ হয় শেষ হওয়ার নয়। ন্যূনতম পক্ষে আরও একঘণ্টা গাড়িতে থাকতে হবে। দুপুরের পরে আর কোথাও আমরা যাত্রা বিরতি করিনি বা করার জায়গাও পাওয়া যায়নি।
মালদা শহরের জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। দু’টি পৌরসভা সদর এবং ইংলিশ বাজার। ইংলিশ বাজারই পুরনো শহর এবং এখানেই জেলা সদর অবস্থিত। এগারোটি পুলিশ স্টেশনে বিভক্ত শহর। এখানে অন্যান্য বিদ্যাপীঠসহ একটি মেডিকেল কলেজ আছে।
মহানন্দা আর কালিঙ্গি নদীদ্বারা বিধৌত মালদা শহর। মালদা পুরনো জনপদ। এক সময় বাংলার দু’টি রাজধানী ছিল এই অঞ্চলে। এর একটি গৌড় অপরটি পান্ডুয়া। এই দুটো জায়গা কে কেন্দ্র করেই উনিশ শতকের দিকে মালদা আধুনিক শহর গড়ে উঠেছে। এই জেলা আমের জন্যে বিখ্যাত বিশেষ করে মালদার ফজলি আম ভারতবর্ষ জুড়েই বিখ্যাত।
প্রকৃতপক্ষে জেলা শহরটি চলতি ভাষায় মালদা বলে পরিচিত হলে জেলার সদর ইংলিশ বাজারে। এটা ডিভিশন সদরও বটে। এ জেলাটি সংগঠিত হয় পুরনিয়া দিনাজপুর, রাজশাহী অঞ্চল নিয়ে ১৮১৩ সালে। ১৮৩২ সালে আলাদা ট্রেজারি এবং ১৮৫৯ সালে আলাদা ম্যাজিট্রেসি গঠিত হয়। ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত মালদা রাজশাহী ডিভিশনের অন্তর্গত ছিল। পরে ১৮৭৬ সালের পর হতে ১৯০৫ পর্যন্ত ভাগলপুর ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এরপর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পুনরায় রাজশাহী ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আগস্ট ১৯৪৭ এই জেলার অবস্থান অনিশ্চিত ছিল। আগস্ট ১২ হতে ১৫ পর্যন্ত এই জেলার অবস্থান ছিল অনিশ্চিত কারণ স্যার রেডক্লিফের ঘোষণায় এ জেলার অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। এ কয়দিন জেলাটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একজন ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ছিল। অবশেষে ১৭ আগস্ট ১৯৪৭ সালে মালদা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়।
মালদা মেট্রোপলিটন শহর ৮১ বর্গ কিঃ মিঃ বিস্তৃত। ২০১১ সালের শুমারি মোতাবেক শহরের জনসংখ্যা ছিল তিন লাখ পঁচিশ হাজার। জনসংখ্যার এক হাজারের মধ্যে নারীদের সংখ্যা ৮৭৭ জন। শিক্ষার হার শতকরা ৮৫ ভাগ।
সময় প্রায় ৮টা আমরা এখনও হোটেলে পৌঁছিনি যদিও হোটেলটি দৃষ্টি সীমার মধ্যেই। এতক্ষণ যানজটের মধ্যে থেকে শমসের আর বসে থাকতে পারলো না। শমসের আর জয়ন্ত নেমে গিয়ে হেঁটেই হোটেলে পৌঁছল। আমরা আর আধাঘণ্টা পর সুকান্ত চত্বর হতে ইউটার্ন নিয়ে যখন হোটেলের সামনে পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। পশ্চিমপাশের রাস্তায় ভয়াবহ যানজট। হোটেলে কক্ষে পৌঁছে খাবার রেস্তোরাঁতে যেতে যেতে প্রায় সাড়ে নয়টা। আমি আর তানভীর এক রুমেই ছিলাম দুই রাত। রাতের খাবারের অর্ডার আগেই দেয়া হয়েছিল যা জয়ন্ত কলকাতা থেকেই ব্যবস্থা করেছিল। ডাইনিং রুমেই সকালের প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করা হলো। আমাদের সবার জন্যেই গৌড় দেখার প্রথম অভিজ্ঞতা হবে। কেউই-এর আগে গৌড়-এর সাথে তেমন পরিচিতও ছিলাম না। ড্রাইভার সমেত কেউই গৌড়ের রাস্তাও চেনার কথা নয়। কাজেই জায়গায়-জায়গায় জিজ্ঞাসা করে যেতে হবে।
পরদিন সকাল নয়টার মধ্যে নাস্তা শেষ করে আমরা গাড়ি নিয়ে বের হবার আগে রিসিপশনে গৌড় যাবার মোটামুটি রাস্তার ধারণা নিয়ে বের হয়েছিলাম। তবে যা আমরা করতে পারিনি; উচিত ছিল একজন অভিজ্ঞ গাইড নেয়া। যদিও গাইড পাওয়া যেতো কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। হয়তো গৌড় গিয়ে পেতে পারি।
আমরা সকাল নয়টার দিকেই রওয়ানা হলাম। দক্ষিণমুখো হতে হলো। তার মানে গতকাল আমরা গৌড় দক্ষিণে রেখে উত্তরে হোটেলে এসেছিলাম। এখান হতে প্রায় এক ঘণ্টার রাস্তা। আমরা শহরের বাইরে এসে মুসস্থানী মোড় ছেড়ে দক্ষিণ পূর্বদিকের দুমুখো রাস্তা ধরলাম। দু’পাশে ধানের ক্ষেত আর ছোট ছোট আম বাগান। রাস্তার একধারে প্রায় ১ কিলোমিটার লম্বা ট্রাকের লাইন। এগুলো চাঁপাই নবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ বন্দরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। সোজা গেলেই ছোট সোনা মসজিদ আর বাংলাদেশের সীমান্ত। ওই সীমান্ত চৌকিতেও রয়েছে গৌড়ের আরেকটি গেট বা আলাই দরওয়াজা যার ঐতিহাসিক নাম কোতোয়ালী দরওয়াজা। রয়েছে ছোট সোনা মসজিদ এবং মোগল রাজপুত্র আওরঙ্গজেবের ভাই এবং বাংলার সুবেদার শাহ সুজার তোষাখানা। এই পুরো অঞ্চলটিই ছিল এক সময়কার লক্ষণাবতী ও পরে গৌড়। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আগ পর্যন্ত গৌড় গড়ে উঠেছিল বাংলার রাজধানী হিসেবে। কখনও তথাকথিত স্বাধীন এবং বেশি সময়ই দিল্লির শাসকদের অধীন। সে অর্থে বাংলা কখনও স্বাধীন ছিল কিনা তা নিয়ে ইতিহাসে বিতর্ক রয়েছে।
আমরা ট্রাকগুলো পার হয়ে যাওয়ার সময় দিক-নির্দেশনা নিলাম। এবার পশ্চিমদিকের রাস্তা ধরলাম। সরু রাস্তা। এ ধারে জনবসতি কম। বাড়িঘরগুলোর যে চেহারা ফুটে উঠেছে তাতে মনে হয় এলাকাটি বেশ গরিব। মাঠে-ঘাটে কৃষিকাজ এবং আম বাগানে কাজ করাই প্রধান উপার্জনের উৎস। রামকেলী নামক গ্রামের পাড়ে একজনকে পেয়ে নাসরুল্লা গৌড় নামক জায়গার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক এমনভাবে তাকালেন যেন এই নাম জীবনেও শুনেননি। সামনে দেখিয়ে বললেন যে সামনে বাদল্ল্যাবাড়ীর কাছে বেশ পুরনো জায়গা রয়েছে। আমরা আরও কিছুদূর এগুলাম। আমার মনে হলো যে আমরা সঠিক জায়গা যাচ্ছি। আরেকটু এগুতেই একটি পুকুর এবং দু’একটি বাড়ি পার হতেই একটি বড় ঘেরাও দেয়া বহু পুরনো স্থাপনা পেলাম। এখানে আমরা থামিনি কারণ সামনেই গৌড়ের বিখ্যাত প্রবেশপথের আলাই দরওয়াজা বা তোড়ন।
আমি ভেবেছিলাম গৌড়ের এই বিস্তীর্ণ এলাকা দেখার জন্যে এবং দেখাবার জন্যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার (এএসআই) কোনো অফিস থাকবে। সেখানে হয়তো কোনো গাইড ম্যাপ পাওয়া যাবে। তেমন মনে হলো না বা পেলামও না। আমরা আলাই দরওয়াজা দেখে প্রথমে সেখানেই নামলাম। জায়গাটি পরিপাটি করে রাখা। গেটটি দেয়াল বেষ্টিত গৌড়ের প্রধান ফটক। এক সময় সমগ্র শহরটি দেয়াল ঘেরা ছিল। এখনও সে দেয়ালের বহু অংশ দৃশ্যমান।
আমরা নেমে পড়লাম। গেটটি খুলে বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করলাম। এই প্রথম গৌড়ের একটি স্থাপনার সামনে দাঁড়ালাম। ঐতিহাসিক এই রাজধানী শহরটি দৈর্ঘ্যে ৭-৮ কি. মি. এবং প্রস্থে ২ কি. মি. ছিল বলে তথ্যে প্রকাশ। স্থাপিত হয়েছিল অষ্টম শতাব্দিতে এবং ষোড়শ শতাব্দিতে শহরটি রাজধানীর মর্যাদা হারায়। গৌড়ের আদি নাম ছিল লক্ষণাবতী। মনে করা হয় লক্ষণ সেনের নামে এর নামকরণ। লক্ষণ সেন ছিলেন সেন রাজবংশের। যাদের পূর্ব পুরুষরা এসেছিলেন দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকা অঞ্চল থেকে। এই রাজবংশের গোড়াপত্তন করেছিলেন সামন্ত সেন পরে এদেরই রাজবংশের বল্লাল সেন গৌড় দখল করেন। সেন বংশ শুধু বাংলাতেই নয় ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণের বহু অঞ্চলজুড়ে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। লক্ষণ সেন বল্লাল সেনের উত্তরসূরি হিসেবে প্রায় ২০ বছর বাংলা স্থানান্তর করেছিলেন। লক্ষণ সেন শুধু বাংলা নয় বিহার-আসাম এবং ওড়িশ্যা পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। লক্ষণ সেনের রাজগুরু উপদেশ দেয়াতে লক্ষণ সেন দিল্লির আক্রমণ ঠেকাতে রাজধানী নবদ্বীপ-এ নিয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে দিল্লির তুর্কি বংশোদ্ভূত জেনারেল ১২০৪ সালে লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলাকে দিল্লির সুলতানদের অধীনে নিয়ে আসেন।
আমরা দাখিল বা সালামী দরওয়াজা বলে পরিচিত গৌড়ের এককালের প্রধান গেটের চত্বরে প্রবেশ করলাম। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, এর নাম ছিল নীম দরওয়াজা। কিন্তু এএসআই-এর ফলকে লেখা সালামি দরওয়াজা। অনেকটা মোগলদের দরজা বা গেটগুলোর মতোই এর গড়ন। স্থানীয় নকশার সঙ্গে সংমিশ্রণ হয়েছে মধ্য এশিয়া এবং তুর্কি স্থাপত্যের। সমগ্র মধ্যযুগে এবং মোগলদের স্থাপনায় প্রায় একই ধরনের স্থাপত্য দেখা যায়। দাখিল দরওয়াজা তৈরি হয়েছিল ১৪৫৯-৭৪ সালে বাংলার সুলতানি আমলে। এর উচ্চতা ২১ মিটার এবং ৩৪.৫ মিটার প্রস্থ। চার ঘোড়া পাশাপাশি প্রবেশের মত বড় দরওয়াজা। দরওয়াজার দু’ধারে কামান বসাবার জায়গা যার দ্বারা আগত শাহী অতিথিদের স্বাগত জানানো হতো। দরওয়াজার দু’ধারে রক্ষার জন্য সৈনিকদের বাসস্থান ছিল। এই দরওয়াজাটি বানিয়েছিলেন সুলতান বারবাক শাহ।
দাখিল দরওয়াজার ভিতরে প্রবেশ করতেই দু’জন স্থানীয় লোককে বসা দেখলাম। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম তারা এখানে কি করছেন। বললেন যে তারা এএসআইর কর্মচারী। এ জায়গার রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত। যেহেতু এখানকার সব স্থাপনাগুলো ঐতিহাসিক সংরক্ষিত স্থান তাই তাদের নিয়োগ। জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কোনো তথ্য কেন্দ্র রয়েছে কিনা? তারা বললেন নেই। তবে এ রাস্তা ধরে এগুলেই সব দর্শনীয় স্থানগুলো পাওয়া যাবে। এবং রাস্তার উপরেই প্রত্যেকটি স্থানের দিক-নির্দেশনা দেয়া রয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছি যে জায়গাটি আমরা ছেড়ে এসেছি সেটা কোন স্থাপনা। একজন বললেন, বাবু ওটা বড় সোনা মসজিদ নামে পরিচিত। আর একটু সামনে গেলেই পাবেন ‘ফিরোজ’ মিনার। ওখান হতে বাকি সব জায়গার দিক-নির্দেশনা দেয়া রয়েছে।
দাখিল দরওয়াজা তো রীতিমত অট্টালিকা। এর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত ন্যূনতম পক্ষে ২৫ গজ হবে। অপর পাশে সবুজ চত্বরের অপরপ্রান্তে আম বাগান। এখনও আম বড় হয়নি। অনেক গাছে মুকুল হতে আম বের হচ্ছে মাত্র। এগুলো সবই ফজলি আম। দর্শনার্থী আসুক বা নাই আসুক নির্ধারিত ব্যক্তিদের জায়গা পরিস্কার রাখার ব্যাপারে কোনো গাফিলতি দেখিনি। আমি তাদের একজনকে আমাদের পথ নির্দেশক হিসেবে নিতে চাইলাম কিন্তু রাজি হলো না। কারণ তাদের কর্মস্থল ছাড়া নিষেধ। সুপারভাইজার জানলে তাদের চাকরি থাকবে না। জিজ্ঞাসা করলাম কখন এখানে বেশি লোক আসে? জানালেন যে শীত মৌসুমে বহু লোক এসব জায়গা দেখতে আসে এবং অনেক পিকনিক পার্টিও এখানে আসে।
আমরা বেশ কিছুক্ষণ অনেকগুলো ছবি উঠিয়ে রাস্তার ধরে দক্ষিণ পূর্বমুখে রওয়ানা হলাম। আমরা এখন গৌড়ের ভিতরে। তবে এ অঞ্চলের নাম এখন আর গৌড় নেই।
গৌড় রাজধানী না হলেও সেন বংশের পূর্বে এ অঞ্চল পাল বংশের রাজত্বের অংশ ছিল। যদিও পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায় না তবে ভাপাইদা নামক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র যোদ্ধার পুত্র গোপালকে এ অঞ্চলের রাজা নির্বাচন করা হয়েছিল। সময়কাল ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ, শশাঙ্ক ও শক রাজত্ব শেষ হবার পর।
গোপাল এবং পাল বংশের বাংলা বিহার অঞ্চলের রাজা হওয়া নিয়ে একাধিক কিংবদন্তি রয়েছে। শশাঙ্কের রাজত্ব শেষ হওয়ার পর বাংলা অঞ্চল এক অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল। কিংবদন্তি আছে এ অঞ্চলে রাজা হলেই নাগরানীর মোহে পড়ে মৃত্যুবরণ করতো। অবশেষে গোপালকে নির্বাচন করা হয়। গোপাল নাগরানীকে বধ করে রাজত্ব কায়েম করেন। ওই সময়ে গৌড়সহ এ রাজত্বের পরিধি যথেষ্ট বড় ছিল। তবে গোপালকে নির্বাচিত করা হয়েছিল ওই সময়কার জমিদার এবং প্রভাবশালীদের দ্বারা। পালদের শাসনকাল বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্যে ছিল। পাল বংশের পতনের মধ্যে দিয়ে সেন বংশের অভ্যুদয় হয়।
আমরা পাকা রাস্তা ধরে প্রায় অন্ধের মতো দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলাম। এখানে খুব বেশি মানুষের বাস তেমন মনে হয়নি। কারণ তেমন বড় গ্রাম বা জনসংখ্যা চোখে পড়েনি। রাস্তাটি দেখে মনে হলো সার্কুলার রাস্তার মতো। বেশ ভাল অবস্থায় রাস্তাটি রয়েছে। এ রাস্তায় হয়তো গাড়ি ঘোড়ার যাতায়াত কম। এ অঞ্চলে বেশ পুরাতন এবং বড় ধরনের পুকুর চোখে পড়ল। আর আম গাছের অভাব নেই। ছোট বড় নতুন পুরাতন আম গাছে ভরপুর। যেতে যেতে জাকারিয়া বললেন, গৌড় পর্যন্ত কোনোদিন আসা হবে ভাবিনি। তাছাড়া এখানে এত দেখার আছে তাও জানতাম না। শুধু শুনেছি মধ্যযুগের বা তারও আগের বাংলার রাজধানী গৌড়। নাসরুল্লা বললেন, এখানে আসার পরিকল্পনার সকল কৃতিত্ব সাখাওয়াত ভাইয়ের আর ব্যবস্থাপনার জন্যে হাবিব ভাইকে যতই ধন্যবাদ দেয়া হোক তা কমই হবে। অন্যরা সবাই এক বাক্যে দুটো বক্তব্য সমর্থন করলেন।
আমরা দাখিলি দরওয়াজা হতে এক কিলোমিটার পার হতেই রাস্তার পশ্চিম পাশে বড় একটি দীঘি দেখলাম। সেখানে বেশ কিছু লোক মাছের পোনা জাল দিয়ে ধরে এলুমিনিয়ামের বড় বড় ডেকচির মধ্যে রাখছে অন্যত্র নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের গাড়ি থামাতেই একজনকে জিজ্ঞাসা করায় বললেন এই তো ঘাটলার অপর পাশেই তো ‘ফিরোজ মিনার’। তাইতো রাস্তার পূর্ব পাশেই গৌড়ের অন্যতম বিখ্যাত দর্শনীয় বস্তু যার নাম ফিরোজ মিনার। আমরা নামলাম। সবুজ সুন্দর পরিপাটি করে রাখা সবুজ ঘাসের চত্বরের মাঝে একটু উঁচু জায়গায় মধ্যযুগীয় ইটের তৈরি মিনার। মিনারে প্রবেশের পথ নিচের তলায়। মিনারটি ২৬ মিটার উচ্চতায়। উপরে গোলকৃতি ছাদ প্রায় পাঁচতলা হতে উঁচু তিন ধাপের পর উপরের দু’টি ধাপ ব্যালেন্স রাখবার জন্যে একে অপর হতে ব্যাসার্ধে ছোট অনেকেই মনে করেন মিনারটি তৈরি করা হয়েছিল ফিরোজ শাহর সুলতান হবার পর ১৪৮৬ সালে। আবার অনেকে মনে করেন এটা তৈরি শুরু করে হামুজ্জা শাহ ১৪১২ সালে। তবে এএসআইর তথ্য মতে এটি তৈরি করেছিলেন একজন আবেসিনিয়ান ব্যবসায়ী সাইফুদ্দিন ফিরোজ যিনি বারবাক শাহকে হত্যা করে ফিরোজ শাহ নাম ধারণ করে বাংলা অঞ্চলের সুলতান হন। এই মিনারে উঠবার জন্যে তেহাত্তরটি সর্পিল ধাপ রয়েছে তবে এখন এখানে উঠা বন্ধ করা হয়েছে। মিনারের এক পাশে বেশ বড় ধরনের প্রাচীন পাকুর গাছ। তার চারিদিকে সবুজ বেষ্টনী।
ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আমাদের সবার বাংলাদেশের সীম কার্ড চালু হয়ে গেল। গ্রামীণ ফোন ব্যবহার করে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশে যোগাযোগ করলাম। আমার ফোনে বিভিন্ন ধরনের প্রায় পঁচিশটি এসএমএস এলো। এ জায়গা চাঁপাই নবাবগঞ্জ সীমান্ত এলাকা হতে পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার দূরে মাত্র। এ জায়গাটির নাম কনকপুর। গৌড় বলে পরিচিত নয়। ফিরোজ মিনার হতে আমরা সোজা রাস্তায় যাবার উদ্যোগ নিলে স্থানীয় একজন বললেন যে আমরা পুকুরের উত্তর পাশ দিয়ে আম বাগানের মধ্যে দিয়ে গেলে বল্লাল প্রাসাদের ভগ্নাংশ দেখতে পারব এবং দেখতে পারব গৌড়ের সুউচ্চ দেয়ালের একাংশ। ওই রাস্তা ধরে আরেকটু সামনে এগুলেই প্রাসাদের এবং মন্দিরের অংশ পাওয়া যাবে আর নদীর পাড়ে পুরনো ঘাটের ভগ্নাংশ দেখতে পাব। বাকি সব এই একই রাস্তায় রয়েছে। আমরা এবার বল্লাল বাড়ি দেখার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আদি ভাগীরথীর তীরের এই বাড়ির ভগ্নাংশ বল্লাল সেনের না সুলতানদের প্রাসাদের ভিত তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। আর ভাগীরথী নদীর এ জায়গার অংশ এখন মৃত। এই নদীটিই ছিল গৌড়ের প্রাণ।
বলছিলাম গৌড় অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই অঞ্চলে বা বাংলার আলাদা সত্ত্বার গোড়াপত্তন করেন রাজা শশাঙ্ক গৌড় রাজত্ব নামে। শশাঙ্কের রাজত্বকাল ধরা হয় ৫৯০ হতে ৬২৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। তার রাজত্বকাল ধরা হয় হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক সময়ে। শশাঙ্কের সাথে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধও হয়েছিল। হর্ষবর্ধন বঙ্গ আক্রমণও করেছিলেন কয়েকবার। শশাঙ্ক বাংলা অঞ্চল স্থাপন করলেও গৌড় হতে অনেক দূরে বর্তমানের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কর্ণ সুর্বণতে রাজধানী স্থাপন করেন। সময়টি বাংলার বৌদ্ধদের রাজত্বকাল ও বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রসারণের সময়। শশাঙ্ককে বাংলা পঞ্জিকার প্রবক্তা বলে মনে করা হয়।
আমরা বেশ উঁচু মধ্যযুগীয় দেয়ালের একাংশের ধারে উপস্থিত হলাম। কয়েকজন লোক এখনও মাটি খোঁড়াখুঁড়িতে লেগে আছে। দেয়ালের পূর্ব পাশে অনেকখানি জায়গাজুড়ে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে। এটাই বল্লাল বাড়ি বা বল্লাল সেনের তৈরি কথিত প্রাসাদের ভিত। সামনে পিছনে আমের বাগান। অনেকগুলো গাছ বেশ পুরনো। একটি গাছের নিচে কয়েকজন দিবানিদ্রায় মগ্ন। দেয়ালের অপর প্রান্তে কিছু পিলারের ভগ্নাংশ রয়েছে। তবে আমাদেরকে একজন বললেন একটু সামনে আম বাগানের ভিতরে নদীর ধারে গেলে আমরা প্রাসাদের ভিত আর নদীর ঘাটটিও দেখতে পারবো। এই ঘাটটি মোগল আমলের অন্যতম কৃতি বলে অনেক ঐতিহাসিকরা মনে করেন। ইতিহাসের তথ্য মোতাবেক মোগল সম্রাট হুমায়ুন এখানে বেশ কিছু সময় কাটান এবং জায়গা বিশেষ করে আম তার অত্যন্ত পছন্দনীয় ফলে পরিণত হয়। তিনি এ জায়গার নাম দিয়েছিলেন ‘জান্নাতাবাদ’। কিন্তু এ নামে গৌড় কোনোদিন পরিচিত হয়নি।
আমরা গাড়িতে চড়ে নদীর ঘাটের দিকে রওয়ানা হবার জন্যে তৈরি হবার পথে একজন স্থানীয় লোক টলতে টলতে হাজির। মনে হলো সকাল হতেই বাংলা টেনে টাল হয়েছেন। এসে বললেন যে তাকে কিছু টাকা দিলে তিনি সব জায়গায় আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি আছেন। তার যে অবস্থা তাতে মনে হলো আরও কিছু টাকা পেলে তার দু’দিনের বাংলা টানার নিশ্চয়তা হবে। আমরা তার কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে রওয়ানা হলাম। নদীরপাড়ে আম বাগানে গাড়ি রেখে হেঁটে নদীর পাড়ে যাবার পথে বল্লাল বাড়ির মূলভিতের একাংশ দেখলাম। খনন কাজ চলছে। শেষ হতে অনেক সময় লাগবে। কাজ বেশ ধীরগতিতে চলছে। পাশেই বেশ বড় আমবাগান। কয়েকজন মিলে আমের গাছে ওষুধ ছড়াচ্ছে। এদের সবাই অবাঙালি। বিহারের শ্রমিক বাগানের মালিক মালদাতে থাকেন। এই বাগানসহ অনেক বাগান লিজ নিয়েছেন।
আমরা এবার পাকা রাস্তা ধরে চললাম কিছু দূর গিয়ে রাস্তার ধারে এক সাইকেল চালককে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে আর কি দেখার আছে। তিনি বললেন এ রাস্তা ধরে এগুলেই সব দর্শনীয় জায়গায় পৌঁছতে পারবো। এগুলো সবই বাংলার সুলতানি আমলের স্থাপনা। আমরা রওয়ানা হলাম তা দেখার উদ্দেশে। প্রায় এক কিলোমিটার পর অনেকগুলো স্থাপনার সামনে এসে দাঁড়ালাম। এখানে রয়েছে আরেকটি গেট। তার পাশে আমবাগানের মধ্যে এক গম্বুজের মসজিদ এবং রাস্তার অপর প্রান্তে আরেকটি মাঝারি ধরনের মসজিদ। সুন্দর পরিপার্টি করে রাখা।
সামনের গেটটির নাম ‘লুকোচুরি দরওয়াজা’। তৈরি হয়েছিল ১৬৫৫ খৃস্টাব্দে। দিল্লিতে তখন মোগল সাম্রাজ্যের মধ্য পড়ন্ত গগনে। তার পাশে বড় একটি চত্বরে ঘেরা দেয়া। রাস্তার অপর পাশে বেশ কিছু দোকান। চা আর বিভিন্ন খাবার আর কোল্ড ড্রিং-এর সমাহার। সামনের মসজিদ কমপ্লেক্সের নাম ‘কদম রসুল মসজিদ’। আমরা কয়েকজন চত্বরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। পাশে দু’টি পুরনো কবর। তার পাশে একটি পাকা স্থাপনার মধ্যে একটি বড় সড় কবর। সামনে একজন মাথায় টুপি পড়ে দাঁড়ানো। নাম জিজ্ঞাসা করলে বললেন আব্দুল করিম। মসজিদটির নাম কদম রসুল মসজিদ। সুন্দর পরিপাটি করে রাখা। স্বল্প পরিচিতি লেখা এএসআই-এর তথ্য। অন্যটিতে লেখা রয়েছে এই চতুষ্কোণ এই গৃহটি সুলতান নসরত শাহ দ্বারা নির্মিত মসজিদ। এর ভেতরে স্থাপিত হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর পদচিহ্ন। এটি তৈরি করেন সুলতান নসরত শাহ। সামনে বিশ্রামাগার যার কিছু ধ্বংসাবিশেষ দেখা যায়। সামনের এক রুমের কুটুরির ভিতরে একটি কবর। যার সামনে করিম দাঁড়ানো। সামনে সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য। তাতে লেখা রয়েছে এটি ফতে খাঁয়ের সমাধি। এখানে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনাপতি দেলোয়ার খাঁর পুত্র ফতে খাঁ সমাধিস্থ হয়েছেন। সময়কাল ১৬৫৮ হতে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ। আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা সুলতান সুজাকে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরামর্শদানের জন্যে পীর শাহ নিয়ামুতুল্লাকে হত্যা করার জন্য সম্রাট পাঠিয়েছিলেন। কথিত রয়েছে যে গৌড়ে পৌঁছার পর ফতেহ খাঁ রক্ত বমি করে মারা গেলে তাকে এখানে সমাধিস্থ করা হয়।
নাসরুল্লাহ চত্বরে এসে কয়েকটা ছবি তুলে বাইরে গিয়ে একটি দোকানে বসলেন। বাকি সবাই একই জায়গায়। চত্বরের মাঝে গাছের নিচে একটি বেঞ্চে বসে জাকারিয়া সিগারেট ধরালেন। আমি মসজিদের দিকে রওয়ানা হলাম। সামনে পাকা চত্বর আর ছোট বারান্দায় একজন কথিত খাদেম বসা। তিনি জানালেন যে, ভিতরে রসুল (স.)-এর কদম মোবারকের ছাপটি রক্ষিত। আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। ছোট কামরার মাঝখানে একটি উঁচু বেদিতে একটি কালো পাথরখণ্ডের উপরে একজন পরিপূর্ণ মানুষের পায়ের ছাপ। খাদেম জানালেন এটাই হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর কদম মোবারকের ছাপ। জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কিভাবে এই কদমের পাথরটি এসেছে। তিনি তেমন কিছুই বলতে পারলেন না। আমাকে জিজ্ঞাসা করায় বললাম বাংলাদেশ থেকে এসেছি। তিনি বললেন বাংলাদেশ থেকে অনেকে এখানে আসেন। বারান্দায় নামাজও আদায় করেন। আমি একাই কিছুক্ষণ থেকে বের হয়ে এলাম। বের হওয়ার পথে দেখলাম তিনজন বিদেশি পর্যটক একটি গাড়িতে মসজিদ দেখতে এসেছেন। সঙ্গে একজন গাইড।
কদমরসুল মসজিদ থেকে বের হয়ে সামনের একটি চায়ের স্টলে বাকি সবাইকে পেলাম। গ্রামের চায়ের স্টল। পাশে একটা খাবারের দোকান। সেখানে গিয়ে মসজিদের কথা বলাতে আমাদের কয়েকজন বললেন আগে জানলে তারাও যেতেন দেখতে।
শমসের বললেন, নারায়ণগঞ্জে কদমরসুল মসজিদে এরকম আরেকটি কদম মোবারক রক্ষিত রয়েছে। আমি বললাম, হ্যাঁ আমি দেখছি, তবে ওই পদচিহ্নের চাইতে এটা আকারে ছোট এবং স্বাভাবিক মানের। নারায়ণগঞ্জের কদমের চিহ্নের পাথরটি বেশ যত্নে রাখা। সবসময় নাকি দেখানো হয় না। মসজিদটিও একটু উঁচু যায়গায়। আমাকে ওই মসজিদের খাদেম বলেছিলেন যে সম্রাট শাহজাহান এখানে অবস্থানকালে এটা দিয়েছিলেন এবং মসজিদের যায়গাটিও তিনি দান করেছিলেন। ওই সময়কার সামান্য স্থাপনাও রয়েছে। খাদেম আরও বলেছিলেন যে দানপত্রটি এখনও সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। নারায়ণগঞ্জেও একটি মোগলদূর্গ রয়েছে যেখানে মোগল সৈনিকদের অবস্থান ছিল। ১৬৩২ সালে সম্রাট শাহজাহানের হুকুমে পুর্তুগিজদের হাত হতে হুগলি বন্দর উদ্ধার করেছিলেন।
চা শেষ করে আমি, শাহাবুদ্দিন, জাকারিয়া এবং তানভীর পাশের আম বাগান দিয়ে অপর প্রান্তে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি স্থাপনা যা চিকা মসজিদ নামে পরিচিত সেদিকে রওয়ানা হলাম। আম বাগানে ঢুকতেই একটি বড় গাছের নিচে অস্থায়ী নরসুন্দরের দোকান দেখলাম। একটি চেয়ারে কাস্টমার বসা। সামনের গাছে মধ্যম সাইজের আয়না ঝুলানো। চুল কাটা শেষ হবার পর ক্ষৌরকর্মের জন্যে মুখে সেভিং ফোম লাগিয়ে হালকা ম্যাসাজ চলছিল। এমন আরামে খদ্দের আমেজে চোখ বুঝে রইলেন। হয়ত আমাদের আগমন তার আরামের কিছুটা ব্যাঘাত ঘটালো কারণ তিনি চোখ খুলে একবার আমাদেরকে দেখে নিলেন। এক সময়ে আমাদের গ্রামেগঞ্জে বিশেষ করে হাটের দিনে এরকম দৃশ্য অহরহ দেখা যেত এখন আর তেমন দেখা যায় না। এখন গ্রামের বাজার হাটেও চুল কাটার ছোটখাট দোকান রয়েছে। শহরে এখন আর ক্ষৌরকর্ম বলা হয় না বলা হয় হেয়ার কাট আর আধুনিক নরসুন্দরদের এখন পরিচিতি হেয়ার ড্রেসার। আমি তানভীরকে বললাম, মনে হয় না এখানে এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে ক্ষৌরকর্ম করি আর ওর ওই পাতা মাদুরে শুয়ে গা হাত পা মর্দন করাই। তানভীর বললেন, হোটের নিচতলায় স্পা (ঝঢ়ধ) রয়েছে সেখানে যাব।
হাঁটতে হাঁটতে আমরা চিকা মসজিদ নামক স্থাপনার গেটে চলে এলাম। একে গম্বুজ বিশিষ্ট স্থাপনাটি চারদিকে চারটি দরওয়াজা। ভিতরে আর কোনো জানালা নেই। সম্পূর্ণ ছাদটাই গম্বুজ আকৃতির। তথ্য ফলকে লেখা রয়েছে যে এই স্থাপনাটি তৈরি করেছিলেন সুলতান ইউসুফ শাহ ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে। তবে নামটি বেশ চমকপ্রদ। কেন এমন নাম তার একটি ব্যাখ্যা হল যে মসজিদের অভ্যন্তরে অগণিত চিকা বাদুরের বাস। তাই এ মসজিদের নামকরণ। মসজিদের খিলানে কোরানের সূরা খোদিত ছিল যার কিছুটা এখনও দেখা যায়। তবে মসজিদের নকশায় মন্দিরের ছাপ রয়েছে যে কারণে এটি অন্যান্য মসজিদ হতে আলাদা। মধ্যযুগীয় ইটে তৈরি মসজিদটির উপরে কোন আস্তর নেই।
তবে অনেকে মনে করেন এটা সুলতান জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ রাজা গণেশের পুত্র-এর সমাধি। হতেও পারে কারণ কোনো আঙ্গিকেই তথাকথিত চিকা মসজিদটি মসজিদ মনে হয় না। আমার কাছেও তেমনই মনে হয়েছে। তবে এখানে সমাধির কোনো চিহ্নও দেখা যায়নি। তবে এখানকার অনেক দর্শনীয় স্থানের ইতিহাস তেমনভাবে লিপিবদ্ধ নেই।

আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম যা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে তবে আশেপাশের সবুজ ঘাসের চত্বর পরিপাটি করে সাজানো। দক্ষিণদিকে কয়েকটি বাসস্থান। এখানে এএসআইর লোকজন থাকে। পূর্বপাশে একসময় হয়তো একটি জৈন মন্দির ছিল যার খণ্ডিত কয়েকটি পিলার এখনও দণ্ডায়মান। একটু সামনে প্রায় আট বা নয় ফুট লম্বা একটি পাথরের পিলার রক্ষিত। যেটি মন্দিরের পিলার। আরেকটু দক্ষিণে উঁচু ঢিবির মত। যার পেছনে শহরের দেয়ালের সামান্য ভগ্নাংশ এখন দৃশ্যমান। পূর্বপ্রান্তে লুকোচুরি দরওয়াজার পেছনের অংশ।
চিকা মসজিদটির নামের সাথে সুলতান সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের নাম জড়িত। তিনি ছিলেন সুলতান বারবাক শাহর পুত্র। তিনি বাংলার শাসক হন ১৪৭৪ সালে। শুধু এই মসজিদটিই নয় সুলতান ইউসুফ শাহ গৌড়ের আরও কয়েকটি মসজিদ তৈরি করেছিলেন। এমনকি কদমরসুল মসজিদের ভিতও তিনি স্থাপন করেন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। তিনি নিজেও ইসলামিক চিন্তাবিদ ছিলেন। তার স্থাপনাগুলোর মধ্যে বাংলার নির্মাণশৈলীর ঐতিহ্যও মিশ্রিত রয়েছে। তিনি ১৪৭৪ সাল হতে ১৪৮১ সাল পর্যন্ত বাংলার শাসক ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র দ্বিতীয় সিকন্দার শাহ বাংলার সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হয় ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে। তবে তার মানসিক ভারসাম্যের সমস্যা হওয়াতে মাত্র কয়েকদিন সুলতান ছিলেন। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার ভাই জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ।
বাংলায় হাবসী শাসকবৃন্দ ইলিয়াস শাহী বংশের মাঝখানে রাজত্ব করেছিলেন। এরা ছিলেন আবেসিনিয়ার হাবসী। এদের মধ্যে চারজন ছিলেন হাবসী সুলতান। বারবাক শাহ, ফিরোজ শাহ, কুতুবউদ্দিন মাহমুদ শাহ এবং শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ। যাই হোক বাংলার সুলতানদের ইতিহাসের অনেক যায়গা অস্পষ্ট রয়েছে।
আমরা চিকা মসজিদ থেকে ফিরে আসছিলাম তখনও দেখলাম আগে বর্ণিত নরসুন্দরের খদ্দের তখনও আরামে চোখ বন্ধ করে ক্ষৌরকর্ম উপভোগ করছেন। গাছের নিচে এমনিতেই বেশ শীতল পরিবেশ এই গরমে। এ ধরনের পরিবেশে এমনিতেই ঝিমুনি আসার কথা। আমারও খুব ইচ্ছে হচ্ছিল এখানেই এমনভাবে বসে চুল কাটাই।
চায়ের দোকানে ফিরে এসে আবার চা খাবার ইচ্ছে হলো। চা খেতে খেতে দেখছিলাম কিভাবে স্বামী-স্ত্রী দুজনে চায়ের দোকানটি পরিচালনা করছেন।
চায়ের দোকানটি একেবারে গ্রামেগঞ্জের পরিবেশে তৈরি। পাতা বেঞ্চে বসলাম। বিস্কুট চাইলে মহিলা বিস্কুটের ভাণ্ডটি এগিয়ে দিয়ে বললেন যে, আমাদের পছন্দমত বিস্কুট যেন তুলে নেই। জিজ্ঞাসা করলাম কেমন চলে? বললেন যে এই মৌসুমে আশেপাশের গ্রামের লোকছাড়া বাইরের লোক তেমন আসে না। তবে শীতের কয়েক মাস বেশ ভাল চলে। পর্যটকরাও যেমন আসে তেমনি এখানে প্রচুর পিকনিক পার্টি আসে। অবশ্য তার কিছুটা ধারণা আমরাও পেয়েছি আম বাগানে প্লাস্টিকের গ্লাস এবং খাবারের পরিত্যাক্ত পাত্র দেখে। আরও বললেন যে, আমের মৌসুমেও বেশ ভাল বেচাকেনা হয়।
অনেকক্ষণ বসে রইলাম এমন একটি ঐতিহাসিক যায়গায় সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে। আম গাছের প্রাচুর্য আর সবুজের মাঝে। শান্ত পরিবেশ দুপুরের রোদে পাশের আম বাগান হতে চিরপরিচিত ঘুঘুর ডাক শুনতে বড় ভাল লাগছিল। মনে হলো আরও কিছু সময় বসে থাকি কিন্তু সবাই উঠবার তাড়া দিলেন। ফেরার পথে বড় সোনা মসজিদটি দেখে মালদাতে গিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ সারব। বিকেলটায় সময় পেলে একবার ইংলিশ বাজারটা ঘুরে আসব।
গাড়িতে ফেরার পথে ভাবছিলাম যে এই শহরটি ওই সময় কেমন ছিল? প্রশ্ন জাগল যে এতগুলো স্থাপনা দেখলাম সবই বাংলার সুলতানি আমলের কিন্তু বল্লাল সেনের বাড়ি বলে কথিত রাজবাড়ি ছাড়া শাসকদের বাসস্থান বলে কোনো নির্দিষ্ট যায়গার খোঁজ পেলাম না। চোখেও পড়েনি। জাকারিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনিও বললেন, তাইতো? বললাম হয়ত ওই সময় পাকা প্রাসাদের চল তেমন ছিল না যেমনটি পরবর্তীতে মোগলদের সময় দুর্গের ভিতরে সম্রাটদের বাসস্থান ঘিরেই দুর্গের বিন্যাস ছিল। কিন্তু দিল্লি সালতানাতেও একমাত্র মোহাম্মদ বিন তুগলকের দুর্গ জাহানপনা ছাড়া আর কোনো স্থাপনায় বাসস্থান দেখা যায়নি।
আমরা গৌড়ের সবচেয়ে আলোচিত এবং পরিচিত বড় সোনা মসজিদের সামনে পৌঁছলাম। সামনে ছোট একটি পাড়া বা বাসস্থান। সামনে একটি বড় বটগাছ তার পাশে দুটি ছোট মুদির দোকান। সামনেই উঁচু একটি যায়গায় বড় সোনা মসজিদের অবশিষ্ট অংশ। বড় ধরনের ঘেরা দেয়া। সামনের গেটটি ভেজানো। দোকান থেকে একজন বললেন ভিতরে গিয়ে দেখতে পারেন। যদিও একটি টিকেট ঘর ছিল কিন্তু টিকেটের ব্যবস্থা নেই। আমরা গেটটি খুলে প্রবেশ করলাম। মসজিদটি মধ্যযুগীয় স্থাপত্যে তৈরি। ইট আর বড় পাথরের তৈরি। সামনে একটি বড় ঘাসের লন। সুন্দর পরিপাটি করে ছেটে রাখা। তার উল্টোদিকে সুলতানি দরওয়াজা। উত্তর দিকে আরেকটি প্রবেশ গেট তবে পূর্বদিকের প্রধান ফটক হতে ছোট। আমরা যে পথে এসেছি সেখানেও একটি গেট ছিল বলে মনে হয়।
মসজিদটি তৈরি করা শেষ হয়েছিল ১৫২৬ সালে। গৌড়ের সবচেয়ে বড় স্থাপনা এই বড় সোনা মসজিদ। সামনে পায়ে চলা পথ। লনের দু’পাশে হাঁটু সমান ফ্যান্সিং (স্টিলের তৈরি তারের বেড়া)। খুবই সুন্দর করে গাথা মসজিদটি ৫০.৪ মিটার লম্বা, ২২.৮ মিটার প্রশ্বস্থ এবং ১২ মিটার উঁচু। মূল মসজিদের অংশটিতে এখনও ছাদ রয়েছে। মেঝেটি পরিষ্কার তকতকে করে রাখা। এই মসজিদটি তৈরি শুরু হয়েছিল সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সময় এবং শেষ হয় তার পুত্র নাসিরুদ্দিন নসরতের সময়। মসজিদটির আদি নাম বারো দুয়ারি।
বারোদুয়ারি মসজিদটিতে বাস্তবে ১১টি প্রবেশ পথ রয়েছে, যার নকশা ইন্দো-আরব ধরণের। দু’পাশে দুটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার এবং চারকোনায় চারটি মিনার রয়েছে। মিনারগুলোর উচ্চতা বর্তমানের প্রচলিত মিনারের মতো নয়। উপরের ছাদে ৪৪টি আধা গম্বুজের মত তৈরি। ছাদের উপরের অংশে রয়েছে এই ৪৪টি গম্বুজ। তবে অনেকাংশ নষ্ট হলেও এখনও ১১টি বারান্দা রয়েছে যে জায়গায় নামাজ পড়া হতো। এই মসজিদের আদিনাম কুতুবশাহী মসজিদ। নামকরণ করা হয়েছিল সুফি দরবেশ নূর কতুব আলম যারা পিতার নাম সুফি মখদুম আলাউল হক পাণ্ডভী। সোনা মসজিদটির পিলারগুলো এক সময় সোনালি পাত দিয়ে মোড়ানো ছিল-তাই প্রচলিত নাম সোনা মসজিদ।
আমরা মসজিদের পশ্চিমদিকে গেলাম। সেখানে যে বারান্দাটি ছিল তার ছাদ ধসে পড়েছে। পিলারগুলো এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে বেশ কয়েকটি মেহরাব ছিল। পেছনে মানে পশ্চিম দিকে বেশ বড় বড় কয়েকটি পাকুর গাছ রয়েছে। নিচের দিকে সীমানার বাইরে পায়ে চলা পথ এবং বেশ জঙ্গলের মতো।
বেশ অনেকক্ষণ আমরা ঘুরে ঘুরে গৌড়ের সবচাইতে বড় স্থাপনাটি দেখলাম। বের হবার পথে উত্তর মাথায় দু’জন লোককে বসে থাকতে দেখলাম। আমি ওই দু’জনের কাছে গেলে তারা উঠে দাঁড়ালেন। লুঙ্গি গেঞ্জি পরিচিত এই দু’জনের একজন এএসআইর কর্মচারী যিনি এই জায়গায় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আর অপরজন পাশের পাড়ার যিনি এখানে পারিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজের জন্য খণ্ডকালীন নিযুক্ত। পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলাম এখানে এত ফ্লাড লাইট দেখছি এগুলো কি লাইট এন্ড সাউন্ড শোর জন্যে? উত্তরে জানালেন যে শীতের সময় লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হয় তবে প্রতিদিন হয় না। সপ্তাহে দু’ তিন দিন হয়। একজন বললেন আপনাদের ওখানেও তো ছোট সোনা মসজিদ আছে বলে শুনেছি। আমি বললাম হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন তবে ওই মসজিদটি বেশ ছোট। পরে আমি আদিনা মসজিদের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে আদিনা মসজিদ মালদা হতে উত্তর দিকে প্রায় ১৮ কি. মি. প্রধান সড়কের ধারে। ওই জায়গাটির এক সময়ের নাম ছিল ‘পাণ্ডু’। পাণ্ডু বেশ অনেক যুগ বাংলার রাজধানী ছিল। আমরা বড় সোনা মসজিদ হতে বের হয়ে মালদাতে ফেরার পথ ধরলাম। বললাম বিকেল চারটার দিকে আদিনা মসজিদ দেখতে যাব। জাকারিয়া, শমসের রাজি হল আমার সঙ্গে যেতে। পরে তানভীরও যুক্ত হয়েছিল।
গৌড় দেখার পর্ব এখানেই শেষ হলো। গৌড়ে এত স্থাপনা দেখতে পাবো তেমন ধারণা ছিল না। স্থাপনাগুলো যেভাবে সংরক্ষিত আছে সে রকম দেখতে পারব তেমন ধারণাও ছিল না। আমার মনে হল আমাদের এই সফর অন্যদের কাছে কেমন লাগল জানাবার প্রয়োজন। সবাই একবাক্যে বললেন যে এখানে না আসা পর্যন্ত ধারণাই করতে পারেননি যে এখানে এত কিছু দেখার রয়েছে। কয়েকজন তো নামই শুনেননি।
আমরা যে রাস্তায় এসেছিলাম সে রাস্তা ধরেই ফিরছি। এতক্ষণ টের পাইনি যে গরমে শরীর ক্লান্ত হয়ে পরেছে। হোটেলে গিয়ে আরেকবার গোসল করতে হবে।
গৌড় আর পাণ্ডু বা পাণ্ডুয়াতে এখনও যা রয়েছে সেগুলো মুসলিম শাসকদের কীর্তি। এদের কেউই এখনকার মাটির মানুষ ছিলেন না। যেমন ছিলেন না হিন্দু শাসকরাও। এরা সবাই বাংলায় এসেছিলেন সমৃদ্ধির খোঁজে, ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। বাংলায় বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, মুসলিম এবং ইংরেজ সবাই রাজত্ব করেছে।
বাংলায় মুসলমান সৈনিকদের আগমন এবং এখানে রাজত্ব কায়েমের সূত্রপাত হয় ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজির সময়। ভাগ্যান্বেষী একজন আফগান যোদ্ধা কুতুবউদ্দিন আইবেকের দিল্লি জয়ের পর ১২০২ সালে বিহার এবং ১২০৩ সালে নদীয়ার নবদ্বীপে সেন বংশের শেষ নৃপতি লক্ষণ সেনকে পরাজিত করেন। পরে গৌড়ে তিনি অস্থায়ী রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষণ সেন কুসংস্কারে বিশ্বাস করার কারণে বিনা যুদ্ধে পরাজিত হন। মাত্র ১৮ জন সৈনিক নিয়ে রাজধানী আক্রমণ করে সহজেই বখতিয়ার খিলজীর কাছে হার মানেন। লক্ষণ সেনের দরবারের জ্যোতিষী আজানু লম্বিত হাত বিশিষ্ট এক সিপাহশালারের হাতে তার পরাজয়ের ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন বলে তথ্যে পাওয়া যায়। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই লক্ষণ সেন তার রাজধানী পরিত্যাগ করেছিলেন।
বখতিয়ার খিলজি দক্ষিণ আফগানিস্তানের তুর্কি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বহু চড়াই উৎরাই পার হয়ে খিলজি বাংলা জয় করে রাজত্ব কায়েম করেন। খিলজী পরে তিব্বতের দিকে অভিযান চালান তবে কৃতকার্য হতে পারেননি। সেই হতেই বাংলায় মুসলমানদের শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল। এর পরে চতুর্দশ শতাব্দি হতে বাংলা স্বাধীন সুলতানদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। বাংলার সুলতানি শাসন বা শাহী বাংলা বেশির ভাগ সময়েই স্বাধীনভাবে শাসিত হয়। এর স্থায়ীকাল হয় ১৩৫২ হতে ১৫৭৬ পর্যন্ত। এর গোড়া পত্তন করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। এই রাজত্ব শাসন করেন পাঁচটি বংশ। ষোড়শ শতাব্দিতে শেরশাহ সূরীর বাংলা জয়ের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলার পতন হয়। শের শাহর পর মোগল সম্রাট হুমায়ুন বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করেন। আরও পরে ১৫৭৬ সালে সম্রাট আকবর পূর্ববাংলার শেষ সুলতান দাউদখান কররানীকে পরাজিত করেন। এরপর হতেই সমগ্র বাংলা অঞ্চল মোগল বাংলায় পরিণত হয়।
বাংলায় বারো ভূইয়াদের পরাজিত করে ১৬১০ সালে মোগল সিপাহসালার ইসলাম খাঁ রাজমহলে সুবে বাংলার রাজধানী স্থাপন করলেও পরে ঢাকাকে রাজধানী করেন। ওই সময়ে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শহরের নামকরণ করেন জাহাঙ্গীর নগর। গৌড় পরিত্যক্ত হয়। এরপর গৌড় আর পুরাতন ঐতিহ্য ফিরে পায়নি। মুর্শিদকুলি খাঁ দেওয়ানী ঢাকা হতে নতুন শহর মুর্শিদাবাদ পত্তনের পর বাংলার স্বাধীন নবাব ঘোষণার মধ্যদিয়ে রাজধানী ঢাকা হতে মুর্শিদাবাদ স্থানান্তর করেন। ইতিহাসে যা ঘটে যায় তাকে হয়তো ফিরিয়ে আনা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন থাকে ‘যদি’ রাজধানী ঢাকাতেই থাকত তবে কি ‘পলাশী’ ঘটতো।
আমরা দুপুর আড়াইটার দিকে হোটেলে ফিরে এলাম। রিসিপশন থেকে আদিনা মসজিদ, আদিনা পার্ক এবং পাণ্ডুয়ার অবস্থান জেনে নিলাম। তাড়াতাড়ি দুপুরের খাবার শেষ করে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে আমি, জাকারিয়া, শমসের আর তানভীর রওয়ানা হলাম আদিনা মসজিদ দেখতে। মাত্র ১৮ কি. মি. আধা ঘণ্টা সময় লাগার কথা। আমরা মালদা শহরের সুকান্ত মোড় পার হয়ে উত্তরদিকে রওয়ানা হলাম। এ ধারের রাস্তা ৪ লেনের বেশ প্রশস্ত। মাঝের ডিভাইডারও বেশ চওড়া। শহরের এ-প্রান্তে রাস্তায় কিছুটা ভিড়। ট্রাকের সমারোহই বেশি। আশেপাশের শ্রীহীন দোকানগুলো দেখে মনে হলো যে শহরটি তেমন বিত্তবানদের নয়। মাঝপথে এক যায়গায় থামলাম ফল কেনার জন্য। শমসের পাশের হকারের কাছ থেকে একটা তরমুজ কিনলেন আর এক ডজন কলা। আমি কাছাকাছি এক ঠেলাগাড়ি হতে আঙ্গুর কিনব বলে দাঁড়ালাম। এ সময় আঙ্গুরের মৌসুম। বেশ সুস্বাদু। আসে নাসিক অঞ্চল এবং জম্মু কাশ্মীর হতে। আমার পাশে শমসের এসে দাঁড়ালেন। বললাম কিছু আঙ্গুর নিয়ে যাই। বিক্রেতাকে দাম জিজ্ঞাসা করলে বললেন, ২৫০-২৫। আমি মানেটা বুঝলাম না। ২৫০-২৫ মানে কি জিজ্ঞাসা করতেই পাশে দাঁড়ানো শমসের বললেন মানে ২৫০ গ্রামের দাম ২৫ রুপী। তার মানে ১ কেজি ১০০ রুপী। বিক্রেতা বিগলিত হয়ে বললেন, তাই বাবু। আমি বললাম আমি তো ১ কেজি নেব। শুনে দারুণ উল্লসিত হয়ে ১ কেজি মেপে দিলেন। শমসের বললেন, এখানে আমাদের মত ১ কেজি করে খুব কম কেনে তাই ২৫০ গ্রামের হিসাব।
আমরা অনেকগুলো ফলফলাদি কিনে পুনরায় আদিনা মসজিদের পথে রওয়ানা হলাম। আদিনা মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন বিশাল পার্কের নাম আদিনা সাফারি পার্ক। আদিনা মসজিদটি ওই সময়ে এশিয়ার তথা তৎকালীন ভারতের সবচাইতে বড় মসজিদ ছিল। মসজিদটি ছিল বাংলার আরেক রাজধানীর এক প্রান্তে।
পাণ্ডুয়া কোন সুলতানের সময় স্থাপিত হয়েছিল তা খুব একটা নিশ্চিত নয় তবে ঐতিহাসিক তথ্য মোতাবেক ধারণা করা হয় যে শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ-এর সময় এ শহরটি তৈরি করা হয়। পরে ১৩৩৯ সালে আলাউদ্দিন আলী শাহ গৌড় হতে রাজধানী পাণ্ডুয়াতে স্থানান্তরিত করেন। যদিও দুটি ঐতিহাসিক শহর খুব দূরে নয় তথাপি এই দুই জায়গা বাংলার রাজধানী ছিল। পাণ্ডুয়া রাজধানীর মর্যাদা হারায় ১৪৫৩ সালে যখন নাসিরুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ পুনরায় গৌড়ে রাজধানী নিয়ে যান। পাণ্ডুয়া মালদার ইংলিশ বাজার হতে মাত্র ১৮ কিলোমিটার। পাণ্ডুয়াতে এখন দেখার তেমন কিছু নেই। আদিনা মসজিদ ছাড়াও ঐতিহাসিক স্থাপনার মধ্যে আরও রয়েছে এখলাখি সমাধি সৌধ এবং কুতুবশাহী মসজিদ। আদিনা মসজিদটি অনেকটা দামেস্কের গ্রান্ড মসজিদের আদলে তৈরি করেছিলেন সিকান্দার শাহ ১৩৬৯ সালে। আর এখলাখি সমাধী সৌধটি সুফি সাধক বলে পরিচিত জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহের। জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ প্রায় ১৫ বছর রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন বাংলার রাজা গনেশের পুত্র।
রাজা গনেশ বাংলার সুলতান বংশ প্রথম ইলিয়াছ শাহীদের দুর্বলতার কারণে ক্ষমতা দখল করেন ১৪১৫ সালে। পরে তার পুত্র ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করে বাংলার সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হয়। তার সময়েই আরাকান রাজ্যের স্বাধীনতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্বাধীন আরাকান তখন বাংলার করদ রাষ্ট্র হিসেবে ছিল। চিকা মসজিদে তার কবরের ধারণাটি হয়ত সঠিক নয়।
রাজা গনেশের নাম জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহের মুদ্রায় উল্লেখিত রয়েছে কানস রাও অথবা কানস শাহ হিসাবে। তিনি মাত্র ১ বছর (১৪১৪-১৪১৫) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে রাজা গনেশ ভাটুরিয়ার শক্তিশালী জমিদার এবং দিনাজপুরের গভর্নর হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন। বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাস যথেষ্ট জটিল। দিল্লির ইতিহাসের মত এতটা পরিচিত নয়।
আমরা পুরাতন মালদা ছেড়ে হাইওয়েতে। দুপাশে কৃষিক্ষেত। আমের বাগান। এ অঞ্চলে কিছু শিল্প কারখানা রয়েছে। চার লেনের হাইওয়ে। আমরা উত্তরমুখী। ছোট উন্নত গ্রাম সুলতান দিঘী পার হলাম। বেশ কিছু পাকাবাড়ি। ফাঁকে ফাঁকে বাঁশের বেড়া আর মাটির দেয়ালের বাড়িগুলোর উপরে লাল টালি দেয়া। রাস্তায় তেমন ভিড় নেই। সুলতান দিঘি পার হওয়ার পর পশ্চিম দিকে বিএসএফ-এর ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর। মাঠে কিছু সদস্য ফুটবল খেলায় রত। অতি পরিচিত দৃশ্য। সামনে দিক নির্দেশনা বোর্ডে লেখা পাণ্ডুয়া সামনে। আমরা আদিনা মসজিদের কাছাকাছি। পশ্চিমে একটি ছোট রাস্তা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেছে। রাস্তার জংশনের কাছাকাছি একটি মধ্যযুগীয় ছোট মসজিদের মত দেখলাম। রাস্তার দিক নির্দেশনা বোর্ডে লেখা পাণ্ডুয়া। একটু ভিতরে গেলেই পাণ্ডুয়া গ্রাম যা এক সময় বাংলার রাজধানী ছিল। আদিনা মসজিদটিও পাণ্ডুয়ার একাংশে। যে পুরনো মসজিদটি আমরা ছেড়ে এসেছি সম্ভবত ওটাই কুতুবশাহী মসজিদ। ওখানে যাওয়া হয়নি কারণ আমাদের হাতে সময় ছিল না। সূর্য হেলে পড়েছে প্রায় পাঁচটা বাজে। প্রায় আরও এক কিলোমিটার যাওয়ার পর হাইওয়ের পশ্চিম পাশে একটি ছোট রাস্তা, মোড়ে বেশ কিছু কাচাঘরে চায়ের আর রকমারি দোকান। লেখা আদিনা মসজিদ। রাস্তা থেকেই মসজিদের ভগ্নাংশ দৃশ্যমান হল। এটাই ইতিহাস খ্যাত আদিনা মসজিদ।
গাড়ি এক পাশে দাঁড় করিয়ে আমরা চারজন নামলাম। উত্তরেই আদিনা মসজিদ। সুন্দর করে ফ্যাঞ্চিং (স্টিলে তৈরি তারের বেড়া) ঘেরাও দেয়া। আমরা গেটের সামনে গিয়ে দেখলাম গেট বন্ধ। তারই সামনে মোবাইল আইসক্রিম বিক্রেতা। পাশে পানিপুরির ঠেলা গাড়ি। চিকন রাস্তার অপর পাড়ে কয়েকটি বসতবাটি। কয়েকজন মহিলা আর পুরুষ বসে রসুন পরিস্কার করছে। বেশ কয়েক মণ হবে। মনে হলো খেত হতে উঠানোর পর রাস্তার উপরেই শুকানো সেরে পরিস্কার করতে ব্যস্ত। আমরা গেটের কাছে এসে দেখলাম বড় তালা ঝুলছে। পাশে এএসআই-এর সাইন বোর্ড। টিকিট ঘরটি বন্ধ। ওখানে কাউকে দেখলাম না। আইসক্রিম বিক্রেতা জানালেন যে পাঁচটায় গেট বন্ধ হয়ে যায়। সকাল ৮টায় দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেয়া হয়।
আমরা বেশ মর্মাহত হলাম। এত দূর এসে ভিতরে যেতে পারলাম না। মাত্র ১০ মিনিট দেরি করে এসেছি। আশপাশে এএসআইর কাউকেই দেখলাম না যাকে অনুরোধ করে গেট খোলতে পারতাম। আমাদের চেহারায় হতাশা দেখে আইসক্রিম বিক্রেতা জিজ্ঞাসা করলেন কোথা থেকে এসেছি? বাংলাদেশ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজশাহী? বললাম না ঢাকা হতে। বললেন, রাজশাহী তো অনেক কাছে। তার কথা কানে ঢুকল না।
অগত্যা দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানো ছাড়া এ পর্যায়ে আর গতি পেলাম না। বেষ্টনীর বাইরে দাঁড়িয়ে যতটুকু দেখা যায়। মসজিদটি ওই সময়ে ভারতবর্ষের সবচাইতে বড় মসজিদ ছিল। এখন পরিত্যক্ত ভগ্ন দশায়। উপরের বেশির ভাগ জায়গায় ছাদ ভেঙে পরেছে। ভিতরে যতটুকু দেখা গেল তাতে মনে হল ভিতরের অংশ উত্তর দক্ষিণে বড় আয়তনের নামাজের জায়গা ছিল। পশ্চিম প্রান্তে বেশ বড় জায়গায় সবুজঘাসের চত্বর। আশপাশে পুরাতন বেশ কিছু আমের গাছ। সামনে দাঁড়িয়ে এএসআই-এর তথ্য কনিকা পড়লিাম। এ ধারের সব গ্রামগুলোতেই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকের বাস। চেহারায় চলন বলনে তেমনই মনে হলো। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে যতটুকু সম্ভব দেখলাম। পূর্বদিকে লম্বা টানা বারান্দা ছিল। বেশ কয়েকটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরদিকে একটু উচু বেদী যেখানে সুলতানের বসবার জায়গা ছিল।
মসজিদটি দামেস্কের উমাইয়া মসজিদের আদলে তৈরি। এই মসজিদটি তৈরি হয় বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় সুলতান সিকান্দার শাহের সময়-চতুর্দশ শতাব্দীতে। সিকান্দার শাহ ছিলেন সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের পুত্র। সিকান্দার শাহ দিল্লির সুলতানদের আধিপত্যকে পরাজিত করে বাংলাকে পুর্ণাঙ্গ স্বাধীন সালতানাতে পরিণত করেন। সিকান্দার শাহ দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করাতে বাধ্য করেন একটি একটি চুক্তির মাধ্যমে। সিকান্দার শাহ প্রায় তিন দশক শাসন করেন এবং সম্রাট শাহজাহানের মতই শিল্প পিপাসু ছিলেন। তার সময়েই বেশিরভাগ স্থাপনা তৈরি হয়েছিল। এএসআইর তথ্য মতে, এর নির্মাণকাল ১৩৭৩ সাল। বর্তমানে এসব দর্শনীয় জায়গা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে।
জাকারিয়া, তানভীর আর শমসের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছবি উঠাতে ব্যস্ত। আমি এএসআইর তথ্য কনিকা পড়ছিলাম। সামান্য কিছু তথ্য রয়েছে বোর্ডে। মসজিদটি বাংলার সুলতানদের এবং বাংলার স্থাপত্যের গর্বের বিষয় যদিও এখন এর ভগ্নাংশই রয়ে গিয়েছে। মসজিদের দৈর্ঘ্য মোট ১৫৫ মিটার প্রস্থ ৮৭ মিটার। নামাজের জায়গা ২৪ মিটার প্রশ্বস্থ। উচ্চতায় ছিল ১৮ মিটার বারান্দাটি ছিল ১২ মিটার প্রশ্বস্থ। ইট পাথরের সমন্বয়ে তৈরি মসজিদটি। মসজিদের চারদিকেই বারান্দা ছিল যার ভগ্নাংশ এখনও দেখা যায়। উত্তরের একাংশে ছাদ এখনও রয়েছে। রয়েছে ছাদের কলামগুলো অনেক মৌমাছির বাসার মতো, হানি কম্ব সাদৃশ্য।
সমগ্র, গৌড়, যতটুকু দেখিছি প্রায় দশ বছর আগ পর্যন্ত এসব নিদর্শনগুলো প্রায় অজত্নে ছিল যা মুর্শিদাবাদে আমার প্রথম ভ্রমণেই দেখেছিলাম। একথা স্বীকার করতেই হবে যে মমতা ব্যানার্জীর সরকার বাংলার গৌরবময় ইতিহাসের নিদর্শনগুলো তা যে ধর্মেরই-কালের হোক সংরক্ষিত করে রাখছেন যার উদাহরণ মুর্শিদাবাদের মতিঝিল পার্ক এবং মুর্শিদাবাদের ইতিহাস। গৌড় বা লক্ষনাবতীর ইতিহাসই বা আমরা কতখানি জানি বা দেখতে বা বুঝতে চাই। এখানে এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে না এলে বুঝতে পারতাম না। হয়ত আরও আগে এলে আরও ভাল হতো। গৌড় বা পাণ্ডুয়ায় যা দেখেছি তা ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যের নিদর্শন হলেও এর সাথে মিশ্রণ হয়েছে বাংলার স্থাপনা এবং সামাজিক ঐতিহ্য। ছাদ এবং পিলারগুলো দেখলেই সহজে ধারণা করা যায়। অনেক স্থাপনার ছাদ বাংলার সাধারণ বাড়ির বা ঘরের ছাদের আদলেরও দেখেছি। এগুলো দিল্লি বা উত্তর ভারতে স্থাপত্যের চাইতে আলাদা।
প্রায় ৪০ মিনিট কাটালাম। জাকারিয়া বললেন, আফসোস পাণ্ডুয়ার অন্যান্য জায়গায় ঘুরে দেখতে পারলাম না। আমি বললাম পাণ্ডুয়ায় দেখার মতো এই আদিনা মসজিদ। একে ঘিরে অনেক ইতিহাস রয়েছে। এমন হতে পারে যে আগামীকাল আমরা কলকাতায় ফেরার পথে ৮টায় এখানে এসে যদি ৯টাতেও রওয়ানা হই তাতেও আমরা সময়মতো পৌঁছতে পারব। তবে সেক্ষেত্রে হোটেলে গিয়ে বাকিদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কলকাতা মালদা হতে দক্ষিণে কাজেই এ জায়গায় এলে আসা যাওয়াতে আর ৩৬ কি. মি. যোগ করতে হবে। আমার সন্দেহ হল যে আদৌ সকালে আমরা আসতে পারব কিনা?
আমাদের ফেরার পালা। হঠাৎ মনে হলো শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে। প্রচুর ধোঁয়া উঠছে আশপাশের বসতবাড়িগুলো হতে। এ অঞ্চলে এখনও জ্বালানি হিসেবে শুকনা গোবর ব্যবহার করা হয়। প্রায় সব বাড়িতেই ব্যবহার হয় গোবরের ঘুটে যা ছোট বেলায় আমাদের গ্রামগঞ্জেও দেখেছি। এখনও হয়ত ব্যবহার হয় তবে খুব কম। উত্তরবঙ্গের গ্রামের দিকে দেখা যায় মাঝে মধ্যে। তবে এখন তেমন প্রচলন নেই। এখন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থাপন্ন বাড়িঘরে এলএনজি ব্যবহার হয়। দেয়ালে ঘুটে শুকানোর দৃশ্য কলকাতা শহরের প্রান্তেও দেখেছি বিশেষ করে হুগলী নদীর পূর্বপাড়ে।
আমরা ফিরছিলাম সূর্যের আলো তখনও রয়েছে। উত্তরমুখী লেনগুলোতে ক্রমেই ট্রাকের ভিড় বাড়ছে। আমি আদিনা মসজিদের ইতিহাসের সামান্য অংশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম এখানে আসার আগেই। যারা উত্তর বঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে জানেন তারা হয়তো আদিনা মসজিদের নাম আগেই শুনেছেন। এই মসজিদটিই ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম ঘাটি।
উত্তরবঙ্গে বৃটিশ এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল। সদ্য ধর্মান্তরিত হিন্দু-ধর্মালম্বী সাঁওতালরা এ এলাকাসহ উত্তরবঙ্গে সাঁওতালদের আলাদা আবাসভূমির দাবিতে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৯২৪ সালে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন জিতু সাঁওতাল। এর আগে দিনাজপুর-রাজশাহী এবং উত্তর মালদা সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হলে মালদা অঞ্চলে জিতু নামক সাঁওতালের নেতৃত্বে শুরু হয় এবং ১৯৩২ সালে জিতুর হত্যার মধ্যদিয়ে বৃটিশ এবং এ অঞ্চলের জমিদার বাহিনী এ বিদ্রোহ দমন করে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে জিতু আদিনা মসজিদকে দখল করে দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করেন। এমনকি মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তরিত করেন। পরে এখানেই জিতুর মৃত্যু হয় একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মসজিদটি পুনঃদখল করা হয়েছিল। ওই সময়েই মসজিদটি প্রচুর ক্ষতি হয়। তথ্যে প্রকাশ যে, মসজিদের দেয়ালে এখনও বৃটিশদের ছোড়া বুলেটের চিহ্ন রয়েছে।
আমরা যখন হোটেলে ফিরলাম তখন সন্ধ্যা সাতটার উপরে। আঙ্গুরগুলো ধুয়ে আনতে বললাম। গোসল করে চা পানের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। রাত নয়টায় হোটেলের পাঁচতলায় রেস্তোরাঁতে খাবারের অর্ডার দেয়া ছিল। এতক্ষণ সময় আমার রুমমেট তানভীর কলকাতার সিরিয়াল দেখে কাটালেন। বললেন, রাত দশটায় নাকি আরেকটি জমজমাট সিরিয়াল হয়। কয়েকটি সিরিয়াল নাকি তিনি কিছুতেই মিস করেন না। এ সব সিরিয়াল আমার কোনোদিন পছন্দ হয়নি কারণ বেশিরভাগ সিরিয়ালে বাঙালি পরিবারের ঐতিহ্যকে পরিহাস করা হচ্ছে। শ্বশুরের বিরুদ্ধে ছেলের বউয়ের ষড়যন্ত্র বউয়ের বিরুদ্ধে শাশুড়ি, ছেলের বিরুদ্ধে শাশুড়ি এমনকি বউ ছেলে মা বাবার বিরুদ্ধে নানা ধরনের কূটনামি। মাত্র কয়েকদিন আগে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন।
রাতের খাবার টেবিলে এসে বুঝলাম যে সকালে আমাদের আদিনা মসজিদে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা কার্যকর হচ্ছে না কারণ জয়ন্ত আর শার্শার মান্নানকে তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। তারা কেউই উত্তরে মোট ৩৬ মাইল যেতে আসতে চাইবে না। আমি অনেক আগেই বিষয়টি আঁচ করেছিলাম।
অবশেষে সকাল সাড়ে আট টায় আমরা কলকাতার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। রাস্তায় নাস্তা সেরে আমরা দুপুরের খাবার কৃষ্ণনগরে খেয়েছিলাম। কলকাতায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে গেল। পরের দিন আমরা ঢাকার পথে রওয়ানা হলাম। শেষ হল আমাদের মধ্যযুগীয় স্বাধীন বাংলার রাজধানী গৌড় দর্শন। আমাদের বাড়ির কত কাছে বাংলার ইতিহাসের এই গৌরবময় অধ্যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে এত কাছে। গৌড়ের ব্যাপ্তি চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত ছিল যার সাক্ষী ছোট সোনা মসজিদ এবং কোতোয়ালি দরওয়াজা। বলতে হয় যে, ‘দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে দু’পা ফেলিয়া একটি ধানের শীষে একটু শিশির বিন্দু।’